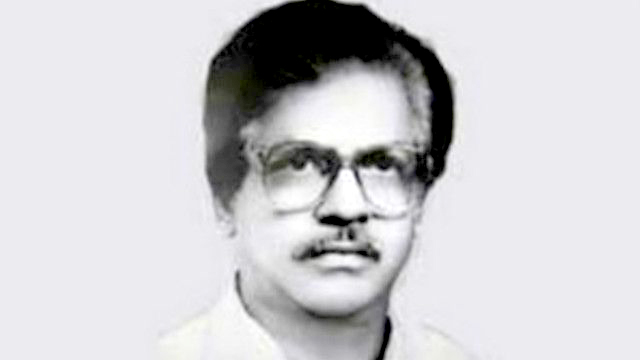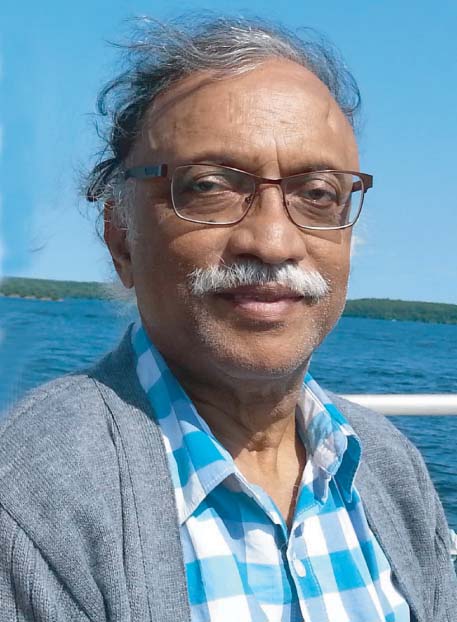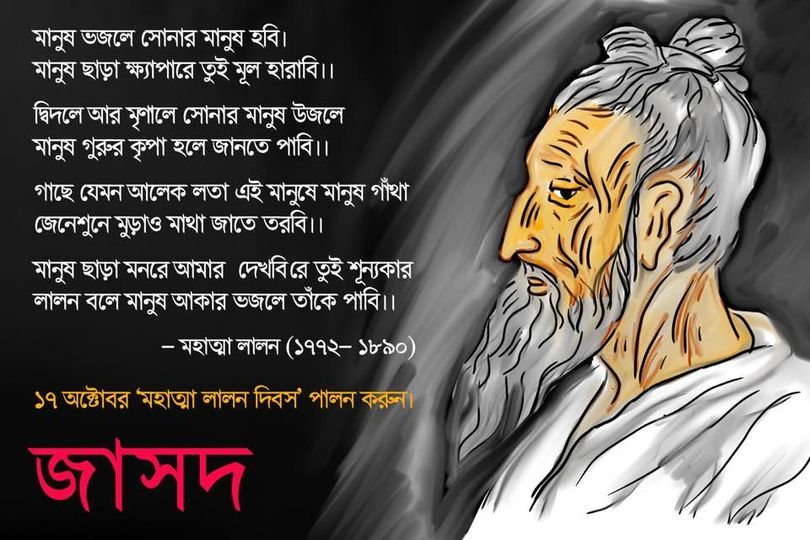কুশল বরণ চক্রবর্ত্তী
ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি অভেদ্য। চিন্তার অতীত ব্রহ্মই যখন ক্রিয়াশীল হয়ে সৃষ্টি, পালন এবং লয়ে অংশগ্রহণ করেন তখন তাকেই আমরা শক্তি বা আদ্যাশক্তি বলি। জগতের সবকিছুর মূলেই এই ব্রহ্মরূপা আদ্যাশক্তি। তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন আবার তিনিই লয় বা ধ্বংস করেন। অনন্ত তাঁর রূপ, অনন্ত তাঁর প্রকাশ এবং অনন্ত তাঁর বৈভব।
শ্রীচণ্ডীর শুরুতেই শ্রীশ্রীচণ্ডীকার ধ্যানমন্ত্রে (ধ্যান : ৩) সেই আদ্যাশক্তি মহামায়াকে “নবকোটীমূর্তিসহিতা” বলা হয়েছে। এই বাক্যের দুই ধরনের অর্থ। নবকোটীমূর্তি বলতে প্রথমত নিত্যনতুন মূর্তিতে দেবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিতা এবং দ্বিতীয় আক্ষরিক অর্থে নবকোটীমূর্তি পরিবৃতা অর্থেও প্রযুক্ত হয়।
“যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।।”
আদ্যাশক্তি মহামায়া যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণ সম্ভূতা ব্রহ্মাণী বা মহাসরস্বতী বলে অভিহিত হন; যখন পালন করেন তখন রজোগুণ সম্ভূতা বৈষ্ণবী বা মহালক্ষ্মী বলা হয় তাঁকে এবং লয় বা ধংসের স্বরূপে মাহেশ্বরী বা মহাকালী বলে অভিহিত হন দেবী।
“যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদি-দৈত্যনাশিনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ড-সংহারিণী, যিনি রক্তবীজ-ভক্ষয়ত্রী, যে মহাশক্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ-অসুর-বিনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নিত্যনতুন মূর্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।”
আরও পড়ুন : শারদীয় দুর্গোৎসব : সম্প্রীতির উৎসব
ব্রহ্ম এবং তাঁর ক্রিয়াশীল শক্তির মাঝে অভেদ-তত্ত্ব বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অসাধারণ কয়েকটি কথা বলেছেন। কথাগুলো শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীম লিখিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে—
”ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এককে মানলেই আর-একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; … অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না।”
“আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোনো কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।”
শারদীয়া দুর্গাপূজা আশ্বিনের শুক্লপক্ষে হয়। আবার কার্তিক মাসেও দেবীর পূজা হয়, যা কাত্যায়নী পূজা নামে খ্যাত। বর্তমানে আমরা বাঙালিরা যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা করি এই পূজা প্রচলন করেন রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ণ...
সামবেদীয় কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী আখ্যানে ব্রহ্ম এবং তৎশক্তি অভেদ, এই শাক্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করা আছে। আদ্যাশক্তি মহামায়া যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণ সম্ভূতা ব্রহ্মাণী বা মহাসরস্বতী বলে অভিহিত হন; যখন পালন করেন তখন রজোগুণ সম্ভূতা বৈষ্ণবী বা মহালক্ষ্মী বলা হয় তাঁকে এবং লয় বা ধংসের স্বরূপে মাহেশ্বরী বা মহাকালী বলে অভিহিত হন দেবী।
“মহালক্ষ্মীর্ম্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী।
ঈশ্বরী সর্বভূতানাং সর্বকারণকারণম্।।
সর্বকামার্থদা শান্তা সুখসেব্যা দয়ান্বিতা।
নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা।।”
(দেবীভাগবত পুরাণ : ৩.৯. ৩৯-৪০)
“অখিল ভূতগণের ঈশ্বরী, সমুদয় কারণের কারণ সেই মহামায়াই মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী। সেই পরম দয়াবতী শান্তময়ী দেবীকে সেবা করাও ক্লেশকর নহে এবং তাঁর আরাধনায় সর্বফল লাভ হয়। অধিক কি তাঁর নাম উচ্চারণ মাত্রেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।”
আরও পড়ুন : এই দুঃখ কোথায় রাখি?
শ্রীচণ্ডীতে তিনটি চরিত্রে আদ্যাশক্তি মহামায়ার তিনটি প্রধান রূপেরই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম চরিত্রে (প্রথম অধ্যায়) দেবী মহাকালিকা রূপে মধুকৈটভকে বধ করেছেন। দ্বিতীয় চরিত্রে (দ্বিতীয়-চতুর্থ অধ্যায়) দেবী মহালক্ষ্মী রূপে মহিষাসুর বধ করেছেন এবং তৃতীয় বা উত্তর চরিত্রে (পঞ্চম-ত্রয়োদশ) দেবী মহাসরস্বতী রূপে শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করেছেন।
শ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখি যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী এবং তিনিই সরস্বতী। কিন্তু আমরা প্রচলিত বাঙালি বিশ্বাসে দেখি দেবী দুর্গার দুই মেয়ে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী; কিন্তু শ্রীচণ্ডী অনুসারে তাঁরা সকলেই এক আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা। শুধুমাত্র প্রকাশ বিভিন্ন। শ্রীচণ্ডীর দেবীকবচে নবদুর্গা নামে দেবীর নয় প্রকার রূপের কথা ব্যক্ত হয়েছে।
“প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদূর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা।।”
(দেবীকবচ : ৩-৫)
“প্রথম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চন্দ্ৰঘণ্টা, চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি, অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম মোক্ষপ্রদাত্রী সিদ্ধিদাত্রী; দেবীর এই নবরূপই নবদুর্গা নামে প্রকীর্তিতা। এই সকল নাম ব্রহ্মের দ্বারাই উক্ত হয়েছে।”
আরও পড়ুন : ধর্ম যার যার থাকুক, উৎসব হোক সবার
সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গাই কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রকাশিতা। বৈদিককাল থেকেই তাঁর পূজা প্রচলিত। আশ্বলায়ন শাখার ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্তে রাত্রিরূপা আদ্যাশক্তি ভগবতী দুর্গাকে ক্ষীরসহ পঞ্চগব্যাদি দিয়ে দেবীর শ্রীবিগ্রহকে অভিষিক্ত করে চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত করে “নমো দুর্গে নমো নমঃ” মন্ত্রে দেবীর গলায় বিল্বপত্রের মালা প্রদান করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নির্দেশনাও রয়েছে।
“ক্ষীরেণ স্নাপিতা দুর্গা চন্দনেনানুলেপিতা।
বৈল্বপত্রকৃতামালা নমো দুর্গে নমো নমঃ।।”
(আশ্বলায়ন শাখার ঋগ্বেদ সংহিতা : ১০.১২৮.৮)
দুর্গাপূজা এই বঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বঙ্গের বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বিধানেও আমরা দুর্গোৎসবের সরব উপস্থিতি পাই...
পুষ্পপত্র, চন্দনাদি অনুলেপন এবং দেবীর শ্রীবিগ্রহের অভিষেকসহ বিবিধ উপাচারে দেবীর পূজাও পদ্ধতিও বৈদিক। অর্থাৎ অনেকেই বলেন, বৈদিকযুগে প্রতিমাপূজা ছিল না, প্রতিমা পূজা পদ্ধতি অবৈদিক, তাদের কথাগুলো সত্য নয়। তারা অনেকটা বেদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে না জেনেই ব্যক্তিগত বা জনপ্রিয় প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেন।
একই সত্ত্বার শুধুমাত্র প্রকাশ বিভিন্ন হওয়ার কারণে এই দৃশ্যমান বিভিন্ন স্বরূপ দেখে মায়ার প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাই আমরা প্রতিনিয়ত। উপাস্য রুচির বৈচিত্র্যের জন্যে একই ব্রহ্মের আলাদা আলাদা রূপের প্রকাশ। আমরা এক পরমেশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কারো উপাসনা করি না। বেদে বিভিন্ন মন্ত্রে অত্যন্ত সুন্দর এবং স্পষ্ট করে বিষয়টা বলা আছে।
“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি-মাহু রথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নি যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।”
(ঋগ্বেদ সংহিতা : ১.১৬৪.৪৬)
আরও পড়ুন : মিলেছি প্রাণের উৎসবে
“সেই সদ্বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু জ্ঞানীগণ তাঁকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য (সূর্য), সুপর্ণ, গরুড়, যম, বায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকেন।”
“ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপুচ্যতে।
য এতং দেবমেক বৃতং বেদ।।”
(অথর্ববেদ সংহিতা : ১৩.৪.২)
“পরমাত্মা এক, তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলে অভিহিত হয় না। যিনি তাঁহাকে শুধু এক বলে জানেন একমাত্র তিনিই তাঁকে প্রাপ্ত হন।”
আরও পড়ুন : রাজনৈতিক সম্প্রীতির দেশ!
বৈদিক একত্ববাদের মতো শ্রীচণ্ডীতেও অসংখ্য স্থানে দেবীর অদ্বৈতবাদী একত্ব বর্ণিত আছে। উত্তর চরিত্রে দেবী ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, নারসিংহী, বারাহী এবং চামুণ্ডা এই অষ্টমাতৃকা শক্তিকে সাথে নিয়ে শুম্ভনিশুম্ভের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
যুদ্ধে দেবীর হাতে শুম্ভের প্রাণতুল্য ভাই নিশুম্ভ বধ হয়। শুম্ভ ভাইকে নিহত হতে দেখে এবং সকল সৈন্যবল বিনষ্ট হতে দেখে, উত্তেজিত হয়ে দেবীকে বলেন, “হে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না তুমি অন্যান্য বিভিন্ন দেবীকে সাথে নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত করছো, তাই গর্বিত হওয়ার কিছুই নেই।” শুম্ভের ক্রোধভরা উক্তি শুনে দেবী তখন বলেন—
“একৈবাহং জগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।।”
(শ্রীচণ্ডী : ১০.০৫)
“আমিই একমাত্র জগতে বিরাজিতা। আমার অতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয়া আর কে আছে জগতে? ওরে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী এই সকল দেবী আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দেখ ওরা আমাতেই মিলে বিলীনা হয়ে যাচ্ছে।”
অর্থাৎ দেবী এক থেকে বহু হয়েছিলেন, আবার বহু থেকে আবার এক অদ্বৈত হয়ে গেলেন।
“একই শক্তির শুধু বিভিন্নরূপের প্রকাশ চারিদিকে
নিরাকারকে সাকারে বাধার ভক্তচেষ্টা।
সরস্বতী-লক্ষ্মী-কালী এ ত্রিধা মূর্তি পরিব্যাপ্ত,
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণপ্রতিভূ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।
অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই চলছে সেই
চিন্ময় শক্তির নিয়ত প্রকাশের খেলা।
সৃষ্টির আনন্দ, স্থিতির অভিভাবকত্ব;
ধ্বংসের মুক্তির প্রশান্তি সর্বত্রই সেই কারণমময়ী।
তিনি অনন্তরূপী,তাঁর কোনো প্রাকৃত মূর্তি নেই,
সন্তানের শুদ্ধমানসলোকই তাঁর মূর্ত্তির উৎস।”
বাঙালিরা ষষ্ঠী থেকে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে পূজা শুরু করে বিজয়া দশমীতে দশমীবিহিত বিসর্জনাঙ্গ পূজা, সিঁদুর খেলা এবং পরিশেষে নৃত্যগীতাদির সাথে বিসর্জনের মাধ্যমে পাঁচদিনের বর্ণাঢ্য দুর্গোৎসব সমাপ্ত করেন...
সমস্যা বাধে তখনই, যখন আমরা যার যার ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকেই যে যে মতাবলম্বী সবাইকে সেই সেই মতাবলম্বী বানাতে চাই। আমরা ভুলে যাই বেদান্তসূত্রের চতুর্থসূত্রকে। “তত্তু সমন্বয়াৎ (১.১.৪)।” এই সূত্রেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে বিভিন্ন মত-পথ নির্বিশেষে সকল মত-পথই ব্রহ্ম লাভ এবং উপলব্ধির এক একটি পন্থা। তিনিই জীবকে অজ্ঞানতার মায়ার ডোরে বদ্ধ করেন, আবার তিনিই সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।
আরও পড়ুন : ফিরে আসুক সম্প্রীতি
ঋগ্বেদ সংহিতায় দেবী বলেছেন, তিনি রাষ্ট্রী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তি ঈশ্বরী। যে সব সাধক তার উপাসনা করে, সেই সব উপাসকদের তিনি মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স ধন এবং জাগতিক আভ্যুদয়িক ধন প্রদান করেন। প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ের মাঝেই তিনি বিরাজিতা। তিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী, সব দেবতাগণের তিনি শক্তিস্বরূপা এবং অগ্রগণ্যা।
বিবিধ রূপে প্রকাশিত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই জগৎ প্রপঞ্চরূপে অনন্তভাবে, অনন্তরূপে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হয়ে বিরাজ করেন। তিনিই নিমিত্ত কারণ হয়ে জগতকে পরিচালনা করেন, আবার তিনিই উপাদান কারণ হয়ে এই জগতের জড় চেতন সকল কিছুতেই বিরাজ করেন।
তিনিই জীবাত্মা হয়ে জীবের মধ্যে প্রবিষ্টা জীবের প্রাণকে সচল রাখেন। রূপ থেকে রূপান্তরে সর্বদেশে, সর্বকালেই তিনি পূজিতা। প্রাণীকুল থেকে দেবতা সকলেই বিবিধভাবে তাকে আরাধনা করে। তিনি যেহেতু অনন্য এবং অনন্ত; তাই তাঁর উপাসনা পদ্ধতিও অনন্ত।
“অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।”
(ঋগ্বেদ সংহিতা : ১০.১২৫.৩)
“আমি রাষ্ট্রী অর্থাৎ সমগ্র জগতের ঈশ্বরী। আমি উপাসকগণের ধন প্রদাত্রী। আমি পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ জেনেছি। আমি যজ্ঞিয় দেবতাগণের প্রধানা। জগৎ প্রপঞ্চরূপে আমি অনন্তভাবে অবস্থান করি এবং জীবাত্মা হয়ে জীবের মধ্যে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।”
আরও পড়ুন : অর্থনীতি যখন উৎসবের অংশ
ঈশ্বরকে মাতৃরূপে আরাধনা সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয় সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল সৃষ্টিকর্তাকে মাতৃরূপে আরাধনার প্রভাব। প্রত্যেকটি জাতির জীবনেই দেখি ঈশ্বরীরূপা মহাদেবীর অবস্থান। যেমন, সেমিটিকদের মধ্যে ছিল দেবী ননা, অনৎ; আরবদের ছিল ঈশ্বরীস্বরূপা সর্বশক্তিমান অল্লৎ; ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতে ইশতার; পারস্যে ছিলেন মহাদেবী অর্দ্বি; ফিনিশিয়দের হলেন মিলিত্তা; মিশরের অন্যতম প্রধান দেবী হলেন আইসিস; এথেন্সের হলেন এথিনি; গ্রিকদের হলেন আর্তিমিস; রোমানদের হলেন ডায়না। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাচীন খুব কম জাতিই আছে যাদের জীবনে একজন শক্তি স্বরূপা মহাদেবী নেই।
আমাদের প্রচলিত ধারণা মতে, বসন্তকালের দুর্গাপূজাই প্রকৃত পূজা। কিন্তু এই তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীচণ্ডীতে জগন্মাতা দুর্গা নিজেই তাঁর বাৎসরিক পূজা শরৎকালে করতে বলেছেন। বাল্মীকিরচিত রামায়ণে কোথাও শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার কথা পাওয়া যায় না। অবশ্য বাল্মীকিরচিত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বা লঙ্কাকাণ্ডে একটা শ্লোকে (৮৫.৩৪) ব্রহ্মার বিধান দ্বারা রঘুনন্দনের মহামায়া পূজার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে দুর্গাপূজা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) লেখা কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণে।
“শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতম্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।।”
(শ্রীশ্রীচণ্ডী : ১২.১২)
“শরতকালে আমার যে বাৎসরিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সবাই ভক্তি সহকারে আমার মাহাত্ম্য কথারূপ শ্রীচণ্ডী পাঠ করে শুনবে।”
দুর্গাপূজার প্রচলন বা মাহাত্ম্য সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় যা আমাদের কাছে শ্রীচণ্ডী নামে খ্যাত। এই শ্রীচণ্ডীর তেরটি অধ্যায়ের ৫৭৮টি শ্লোক এবং ৭০০টি মন্ত্রে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্ত্রী-সন্তানদের দ্বারা প্রতারিত সমাধি নামক এক বৈশ্য একদিন মেধা ঋষির আশ্রমে যান। সেখানে তাঁর নির্দেশে তাঁরা দেবীদুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা করেন এবং দেবীসূক্ত জপ করেন। পূজায় সন্তুষ্টা হয়ে দেবী তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কালিকা পুরাণ থেকে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে যুদ্ধজয় করতে দেবীকে পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এই পূজার নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। চৈত্রের শুক্লপক্ষেও দেবীর পূজা হয় যা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে খ্যাত।
শারদীয়া দুর্গাপূজা আশ্বিনের শুক্লপক্ষে হয়। আবার কার্তিক মাসেও দেবীর পূজা হয়, যা কাত্যায়নী পূজা নামে খ্যাত। বর্তমানে আমরা বাঙালিরা যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা করি এই পূজা প্রচলন করেন রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ণ, তিনি ছিলেন মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের বংশধর।
কংশনারায়ণকে পূজা পদ্ধতি প্রদান করেন রাজপুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী। দুর্গাপূজা এই বঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বঙ্গের বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বিধানেও আমরা দুর্গোৎসবের সরব উপস্থিতি পাই। জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসব নির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০) দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসব বিবেক, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়া চিন্তামণি, শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব গ্রন্থেও দুর্গাপূজার বিধান পাওয়া যায়।
রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণের পরবর্তীতে, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩) বিভিন্ন আড়ম্বর এবং চাকচিক্যের মাধ্যমে দুর্গাপূজাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। একবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে দুর্গাপূজা রাজা, মহারাজা এবং জমিদারদের হাত থেকে বেড়িয়ে সর্বজনীন এক মহোৎসবে পরিণত হয়ে যায়। এই মহোৎসবের পরিধি বাড়তে বাড়তে আজ সারাবিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।
আজ দুর্গোৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি ছোট, বড় শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। শুক্ল পক্ষের অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া দশমী সারা পৃথিবীতেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ হয়তো ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী থেকে পূজা শুরু করে, কেউ প্রতিপদ থেকে, কেউ বা পঞ্চমী থেকে।
বাঙালিরা ষষ্ঠী থেকে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে পূজা শুরু করে বিজয়া দশমীতে দশমীবিহিত বিসর্জনাঙ্গ পূজা, সিঁদুর খেলা এবং পরিশেষে নৃত্যগীতাদির সাথে বিসর্জনের মাধ্যমে পাঁচদিনের বর্ণাঢ্য দুর্গোৎসব সমাপ্ত করেন।
দেবী দুর্গা যে রাজা-প্রজা, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলেরই মা এবং তিনি যে সর্বস্থানেই বিরাজ করেন এই সরল তত্ত্বীয় বিষয় বোঝাতেই দেবীর মহাস্নানে সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত রাজার দ্বারের মাটি যেমন লাগে; পক্ষান্তরে সমাজের সর্বোচ্চ অপাংক্তেয় বেশ্যার দ্বারের মাটিসহ আরও বহু স্থানের মাটি, জলের প্রয়োজন হয়। অবশ্য বেশ্যা শব্দটি গণিকা শব্দের বাইরে ভিন্ন অর্থও হয়। তন্ত্র মতে বেশ্যা শব্দের অর্থ, কৌল অভিসিক্তা নারী অর্থাৎ শাক্ত মতে, সাধন পথে অভিষিক্তা নারীকেও বোঝায়।
দেবী দুর্গার সর্বজনীনতার এই বিষয়টি বুঝতে হলে এই ভূখণ্ডের মনন প্রয়োজন। চোখের দৃষ্টিপথে বৈদেশিক সংস্কৃতির চশমা পরিধান করে থাকলে, কখনো বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।
কুশল বরণ চক্রবর্ত্তী ।। সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়