আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ আর নেই। বুধবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৯ বছর বয়সে চিরপ্রস্থানের এ যাত্রায় শামিল হলেন শঙ্খ ঘোষ।
এমনিতেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কবি, যা শারীরিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল তাকে। এর আগে জানুয়ারিতেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাকে। শক্তি-সুনীল-শঙ্খ-উৎপল-বিনয়, জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতার এই পঞ্চপা-বের বাকি চার জনের পর এবার চলে গেলেন কবি শঙ্খ ঘোষ।
গায়ে জ্বর থাকায়, গত সপ্তাহে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন কবি। ১৪ এপ্রিল বিকালে রিপোর্ট এলে জানা যায়, তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। কোভিড সংক্রমণ ধরা পরার পর ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আচমকা তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।
বুধবার সকালে তাকে ভেন্টিলেটরে দেওয়ার চেষ্টাও হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চিরতরে চলে গেলেন তিনি। দীর্ঘ কর্মজীবনে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে শঙ্খ ঘোষকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন।
১৯৯২ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করেন। বছর দুয়েক আগে ‘মাটি’ নামের একটি কবিতায় মোদি সরকারের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। সাহিত্যজীবনে একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। ১৯৭৭ সালে ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে কন্নড় ভাষা থেকে বাংলায় ‘রক্তকল্যাণ’ নাটকটি অনুবাদ করে ফের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান তিনি।
এ ছাড়াও রবীন্দ্র পুরস্কার, সরস্বতী সম্মান, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১ সালে তাকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে ভারতের তৎকালীন সরকার। শঙ্খ ঘোষ এর আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। তার পিতা মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতা অমলা ঘোষ।
১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুর জেলায় তার জন্ম। বংশানুক্রমিকভাবে পৈত্রিক বাড়ি বরিশালের বানারিপাড়ায়। তবে শঙ্খ ঘোষ বড় হয়েছেন পাবনায়। পিতার কর্মস্থল হওয়ায় তিনি বেশ কয়েক বছর পাবনায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় কলা বিভাগে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।
Category: মশাল সাহিত্য
-
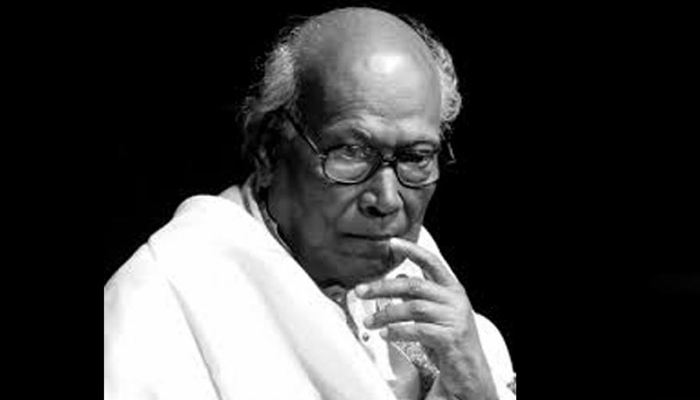
কবি শঙ্খ ঘোষ আর নেই
-
করোনারে করোনা
সুভাষ চৌধুরী
করোনারে করোনা
তুই হলি সব যন্ত্রণা।
তোর থাবায় মরলে লাকি
ব্যাংকার পায় পঞ্চাশ লাখ।
তুই কি মানুষ বেছে খাস
কিষান শ্রমিকের হয় কি জানিস।
রোগ সারাতে টাকা জোটেনা
মরণের পর জায়গা মেলে না।
এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম
এই নাকি তোর বিধান।
তোর হামলায় মরলে পরে
কেউ আসে না গরিবের ধারে।
করোনারে করোনা
আরে একটুখানি থাম না।
মানুষ খেকো করোনা
তোর কি পেট ভরে না।
কারও কপালে লাখে লাখ
অন্যের বেলায় চিচিং ফাঁক।
পুলিশ ডাক্তার পায় ভাগা
মুটে মজুরের কপাল ফাঁকা।
চাকরিজীবী ঘরে বসে
বেতন তুলে খায় দায়।
গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়
হর্ণ বাজিয়ে লোক সরায়।
ঈদ বাজারে ভিড় করে
শপিং ব্যাগ ভর্তি করে।
আমাদের কয় সরে দাঁড়াও
আম জনতা ভয় পেয়ে যায়।
সরকারজীবী আরও মজায়
ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচায়।
হাঁকিয়ে গাড়ি ভাঙ্গে লক
বলে দোকান বন্ধ রাখ।
স্কুল কলেজ খুলবি না।
ছেলে মেয়েরা থাকবি বাড়ি
প্রাইভেট পড়ে শিখে নিবি।
অটো পাস সার্টিফিকেট
পেয়েই যাবি অটোমেটিক।
নরখাদক করোনা
তোর কি হয় না করুণা।
মানুষ মেরে কী লাভ তোর
রক্ত খাস ক্যান চশমখোর।
তোর বিরুদ্ধে আমার লড়াই
করিস নাতো আর বড়াই।
দম আটকে মরছি ঘরে
এবার খুলবো জগতটারে।
ভ্যাকসিন দিয়ে পুড়াবো তোরে
চার হাত পা বেঁধে তোরে।
তোর জ¦ালাতন সইতে নারি
দেখবি আর কী করতে পারি।
বাড়াবাড়ি বন্ধ কর
নইলে তোর নেই নিস্তার।
ধর করোনারে ধর
হাসপাতাল ঘেরাও কর।
উঁচিয়ে লাঠি বাজিয়ে বাঁশী
করোনারে ধাওয়া কর।
ধরে ধরে ব্যাগে পুরে
ইনজেকশনে ধ্বংস ক’রে।
করোনামুক্ত জীবন গড়ি
লক ডাউন ফেলে চলি ফিরি।করোনারে করোনা
সুভাষ চৌধুরীকরোনারে করোনা
তুই হলি সব যন্ত্রণা।
তোর থাবায় মরলে লাকি
ব্যাংকার পায় পঞ্চাশ লাখ।
তুই কি মানুষ বেছে খাস
কিষান শ্রমিকের হয় কি জানিস।
রোগ সারাতে টাকা জোটেনা
মরণের পর জায়গা মেলে না।
এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম
এই নাকি তোর বিধান।
তোর হামলায় মরলে পরে
কেউ আসে না গরিবের ধারে।
করোনারে করোনা
আরে একটুখানি থাম না।
মানুষ খেকো করোনা
তোর কি পেট ভরে না।
কারও কপালে লাখে লাখ
অন্যের বেলায় চিচিং ফাঁক।
পুলিশ ডাক্তার পায় ভাগা
মুটে মজুরের কপাল ফাঁকা।
চাকরিজীবী ঘরে বসে
বেতন তুলে খায় দায়।
গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়
হর্ণ বাজিয়ে লোক সরায়।
ঈদ বাজারে ভিড় করে
শপিং ব্যাগ ভর্তি করে।
আমাদের কয় সরে দাঁড়াও
আম জনতা ভয় পেয়ে যায়।
সরকারজীবী আরও মজায়
ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচায়।
হাঁকিয়ে গাড়ি ভাঙ্গে লক
বলে দোকান বন্ধ রাখ।
স্কুল কলেজ খুলবি না।
ছেলে মেয়েরা থাকবি বাড়ি
প্রাইভেট পড়ে শিখে নিবি।
অটো পাস সার্টিফিকেট
পেয়েই যাবি অটোমেটিক।
নরখাদক করোনা
তোর কি হয় না করুণা।
মানুষ মেরে কী লাভ তোর
রক্ত খাস ক্যান চশমখোর।
তোর বিরুদ্ধে আমার লড়াই
করিস নাতো আর বড়াই।
দম আটকে মরছি ঘরে
এবার খুলবো জগতটারে।
ভ্যাকসিন দিয়ে পুড়াবো তোরে
চার হাত পা বেঁধে তোরে।
তোর জ¦ালাতন সইতে নারি
দেখবি আর কী করতে পারি।
বাড়াবাড়ি বন্ধ কর
নইলে তোর নেই নিস্তার।
ধর করোনারে ধর
হাসপাতাল ঘেরাও কর।
উঁচিয়ে লাঠি বাজিয়ে বাঁশী
করোনারে ধাওয়া কর।
ধরে ধরে ব্যাগে পুরে
ইনজেকশনে ধ্বংস ক’রে।
করোনামুক্ত জীবন গড়ি
লক ডাউন ফেলে চলি ফিরি। -

আহমদ ছফা : একজন খাঁটি স্বাধীন লেখক
আহমদ ছফা
একজন খাঁটি স্বাধীন লেখক
সাখাওয়াত টিপুআমাদের সৌভাগ্য এই আমরা আহমদ ছফার [৩০ জুন ১৯৪৩, ২৮ জুলাই ২০০১] যুগে জন্মেছিলাম। আর বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য এই তাঁর মতো কীর্তিমান লেখক বাংলা ভাষায় জন্মেছিলেন। বাংলা ভাষার চৌহদ্দী বিবেচনায় আনলে দেখা মিলবে, তিনি রেখে গেছেন সাহিত্য সৌন্দর্যের নানা চিহ্ন, নানা সৃষ্টি, নানা চিন্তা, নানা পথ, নানা উদ্দীপনা আর লড়াই-সংগ্রামের ভাষার অমূল্য কীর্তি। তাঁর ইহকাল ত্যাগের দুই দশক পর কথাটা আমরা কত না সহজে বললাম! বলা এত সহজ ছিল না জীবদ্দশায়। কেন? আমরা যারা মহাত্মা ছফার সামান্য সান্নিধ্য পেয়েছি, তারা অল্প-বিস্তর জানি। জীবদ্দশায় কলিকালের সমাজ আহমদ ছফার প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার তো দূরবাত, কোনো পত্রিকার সংখ্যাও আহমদ ছফার নামে হয়নি। অথচ কত খইভাজা লেখককে নিয়ে সমাজে কত কিছু হয়! আদতে ছফার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে ইহকালের পর।
প্রশ্ন দাঁড়ায় আহমদ ছফার রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে? জীবদ্দশায় ভক্ত-অনুরাগী পাঠক যেমন ছিল, ঠিক তেমনি কম ছিল না সমালোচকের আধিক্য। ইহকাল ত্যাগের পর ঢাকার একদল লেখক বলতে লাগলেন ছফাকে নিয়ে অহেতু গুঞ্জন করবার কিছু নেই। কিন্তু দেশ যখন নানা সংকটের মুখে আবর্তিত হয়, তখন ছফার বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা হয়ে ওঠে জনগণের আশ্রয়। তখন তারা বলতে থাকেন আহমদ ছফা একজন খাঁটি বুদ্ধিজীবী। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বেহতর নন। আবার তিনি যখন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক বাস্তবতা, প্রকৃতির স্বভাব, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির অবনমনের বিপরীতে প্রজ্ঞা আকারে হাজির হন, তখন উল্টো সুরে বলেন ছফার উপন্যাস ভালো, কিন্তু কবিতা ‘বাজে’। এখন এই সব স্বর মৃদুতর হচ্ছে ক্রমশ। হয়তো কেউ কেউ বলবেন, দু-চারটে ভালো কবিতা তিনি লিখেছেন বটে! বস্তুত ছফাকে বাজালে দেখা যাবে সমস্ত আহমদ ছফা, অনন্য এক বাংলা ভাষা। ভাষা ভাবের অর্থ শুদ্ধ কথার কথা নয়। ভাষা মানে দেশ। আর আমরা যাকে দর্শনযোগে বলি, ভাষার অপর ঠায়। মানে দেশ। আর আহমদ ছফার চিন্তায়, মননে আর সৃষ্টিশীলতায় ঠায় আস্ত একদেশ স্বপ্ন, নাম বাংলাদেশ।২
মনীষী আহমদ ছফাকে নিয়ে নানাজন নানা রূপে কাজ করেছেন। করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। ভবিষ্যতে নতুন নতুন চিন্তায় আর বিশ্লেষণে নতুনভাবে সাহিত্যে আবির্ভূত হবেন তিনি। কারণ তিনি আমাদের সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে জাতীয় সম্পদ হয়ে গেছেন। তবে তাকে নিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন আহমদ ছফার গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্র ও কথাসাহিত্যিক নুরুল আনোয়ার। ছফার ৫৮ বছরের প্রায় লেখাজোখা আর কথামালার সঞ্চয় একত্র করেছেন তিনি। অনেকটাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন নুরুল আনোয়ার। কারণ ছফার জীবন খুব গোছানো ছিল, তা হলফ করে বলা যাবে না। লেখায়, চিন্তায়, লড়াইয়ে আর সৃষ্টিশীলতায় ছফা যত না সংহত, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন খানিক অগোছালো। তবে ব্যক্তিগত জীবনে বস্তুগত সহায়-সম্পদের হাতছানি থেকে নিজের দূরে রেখেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, আজ প্রথাগত জীবনের বাইরে এক অলঙ্ঘনীয় সাহিত্যের রাজপথ পাড়ি দিয়েছেন ছফা। সত্যিকার অর্থেই অকৃতদার আহমদ ছফা এক বর্ণাঢ্য লেখকজীবন পার করেছেন। সমাজের ক্লেদ, অন্যায়, অবিচার আর অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে জীবনের শেষ আয়ু ত্যাগ করেছেন তিনি। খোদ বাংলাদেশে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো এমন চরিত্র বিরল।
আহমদ ছফাকে নিয়ে অপর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজটি করেছে আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা। সভার অন্যতম প্রধান মশহুর লেখক ও চিন্তাবিদ সলিমুল্লাহ খান। রাষ্ট্রসভার সভ্যগণ বছর বছর সেমিনার করে আহমদ ছফার সাহিত্যচিন্তাকে নানাভাবে বিচার করেছেন। পাঠকের পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন সামনে এনেছেন। নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছেন। এমন ফলপ্রসূ উদ্যোগ বাংলাদেশে হয় না বললে চলে, সচরাচর। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, ইহকাল ত্যাগের পর বাংলাদেশে বেশির ভাগ কথিত প্রধান সাহিত্যিক ‘নাই’ হয়ে যান। কিন্তু আহমদ ছফার বেলায় ঘটেছে নিয়মের অতিক্রম। তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিকরূপে আবির্ভূত হন ইহকাল গতের পর। এটার প্রধান কারণ ছফার সাহিত্যচিন্তা আর সৌন্দর্যের গুণ। অন্য গুণ সহজ ভাষায় জটিল চিন্তার বয়ান। অপর কারণ আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা আন্দোলন। হয়তো কোনো কোনো প্রশ্নে কেউ কেউ একমত না-ও হতে পারেন, তবে সত্য এই আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার আন্দোলন দিয়েছে তার সাহিত্যের পুরুজ্জীবনের প্রশস্ত পথের নব দিশা।৩
জগতে একবার যিনি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন, তার পক্ষে অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়! দাসত্ব মানেই অপরের অধীন কালযাপন। কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার সূত্র অপরের স্বাধীনতার সমান। কিন্তু মানব সন্তানের চিন্তার স্বাধীনতা অবারিত। অবারিত চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্তির সৃষ্টিশীল পথ প্রশস্ত করে। কীর্তিমান আহমদ ছফার সৃষ্টিশীল কর্মের বেলায়ও তাই ঘটেছে। ফলে তিনি আমাদের কাছে আনকোরা। একেবারেই নতুন চিন্তার আকর। কেননা তিনি কথায় টগবগে, বচনে সহজ, যাপনে সরল, চিন্তায় দার্ঢ্য আর সাহিত্যকে অন্তর্গত সত্যের দুয়ারের সামনে হাজির করেছেন। তার নিষ্ঠ পাঠকমাত্র সেই পরকীয়া সূত্র টের পাবেন। বলতে দ্বিধা নেই, লেখক হিসেবে ছফা তাঁর সময়কে অতিক্রম করেছিলেন। কারণ মত প্রকাশের সততার ক্ষেত্রে তার কোনো পিছুটান ছিল না। তিনি কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না, বলতেন সত্যের দোহাই রূপে। তাঁর বলার ভেতরে ব্যক্তিগত ক্ষতি-বৃদ্ধির ব্যাপার নেই। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবসায়ে তিনি জীবদ্দশায় কারো কারো অস্বস্তির কারণও ছিলেন। কিন্তু যত ছুতোই থাকুক না কেন আজ তার সৃষ্টিশীল পর্যবেক্ষণকে অস্বীকার করবার কোনো জো নেই।
নানা পত্রপত্রিকায় এখনো ছড়ানো আছে আহমদ ছফার অমূল্য বয়ান। তাই আমরাও মনীষী আহমদ ছফাকে নতুনভাবে পরখ করার অবসর নিয়েছি। চালু বাংলায় অবসর মানে কর্মমুক্তি। তবে অবসরকে আমরা জিরানো অর্থে নিলাম। অবসর নিলাম আহমদ ছফার লেখার ওপর একটু দম ফেলার। মানে চিন্তার অবসর আকারে। আমরা মনীষী ছফার কয়েক টুকরো সাক্ষাৎকার একত্র করেছি। নাম জারি করেছি ‘আহমদ ছফার বাছাই জবাব’। কেন বাছাই জবাব? প্রথমত, আহমদ ছফাকে নতুন রূপে পড়া আর বোঝার জন্য সাক্ষাৎকারের বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত, যেকোনো প্রশ্নের উত্তরে একজন লেখক কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তৃতীয়ত, লেখার বিষয় অতিক্রান্ত যেসব চিন্তা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, সেসব প্রশ্নের জবাব সামনে হাজির করা। চতুর্থত, আহমদ ছফার জীবদ্দশার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্তর্দৃষ্টির একটা অবলোকন। যেকোনো সাক্ষাৎকার মাত্রই একজন লেখকের অন্তর্দৃষ্টির তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ। তাতে বান্তর আর অবান্তর দুই ধরনের কথার সমাহার থাকে। থাকে কল্পনা আর জ্ঞানের সম্বন্ধ। তবে যেকোনো প্রশ্নই তার উত্তরের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলো লেখার অপূর্ণ বিষয়ের শূন্যস্থান পূরণ। ফলে একজন আহমদ ছফাকে বুঝবার আর জানবার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার এক অনন্য উপায়।
‘আহমদ ছফার বাছাই জবাব’ বইয়ের প্রচ্ছদ৪
আমরা যখন ‘আহমদ ছফা : বাছাই জবাব’ সম্পাদনায় হাত দিয়েছি, তখন মহামারিকবলিত দুনিয়া স্থবির। সংকটকবলিত মানব প্রজাতি আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে রত। সে অনির্বচনীয় মহামারি মোকাবেলা করতে হচ্ছে দেশের মানুষকে। বস্তুত এই সময় মানুষ যার মতো একা হয়ে যায়। ফলে ছফার অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার উদ্ধার করতে ঊন-কাঠখড় পোহাতে হয়। তবে আমরা সংকলনে গ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের সকল গ্রহীতার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমাদের সৌভাগ্য আলাপচারীগণ খুবই সানন্দে প্রকাশের সম্মতি দেন। সম্পাদনার তথ্য ঘাটতি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রেক্ষিত আর সময়ের অপরাপর বিষয়াবলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। নানা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। তাদের সার্বিক পরামর্শ ও ভালোবাসার কারণে দ্রুততম সময়ে সম্পাদনা সম্পন্ন হয়। আমরা সবার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারে প্রকাশিত আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার অনুবাদ করেছেন লেখক সামসুদ্দোজা সাজেন। আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার সজ্জন লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও সামসুদ্দোজা সাজেনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নানা তথ্যের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়েছেন সর্বজন লেখক নাসির আলী মামুন, সলিমুল্লাহ খান, নূরুল কবীর, মারুফ রায়হান, সাজ্জাদ শরিফ, রাজু আলাউদ্দিন, আলতাফ পারভেজ, জুলফিকার হায়দার, আহমাদ মোস্তফা কামাল, বিপ্লব রহমান, মিল্টন আনোয়ার ও শেখ মামুনুর রশিদ। দুটো অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের সন্ধান দিয়েছেন লেখক হামীম কামরুল হক ও লোক সম্পাদক অনিকেত শামীম। সম্পাদনায় শিরোনামের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। আগের প্রচারিত শিরোনামের বদল করেছি। যাতে নতুন রূপে আহমদ ছফাকে দৃষ্টিপাত করা যায়। আমাদের ইচ্ছে ছিল আরও দু-একটি সাক্ষাৎকার সংকলন ভুক্ত করার। কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা করে পাইনি। ফলে সংকলন ভুক্ত হয়নি। আহমদ ছফার আরও কিছু অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের গুজব শুনেছি, কিন্তু অক্ষরে দেখিনি। ভবিষ্যতে হয়তো দেখা মিলবে।
সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এতদ সময়ে ভারতের কবি সৌম্য দাশগুপ্তের সঙ্গে বাঙালি প-িত ও লেখক সুধীর চক্রবর্তীর সম্পাদনা সাক্ষাৎকার গ্রন্থভুক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সৌম্য আমাদের হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন তার কাছে। কিন্তু অল্পদিন গতে তিনি পরলোক যান। তার হাতে সংকলনটি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের ‘স্বাধীন বাংলা’ পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক কেশব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন বন্ধু রবীন গুহ। উদারচিত্তে তিনি সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন। শিলাপাঠ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখক মিজান রহমানের নেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিয়েছেন চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী চৌধুরী ফাহাদ। মহামারির এই সংকটময় সময়ে বই প্রকাশের ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য চন্দ্রবিন্দু পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। বইয়ে সাক্ষ্য মিলবে চিন্তায় আর কথায় আহমদ ছফা একজন স্পষ্টবাদী লেখক। কারণ অপ্রিয় সত্য বলতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। ছিল না ট্যাবু কিংবা পিছুটান। ছিল সৎ সাহস আর ভাষার পরিমিতি বোধ। ছিল জটিল বিষয়কে সহজভাবে ব্যাখ্যা হাজির করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি ছিলেন মেরুদ- বর্গা দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আদতে আহমদ ছফা একজন আপাদমস্তক খাঁটি লেখক ও সহজ চিন্তাবিদ। আমাদের আশা, তার রচনাবলি আর কথামালা আরও অধিক পাঠক সমাদৃত হবে।
বড়ই আনন্দের বিষয় সংকলনে আমরা আহমদ ছফার পনেরোটি প্রতিকৃতি সন্নিবেশ করেছি। শিল্পের বিভিন্ন ফর্মে প্রতিকৃতিগুলো এঁকেছেন সমকালীন পনেরোজন তরুণ শিল্পী। তা সম্ভব হয়েছে শিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্য ও আবীর সোমের দৌলতে। বইয়ের সুন্দর প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্য। অত্যন্ত দরদ দিয়ে ছফাকে এঁকেছেন শিল্পীরা। বলা যায় স্বল্প সময়ে অসাধ্যকে সাধ্য করেছেন তারা। তাদের জন্য অটুট ভালোবাসা আর সাধুবাদ। আমরা ছফাকে নানা দিক থেকে জানা, দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। সংকলনভুক্ত আহমদ ছফা সাক্ষাৎকারে সাহিত্য থেকে সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে দর্শন, রাজনীতি থেকে ইতিহাস, প্রকৃতি থেকে মানুষ, কৃষি থেকে শিল্প, লড়াই সংগ্রাম থেকে মুক্তির প্রশ্ন, জনসমাজ থেকে মানব প্রকৃতির অন্তর্গত স্রোতোধারার বিশ্লেষণ জারি আছে। মতাদর্শিক তাড়না নয়, বাস্তবতার নিরিখে সত্যাদর্শে কলম সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। তার লেখার বড় আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন থাকা। তাতেই রচিত হয়েছে অতীত আর ভবিষ্যতের অমূল্য মেলবন্ধন। বাংলা সাহিত্যে সত্যিই তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান লেখক বিরল। -
“ছিঃ” শামীম রুনা
ছিঃ
শামীম রুনামোবাইল স্ক্রিনে অনলাইন নিউজ পড়তে পড়তে মাহমুদের গম্ভীর মুখের চামড়ার ভাঁজে সূক্ষ্ম সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে ওঠে। দেশের চলমান পৈশাচিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের মধ্যে প্রচ- ক্ষোভ কাজ করছে এখন। সবাই ধর্ষণ রোধের মিছিল বা মিটিংয়ে পথে না নামলেও যে পরিমাণ তরুণ প্রজন্ম নেমে এসেছে, সেটিও কম নয়। এখন এই মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। তাই এখন ওর আর ওর দলের অনেক কাজ, মানুষদের পথে আটকে রাখতে হবে, আন্দোলন জোরদার করতে হবে। মানুষ যত পথে নেমে আসবে, যত স্লোগান তুলবে, যত পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে সামনে এগোবে তত মাহমুদরা নিজের আধিপত্য বিস্তারের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও, এই আন্দোলন, মিছিল মিটিং করে কম পথ তো পাড়ি দেওয়া হলো না! প্রথমে মনে হয়েছিল, সরকারের বিরুদ্ধে, আইনের অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদে, প্রশাসনের স্বেচ্চাচারিতার বিরুদ্ধে, সমাজের নৈতিক স্খলনের প্রতিবাদে এই সব আন্দোলন করে কিছুই পাওয়া যাবে না; পুলিশের লাঠিপেটা আর হয়রানি ছাড়া।
শুরু সেই ২০১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি নিয়ে, শাহবাগে। যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ বিচার তো ওদের আন্দোলনের কারণে দ্রুত আর কার্যকর হয়েছিল। অবশ্য এক একটি যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির আনন্দ সংবাদের পর, ওদের খাসির বারবিকিউ পার্টি বা বিরিয়ানি সেলিব্রেট নিয়ে কিছু সুশীল মানুষের বিখাউজের চুলকানি উঠেছিল, ওসব ছিল ক্ষণকালীন। বিশাল আন্দোলনের পর কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি এলে পোলাপানরা যদি একটু আনন্দ না করে তাইলে কেমনে কী!আপন মনে ভাবে মাহমুদ।
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি, ব্লগার হত্যার বিচারসহ আরও কত বিচারের দাবি নিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ওরা রাস্তায় নেমেছে, সব আন্দোলন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু মাহমুদ নিজে সফল। এখন ও কোনো মিছিলের আয়োজন করলে কয়েক শ তরুণ-তরুণী শাহবাগে জড়ো হয়ে যায়, সংবাদপত্রে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধির স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতীক হিসেবে ওর ওপর আর্টিক্যাল ছাপা হয়, মধ্য রাতের টক শোর নির্দলীয় হেভিওয়েট বক্তা হিসেবে দর্শকদের প্রথম সারির পছন্দ। দুই দিন আগে, দেশের চলমান সংকট এবং ধর্ষণ নিয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল টিভিতে ওর দীর্ঘ জুম সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে। এত বড় কাভারেজের কারণে আন্তর্জাতিক পরিম-লে ওর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে নিঃসন্দেহে, সেই সঙ্গে দেশের অনেকের ঈর্ষার ব্যক্তিতেও পরিণত হয়েছে। এই সব অর্জন মাহমুদকে ভেতরে ভেতরে ভালো আর দম্ভের শিহরণ আর তৃপ্তি বোধ দেয়।
আবার, আজ একটি পত্রিকায় ধর্ষণ রোধে সমাজ এবং রাষ্ট্রের করণীয় এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে ওর লেখা একটি আর্টিক্যাল ছাপা হয়েছে। দেশের সচেতন নাগরিকরা তো বটে, প্রশাসনের লোকজন এবং সুশীল সমাজের টনকও নড়িয়ে দেওয়ার মতো হয়েছে লেখাটি। আর্টিক্যালের নিচে কমেন্ট বক্সে মন্তব্যের পর মন্তব্য আসছে, সেগুলো পড়তে পড়তে পরবর্তী আর্টিক্যালের খসড়া নিয়ে মনে মনে ভাবে মাহমুদ।
এ সময় পাশে রাখা সেলফোনটি মৃদু শব্দে বেজে উঠলে হাতে নিয়ে দেখে মাহমুদ, কোনো নাম নয়; বেশ বড় নম্বর। সম্ভবত দেশের বাইরের। দ্বিধা না করেই ফোনটি রিসিভ করে মাহমুদ।
হ্যালো, বলার পর ওপাশ থেকে কোনো প্রতিত্তোর শোনা যায় না। মাহমুদ আবার সফটলি হ্যালো বলে, আজকাল ওকে তো আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অনেকই ফোন করে, তেমন কোনো ফোনকল হয়তো।
কেমন আছো মাহমুদ? এবার একটি নারী কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে জানতে চায়। মাহমুদ কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারে না, কিন্তু ওপাশের কণ্ঠস্বরে অন্য রকম কিছু একটা আছে, যা মাহমুদকে অস্বস্তি বোধ দেয়। তারপরও সে ভারী আর মৃদুকণ্ঠে আবার জানতে চায়, কে বলছেন? সরি চিনতে পারছি না…
স্বর্ণা…মনে আছে? তো?
স্বর্ণা! মাহমুদের মনে হয় ওর পা দুটি যেন কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোতে চায় না, তারপরও ফ্যাসফ্যাসে স্বরে জানতে চায়, তুমি? তুমি এত দিন পর?
এত দিন পর মানে? তুমি তো আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চেয়েছ, তাই এত দিন পর এই প্রশ্ন কেন?
মানে?…এত দিন পর কী মনে করে?
তোমার সাথে আবার যোগাযোগ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তারপরও করতে বাধ্য হলাম, তোমার ইন্টারভিউ দেখে।
অ…হুম…
তুমি যা বলেছ তা কি তুমি বিশ্বাস করো?
অবশ্যই করি।
লজ্জা ধর্ষকের, ধর্ষিতার নয়। তাই আমাদের উচিত নয়, ধর্ষিতার দিক আঙুল তোলা বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। তাদের মানসিক বিপন্নতায় আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে মানবিক হওয়া। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাদের আশ্বস্ত করা, তুমি অশূচি নও, বরং যে তোমাকে আঘাত করেছে তারা অসুর। প্রত্যেক নারীর ভেতর দুর্গা বাস করে, অসুর বধ করাই দুর্গার কাজ। নারী তুমি দুর্গা হয়ে অসুর বধ করে নিজের পথে এগিয়ে যাও। একঘেয়ে স্বরে কথাগুলো আউড়িয়ে যায় স্বর্ণা, যেন মুখস্থ কোনো লেখা পড়ে শোনাচ্ছিল সে।
মাহমুদের কপালে তখন পাতলা ঘামের প্রলেপ। সে ইতস্তত স্বরে বলে, এসব কেনো বলছ? এসব কথায় তো কোনো সমস্যা নেই…
অবশ্যই সমস্যা নেই। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে যখন এই সব কথা বেরোয় তখন এসব কথা ফাঁকা বুলি আর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি, তুমি এসব কথার এক বিন্দুও হৃদয় থেকে অনুভব করো না। তুমি হলে হৃদয়হীন একজন ব্যক্তি। তারপরও এই সব আন্দোলন করছো শুধু নিজের পরিচিতির জন্য, তাই না? ধিক! ধিক তোমার ভাবনাকে!
শোনো স্বর্ণা…তখন আমার বয়স কম ছিল। আমি আসলে বুঝে উঠতেই পারিনি আমার কী করা উচিত ছিল। আমি জানি, তোমার পাশে না থেকে আমি ভয়ানক ভুল করেছিলাম।
ভুল! তোমার সে ভুল বাইশ বছর পরও ভাঙেনি, তাই না? এই বাইশ বছরে তুমি একবার আমার খোঁজ নিয়ে জানতে চেয়েছিলে, আমি কেমন আছি? আমার সঙ্গে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, তারপর একজন তরুণীর আত্মহত্যা করার কথা, ট্রমায় পড়ে যাবার কথা। সে সময় আমার একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন ছিল, অথচ সে সময় তুমি তোমার প্রেমিকার কাছ থেকে সটান সটকে পড়লে। একবারের জন্য ভাবলে না, আমি কি বেঁচে আছি না মরে গেছি।
সে সময়ে আমার অমন ব্যবহারের জন্য দুঃখিত…যেসব তরুণ-তরুণীদের নিয়ে তোমাদের আন্দোলন গড়ে তুলছ, এরা কিন্তু তোমার সেই বয়সটার থেকেও অনেক ছোট। কিন্তু দেখ, কী দারুণ ওদের সাহস। কেমন স্ফুলিঙ্গ ওদের ভেতর! আমার কী মনে হয় জানো? ওরা কখনো বন্ধুর হাত ছাড়বে না। ওদের সেই স্ফুলিঙ্গ কাজে লাগিয়ে তুমি মাহমুদ এখন তরুণদের প্রতিনিধি। হিপোক্রেট! বয়সের দোহাই দাও। বয়স দিয়ে কী আসে যায়। বিষয়টা হলো, মানবিকতা বোধের, দায়িত্ব বোধের, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর ভালোবাসার। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আস্থা আর বিশ্বাসের।
মাহমুদ কোনো কথা বলে না, স্বর্ণার কথাগুলো শুনতে শুনতে বাইশ বছর আগের এক বিকাল ওর মাথার মধ্যে ঝড় তোলে। এক কালো বিকালের কথা ওর মনে পড়ে যায়।
বাইশ বছর আগে, মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে রেজাল্টের অপেক্ষার পাশাপাশি চাকরির চেষ্টাও করছিল। আর স্বর্ণা হোমইকোনমিকসে মাস্টার্সের ছাত্রী। দুজনের দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক। কী এক অজানা কারণে, সে বিকালে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বাদ দিয়ে রিকশা করে চলে যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে পার্কের কিছুটা ভেতরের দিকেই চলে যায়। তখনো বিকাল ফুরায়নি, একপশলা বৃষ্টির পর চারিদিকের মায়াবী আলোছায়া আর সতেজ সবুজ গাছগাছালি মুগ্ধতা আনে। ঠিক তেমন সময়টি হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে ওদের ঘিরে, চার-পাঁচজন ছেলে ওদের ঘিরে ধরে। কিছু বোঝার আগেই দেখতে পায়, ছেলেগুলোর হাতে চকচকে ছুরি-চাক্কু, একজনের হাতে আবার পিস্তল। পিস্তলটি সোজা মাহমুদের ঘাড়ে চেপে ধরে একজন বলে, ভাইয়া; আপনি একটু এইখানে বসেন। এ্যাই তোরা দুইজন ভাইরে নিয়া বস তো…
মাহমুদ কি ওদের কথা শুনে প্রতিবাদ করেছিল তখন? ঠিক মনে পড়ে না, তবে ওর গালে, পেটে পটাপট কয়েকটি চড় ঘুষি এসে পড়েছিল। ও নাকের রক্ত মুছতে মুছতে দেখেছিল, দুই-তিনজন ছেলে স্বর্ণাকে টেনেহিঁচড়ে পাশের বড় ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। চোখের আড়াল হওয়ার আগে স্বর্ণার বিবর্ণ আর বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথমবার ভয়ানক অসহায় বোধ আর নিজের প্রতি ঘৃণা এসেছিল মাহমুদের।
স্বর্ণার সঙ্গে শেষ দেখা, ট্যাক্সি করে ওকে হোস্টেল গেটে নামিয়ে দেওয়ার সময়, মাহমুদ জানতে চেয়েছিল, ডাক্তারের কাছে যাবে কিনা? স্বর্ণা কোনো উত্তর না দিয়ে হোস্টেলে ঢুকে যায়।মাহমুদ দুই দিন হোস্টেলে নিজের রুমে শুয়ে কাটায়। তারপর নিজের গ্রামের বাড়ি গিয়া টানা দুই মাস পার করে তারপর একটি স্কলারশিপ নিয়ে থাইল্যান্ড চলে যায়। গ্রামের বাড়িতে থাকার সময়টা সে একবারও স্বর্ণার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেনি, বরং স্বর্ণার সঙ্গে যেন কোনো যোগাযোগ না হয় সে ব্যাপারে ছিল সতর্ক, কমন বন্ধুদের পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছিল। দুই বছর পর দেশে ফিরেও কখনো স্বর্ণার খোঁজ করেনি, তবে দু-একজনের মাধ্যমে উড়োধুড়ো জেনেছিল, স্বর্ণা ইউরোপে চলে গিয়েছে, ব্যস; এটুকুই।
মাঝে এতটা বছর পার হয়ে গেছে, যদিও দুজন মুখোমুখি নয়, তারপরও যেন মাহমুদ আজ স্বর্ণার মুখোমুখি। মাহমুদের বোধ হয়, ও শুধু স্বর্ণার মুখোমুখি নয়, বরং ওর সঙ্গে আন্দোলন করে যারা, একপাল সবুজ আর আগ্নেয়গিরির স্ফুলিঙ্গের মতো তারুণ্য, ও ওদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। ওর শরীর থেকে মেকি সম্ভ্রম প্রাচীন প্রসাদের পলেস্তারার মতো খসে খসে পড়েছে। এত দিনের লুকিয়ে রাখা ভেতরের গোপন জীর্ণতা সবার সামনে উন্মোচিত। ওদের সবাইর চোখে ধিক্কার! স্বর্ণা এখনো কথা বলে যাচ্ছে, মাহমুদের কানে আর কিছুই ঢোকে না, লজ্জায় লীন হতে হতে ওর কানে একটি শব্দ ধাক্কা দিয়ে ওর বাকি অস্তিত্বকেও ভেঙেচুরে দেয়, ছিঃ! -
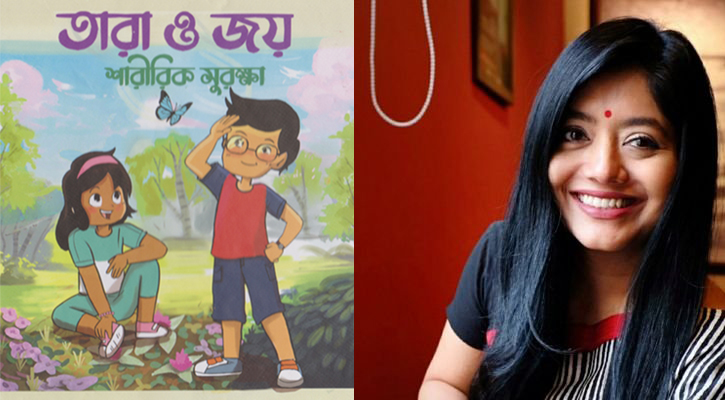
ফারিন দৌলাহ’র শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক বই
অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ফারিন দৌলাহর শিশু-শারীরিক সুরক্ষা বিষয়ক বই ‘তারা ও জয়’। ‘ওয়ান সার্কেল’ এর সহযোগিতায় ‘সেইবই’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বইটি।
বইটি সম্পর্কে লেখক ফারিন দৌলাহ বলেন, “শিশুর সামাজিকীকরণ, মানবিকতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো স্পর্শ। কিন্তু এই স্পর্শই কখনো কখনো শিশুর জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। খারাপ স্পর্শে শিশুকে দীর্ঘদিন অনিন্দ্রা আর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শিশু বড় হলে যৌনভীতি, সম্পর্কভীতি, আত্মনিন্দা, দ্বৈতব্যক্তিত্বসহ নানা ধরণের ডিসঅর্ডারেও ভুগে। এটা এত বেশি ট্রামাটিক।এই ভীতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে বেড়াতে পারে।”
শিশু সুরক্ষা নিয়ে বই লেখা কারণ নিয়ে ফারিন দৌলাহ বলেন, “পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখছি প্রতিদিন দেশের কোনোনা কোনো স্থানে শিশু নির্যাতিত হচ্ছে। সরকারি পাঠ্যসূচিতে বয়ঃসন্ধি নিয়ে অল্পবিস্তর সিলেবাস থাকলেও শিশুর শারীরিক সুরক্ষা নিয়ে কোনো বই নেই। বেসরকারি উদ্যোগেও কোনো বই প্রকাশ হচ্ছে না। তাই চেষ্টা করেছি এ নিয়ে লেখার।”
বইটির অলংকরণ করেছেন তাসনিয়া সাখাওয়াত অরণা। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় সংস্ককরণেই পাওয়া যাচ্ছে এই বইটি। প্রতিটি সংষ্ককরণের মূল্য রাখা হয়েছে ১৭৫ টাকা। -

নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ’র জন্মদিন আজ
আজ নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ’র ৭২তম জন্মদিন জন্মদিন। ১ ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুরে জন্মগ্রহণ করেন দুই বাংলার তুমুল জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। about:blank
তার জন্মদিনকে ঘিরে ভক্ত-অনুরাগীরা ভাসছেন স্মৃতির সাগরে। প্রিয় লেখকের নানা উক্তি, ছবি পোস্ট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এছাড়া বেশকিছু টিভি চ্যানেলে প্রচার হবে নানারকম অনুষ্ঠান। জন্মদিন উপলক্ষে হুমায়ূন আহমেদের পরিবারের পক্ষ থেকেও নেয়া হয়েছে কিছু উদ্যোগ। লেখকের নিজের হাতে গড়া নুহাশপল্লীতে তার সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হবে।
বাংলা সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও গান পালাবদলের এ কারিগর ১৯৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ‘নন্দিত নরকে’ দিয়ে সাহিত্য জগতে পা রাখেন। এরপর তিন শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন তিন। যার সবগুলোই পাঠকনন্দিত।
১৯৯০-এর গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। তার পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র ‘আগুনের পরশমণি’ মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালে। বদলে দেন নির্মাণের বাঁক। ২০০০ সালে ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ ও ২০০১ সালে ‘দুই দুয়ারী’ দর্শকের কাছে দারুণ গ্রহণযোগ্যতা পায়। ২০০৩-এ নির্মাণ করেন ‘চন্দ্রকথা’।
১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে নির্মাণ করেন ‘শ্যামলছায়া’ সিনেমাটি। এটি ২০০৬ সালে ‘সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র’ বিভাগে একাডেমি পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এছাড়াও এটি কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এরপর ২০০৬ সালে মুক্তি পায় ‘৯ নম্বর বিপদ সংকেত’। ২০০৮-এ ‘আমার আছে জল’ চলচ্চিত্রটি তিনি পরিচালনা করেন। ২০১২ সালে তার পরিচালনার সর্বশেষ ছবি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ মুক্তি পায়।
টেলিভিশন নাটকেও চমক দেখিয়েছেন তিনি। কখনো চিত্রনাট্যে কখনোবা নির্মাণে তিনি উপহার দিয়েছেন ‘এইসব দিনরাত্রি’, ‘অয়োময়’, ‘বহুব্রীহি’, ‘কোথাও কেউ নেই’, ‘আজ রবিবার’, ‘নক্ষত্রের রাত’, ‘উড়ে যায় বকপক্ষী’, ‘কালা কইতর’, ‘সবুজ ছায়া’র মতো ধারাবাহিকগুলো। আর অসংখ্য খণ্ড নাটক আজও তাকে এদেশের সেরা নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে কিংবদন্তি করে রেখেছে।
কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। তবে হুমায়ূন আহমেদ সর্বজনপ্রিয় হয়ে আছেন হিমু ও মিসির আলী চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে। এছাড়াও তাকে বলা হয় তারকা গড়ার কারিগর। তার হাত ধরে অনেক অভিনয় ও সঙ্গীতশিল্পীরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।
হুমায়ূন আহমেদের বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দোসরদের হাতে শহীদ হন। মায়ের নাম আয়েশা ফয়েজ। তার দুই ভাই মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও আহসান হাবীব। প্রত্যেককেই লেখালেখিতে পাওয়া গেছে।
হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন অভিনয়, নৃত্যের পাশাপাশি পরিচালক হিসেবেও প্রশংসিত। তার সংসারে নিনিত ও নিষাদ নামে দুই পুত্রের জনক হুমায়ূন আহমেদ। অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে প্রথম স্ত্রী গুলতেকিনের বিচ্ছেদ হয় ২০০৩ সালে। তাদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর সাত বছর পর গেল বছর বিয়ে করেছেন গুলতেকিন।
-

সে কোন সাধনা
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল’, কিংবা ‘আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’— জনপ্রিয় এই শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। লিখেছেন আগমনি, দুর্গাস্তুতি, পদাবলি, কীর্তনও। গীতিকার, সুরকারের ধর্ম যে ভিন্ন, তা কখনও কেউ খেয়ালও করেনি— এটাই চিরকাল বাঙালির ধর্মীয় সঙ্গীত-জগতের ঐতিহ্য। ‘মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়’ নজরুলের আর একটি বিখ্যাত গান। গানগুলির কথা শুনলেই বোঝা যায়, হিন্দু শাস্ত্র ও ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞান ও অনুভব ছিল তাঁর।
আর এক মুসলিম গায়ক শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মহম্মদ কাসেম। তিনি অবশ্য শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন, কে মল্লিক ছদ্মনামে। অনায়াসে, অন্তরের মাধুর্য ঢেলে তিনি গেয়েছিলেন, ‘দুঃখহরা তারা নাম তোমার, তাই ডাকি মা বারবার’, কিংবা, ‘আনন্দময়ী শ্যামা মা’কে আমি বড় ভালবাসি, হৃদয়ে উদয়া হলে হরজায়া কাজ কী আর আমার গয়া-বারাণসী।’ নজরুলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কাসেম, জন্ম ১৮৮৮-তে। বর্ধমানের আদি বাসিন্দা, কলকাতায় থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। বাড়ির মালিক মল্লিকদের পদবি নিয়েছিলেন। তাঁর গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত, আগমনি গান আজও সাক্ষ্য বহন করে যে, সঙ্গীত-জগতে ধর্মের ভেদাভেদ অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। ধ্রুপদী সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ‘আল্লা জানে, মৌলা জানে’ বন্দিশ যেমন হিন্দু ছাত্রেরা শিখেছে ও গেয়েছে, তেমনই আমির খান গেয়েছেন মালকোশের বিলম্বিত বন্দিশ ‘পাগলাগন দে মহারাজ কুঁয়ার’। বড়ে গুলাম আলি খান গেয়েছেন ভজন, ‘হরি ওম তৎসৎ’।
মানবজমিন
সনাতন পাল: কালীপুজো এলেই যাঁর নাম মনে আসে, তিনি শাক্ত কবি তথা সাধক রামপ্রসাদ সেন। তাঁর ভক্তিগীতিই ‘রামপ্রসাদী’ নামে পরিচিত। জন্ম সম্ভবত ১৭১৭-১৭২৩ সালের মধ্যে কোনও এক সময়ে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি এবং হিন্দি— এই চারটি ভাষা খুব ভাল করে রপ্ত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।
বাবার মৃত্যুর পরে রামপ্রসাদ কেরানির কাজ নেন। হিসাবের খাতায় ভক্তিগীতি লিখতেন। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রামপ্রসাদকে বিনা কর-এ ১০০ একর জমিও দান করেছিলেন। রামপ্রসাদ তঁার বিখ্যাত কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ কৃষ্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধারা বাউল ও বৈষ্ণব কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন সুরের সৃষ্টি করেন, যা ‘রামপ্রসাদী’ সুর নামে প্রচলিত।
এই সুরে পরবর্তী তিন শতাব্দী গান রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামও রামপ্রসাদী সুরে গীতিরচনা করেছেন।
তাঁর গানে কেবল ভাবাবেগই ছিল না, ফুটে উঠেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছোঁয়া, মানুষের আর্থিক দুরবস্থা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের কথা। রামপ্রসাদ সেনের বহু জনপ্রিয় গানের মধ্যে একটি হল, ‘মন রে কৃষিকাজ জানো না, এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।’ আজকের দিনে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিতেও এমন ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
নাথপন্থী
ভাস্কর দেবনাথ: কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দু পূজারি ব্রাহ্মণদের জন্য এক হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেছে। এই বাংলা তথা ভারতে এমনও সম্প্রদায় রয়েছে, যা সুদীর্ঘ কাল ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। নাথপন্থী সম্প্রদায়ের কত মঠ-মন্দির যে বেহাত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। সেই সময়ে বঙ্গদেশে পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন।
কথিত আছে, কালীঘাটের মা কালীর প্রতিষ্ঠা করেন নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথ। হুগলির মহানাদে আছে জটেশ্বরনাথ শিবমন্দির, যেখানে আজও নাথপন্থী সেবায়েতগণ পরম্পরা মেনে পূজা করে আসছেন। নাথ সাধকেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। আজও বঙ্গের অনেক স্থানে নাথ-যোগী দাদা গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘মাছলন্দি পির’ নামে পূজিত হন। নিরাকার নিরঞ্জন এবং ধর্ম ঠাকুরের মিশ্রণের ফল হিসেবে উঠে এসেছিল লোকায়ত গ্রাম্য দেবতা ‘পঞ্চানন্দ’, যিনি পরবর্তীতে মহাদেবের সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। মধ্যযুগের সমন্বয়ের এই আবহে ধর্মঠাকুর বা পঞ্চানন্দ দেবতার পূজারি হিসেবে নাথ-যোগী সেবায়েতদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল সমাজের সর্বস্তরে। পূজার মন্ত্রেও ব্রাহ্মণ্যবাদী ছোঁয়া ছিল নামমাত্র। বরং নির্দ্বিধায় যবন শব্দ স্থান করে নিয়েছিল পূজামন্ত্রে।
আজকাল দলিত সাহিত্য চর্চা এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। চর্যাপদের যুগ থেকেই এই নাথপন্থী সম্প্রদায়ের সাহিত্য সাধনার খবর মেলে। মীননাথকে ‘বাংলা ভাষার প্রথম কবি’ বলেছেন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ড. শহিদুল্লাহ। কল্যাণী মল্লিকের সুবৃহৎ গবেষণাধর্মী নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী বইতে নাথ সম্প্রদায়ের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। নাথ ধর্মের বিকাশ বঙ্গদেশ থেকেই। আজ এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
মানুষই বড়
পৃথা কুন্ডু: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে অজয় করের পরিচালনায় সপ্তপদী মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬১ সালের অক্টোবরে। এ বছর ৬০ বছরে পা দিল ছবিটি। শুধু একটি জনপ্রিয় কাহিনিচিত্র হিসেবেই নয়, এই ছবি স্মরণীয় বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী বার্তার জন্য। সাহেব-মেমরা বাঙালি আবাসিক ছাত্রদের পড়াশোনার অসুবিধেকে অগ্রাহ্য করে তারস্বরে ‘অন দ্য মেরি গো রাউন্ড’ গাইতে থাকলে, খোল-করতাল সহযোগে ‘এ বার কালী তোমায় খাব’ গেয়ে জবাব দিতে ভোলে না কৃষ্ণেন্দু আর তার বন্ধুরা। হাসি-তামাশার আঙ্গিকে উপস্থাপিত হলেও, এই সব দৃশ্যে প্রতিবাদের স্বর চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কলেজের অনুষ্ঠানে সেই ‘ব্ল্যাকি’ কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গেই ওথেলো নাটকে অভিনয় করতে হয় রিনাকে। মনে রাখতে হবে, ওথেলো নাটকের বার্তা কিন্তু বর্ণবিদ্বেষকে ঘিরেই।
ছবিতে শেষ পর্যন্ত জন্মপরিচয়, ধর্ম নয়, মানুষই বড় হয়ে ওঠে। শেষে গির্জা-সঙ্গীতের সঙ্গে দূরে মিলিয়ে যায় চরিত্র দু’টি, কিন্তু এখানে গির্জা থেকে ভেসে আসা সুর কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতীক নয়, বরং তা অনেক বেশি করে হয়ে ওঠে মনুষ্যত্বের, ভালবাসার চিরন্তন সঙ্গীত। আবহে অসামান্য কাজ করেছেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণেন্দু যখন ধর্মান্তরিত হয় আর রিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, আবহে মন্দিরের ঘণ্টা মিশে যায় গির্জার ঘণ্টায়। এই সুরেই যেন বাণীরূপ পায় ছবির মূল কথাটি— “মানুষের মধ্যে যে জীবন, সে যেখান থেকেই সৃষ্টি হোক, সেখানে ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, হিদেন নেই। সবার মধ্যে, সমান মহিমায় ভগবান আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল।” আজকের দিনেও সমাজ, ধর্ম, জন্ম, কর্ম— সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে এই মনুষ্যত্বের, সম্প্রীতির বোধ একই রকম প্রাসঙ্গিক।
এই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তমকুমার, আর সুচিত্রা সেনও পেয়েছিলেন মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। সর্বোপরি, জাতীয় স্তরে এই ছবিটি পেয়েছিল বাংলা ভাষায় ‘দ্বিতীয় সেরা’ কাহিনিচিত্রের মর্যাদা।
-
বৌদির দেওয়া ৫০ টাকা
আবুল কাসেম
এটা ছিল জীবনের তৃতীয় পতন। ব্যবসা লাটে উঠেছে। উঠবেইনা কেনো – ব্যবসা চালাতে যে ধৈর্য্য আর অভিজ্ঞতা দরকার, তা আমার ছিলনা কখনো। তাছাড়া এতগুলো টাকা মেরে দিয়ে লাপাত্তা হওয়ার ধকল সইবার ক্ষমতাও ছিলনা আমার। বিশ পেরোনের আগেই পারিবারিকভাবে বিয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক বালিকা। কয়েকদিনেই বুঝলাম, ছি-কুতকুত আর দড়ি-খেলাই যখন তার প্রিয় কাজ হওয়ার কথা,তখন এই সঙের কাজ, সত্যিই বেমানান এই মিষ্টি বালিকাটির জন্য। আমি তাকে স্বাধীনতা দিলেও রেলস্টেশনে এসে নৌকায় চড়ে ঘুরতে চাওয়া-তো আর হয়না। একদিনতো তার কথা শুনে আমি হতবাক। ’ দিনে দু’শ টাকা বিক্রি হয় দোকানে?’ কোন ধারণা আর চিন্তা থেকে সে এই প্রশ্ন করেছিল, আজো আমি এই প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করি। একপর্যায়ে সেনাবাহিনী থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া জনৈক ভদ্রলোকের কাছে দোকান বিক্রি করে দিলাম। যে টাকাগুলো পেলাম, সবটাই ভাইকে দিয়ে দিতে হলো। কপর্দকহীন অবস্থায় আবারও পদযাত্রা। চাল কিনলাম বাকিতে। গ্রামে বেশ কিছু জমি-জমা ছিল। পুরোটাই ডুবানো। জলাবদ্ধতা আর নদী ভাঙনে কত জমি-জমাওয়ালা মানুষকে যে ভিখেরি করেছে, তার হিসেব কে জানে। দুর্শ্চিতা দূর করতে কাজে ডুবে যাওয়া প্রয়োজন। ডেল কার্নেগীর এই উক্তি বারবার মনে উকি মারছিল। আধা-শিক্ষিত বেকার তরুণদের আর কিইবা করার আছে, টিউশনি করা ছাড়া। কোথায় যেন পড়েছিলাম, নিজ স্বপ্নের চারা বড় করার সময়ে নামমাত্র মূল্যে অন্যের স্বপ্নবীজ সত্য করার নামই টিউশনি। তবুও বেকারদের একমাত্র অবলম্বন এটা। শুরু করলাম পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে দিয়ে। তবে টিউশনি করার সুখস্বপ্ন আমার নিমিষেই কেটে গিয়েছিল, যখন সে বিজ্ঞের মত সব বোঝার ভান করত। অথচ কিছু ধরলে হা করে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে আবার হাসিও পেত, যখন সে কিছু বুঝলেই হাতে তুড়ি মেরে ‘চন্ট’ বলে চেচিয়ে উঠত। সামান্য আয়ে সংসার যেন আর চলেনা। এমনও হয়েছে দু’টাকায় পঞ্চাশ গ্রাম ডাল কিনে দু’দিন চালাতে হয়েছে। খুবই খারাপ লাগত বালিকা বউটির জন্য। নিজের অসহায়ত্বে মনে হতো লজ্জা পেয়ে পাতা কুকড়িয়ে যাচ্ছে বাড়ির সামনে থাকা পেয়ারা গাছটির। আবারো পড়া-লেখা শুরু করলাম। ছোট বেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী বলে স্বীকৃতি ছিল। ইংরেজিতে অনার্স পড়তাম। তবে জীবন ধ্বংস হয়েছে ছাত্ররাজনীতির কারণে। ছোট বেলা থেকে আমার একটা বৈশিষ্ট ছিল। আমি যা করি-খুবই মনোযোগ দিয়ে করি। পড়তে বসেছি একদিন-এমন সময় আমার বিবাহিতা ছোট বোন বেড়াতে এসে আমাকে ডাকছে। অনেক দিন পর সে বেড়াতে এসেছে। আমি তার ডাকের উত্তরে “হ্যা-হ্যা” করেই যাচ্ছি। অথচ আমার খেয়াল নেই, আমার অতি আদরের ছোট বোন এসেছে। এভাবেই গড়াতে লাগল দিন। সারাদিন বিরামহীন পথচলা আর রাতে ক্লান্তিহীন লেখাপড়া। সামনে বিএসএস পরীক্ষার ফর্ম-ফিল-আপ। সঠিক হিসেব নেই। তবে হাজার চারেকের কম হবেনা। কিভাবে এত টাকা ম্যানেজ করব-বুঝে উঠতে পারছিনা। ধার-কর্জ করাটা ঠিক আমার দিয়ে হয়না। তাছাড়া চাইব-বা কার কাছে। চলার পথে আমার নীতিটা এমন-না থাকে-খাবনা, হাত পেতে রাজভোগ ভক্ষণ, আমার দিয়ে হবেনা। অবশেষে চোখ পড়ল,বউয়ের কানের দুল আর চেইনের ওপর। মুখ কাচু-মাচু করে বলতেই সে খুলে দিল। তবে তার চোখের কোনে ঈষৎ জমা জল আমার বুকে সাগরের বিশাল জলরাশির ধাক্কা দিচ্ছিল। হায়রে বাঙ্গালী নারী,পৃথিবীর শ্রেষ্ট নারী। এরাই পারে,হাড়ির ওপরের খাবার পরিবারের মাঝে সবটুকু বিলিয়ে, তলার তেলকাষ্টে খেয়ে তৃপ্তিতে থাকতে। গহনা বন্ধকের টাকায় ফর্ম-ফিল-আপ করে আসলাম। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। যশোরে থাকার জায়গা নেই। হোটেলে থাকার পয়সা নেই। অগত্য বাড়ি থেকেই যেতে হলো। দু’একদিন এমন হয়েছে-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা-ঘন্টা পরে পৌছেছি। দেখতে দেখতে তিন মাস পার। আগামী কাল পরীক্ষার রেজাল্ট। উদ্বেগের জমাটটা ভারী হতে লাগল। যশোরে যাওয়ার টাকা নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম বাসে উঠে ভাড়া দেবনা। দাঁড়িয়ে যাব। সকালে প্রতিবেশিদের কাছে দোয়া চাইতে গেলাম। প্রথমেই বৌদিদের বাড়ি গেলাম। আমি উনাকে বেশ সমীহ করতাম। চালচলনে গম্ভীরতা কিন্তু আচরণে বিনয়ীভাব উনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছিল। তাছাড়া উনি বড় ছিলেন বলে ছোট সব বোনদের নিজের কাছে রেখে পড়ালেখা শিখিয়ে সুপাত্রে পাত্রস্থ করেছিলেন। চাকরির মধ্যেও বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা-যত্নের এতটুকু কমতি ছিলনা তার। বাংলার ঘরে ঘরে এমন মেয়ে জন্মালে কেউ ছেলের আশায় ৪/৫টি মেয়ে জন্ম দিতেন না। আশীর্বাদ চাইতেই , “তোমার জন্য আশীর্বাদ আমার ঠাকুরের ঘরে তোলা, বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, এটা রাখো, যশোরে যেতে কাজে লাগবে। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জ¦ল ছল-ছলিয়ে উঠল। সকালের মিষ্টি রোদ ওই জলে লেগে চিক-চিক করে উঠেছিল কিনা জানিনা। তবে হৃদয়ের গহীনে এই কৃতজ্ঞতা শক্ত পাথরে আকীর্ণ হয়ে রলো। অফিসের সামনে নোটিশ বোর্ডে ফলাফল সাটানো। প্রচণ্ড ভীড়। দেরি না করে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। একপর্যায়ে সুযোগ মিলল রেজাল্ট দেখার। দ্বিতীয় বিভাগের সব রোল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। এক পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগের রোলগুলোও মিলিয়ে নিলাম। কোথাও নেই। পেছনে দাঁড়ানো ফলপ্রার্থীদের চাপে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। ঘাসের ওপর থপাস করে বসে পড়লাম। মাথাটা পোপো করে ঘুরছিল, নাকি পৃথিবী আমাকে ঘিরে ঘুরছিল, বুঝতে পারলাম না। নিজেকে অপদার্থ আর অসার মনে হতে লাগল। আর মনে পড়তে লাগল স্ত্রীর গহনা আর বৌদির দেয়া ৫০ টাকা। মানতে পারছিলাম না। আবারও উঠে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটিশ বোর্ডের কাছে গেলাম। এবার নীচ থেকে দেখতে লাগলাম। তৃতীয় শ্রেণি; নেই। দ্বিতীয় শ্রেণি ; না, তাতেও নেই। হঠাৎ চোখ আটকে গেল নোটিশ বোর্ডে একেবারে ওপরের কোণে। চোখতো ছানা-বড়া! একি! ১০৪৭৬৩-প্রথম বিভাগ। একটাই রোল। আমি কয়েকবার নম্বর মিলিয়ে নিলাম। ঝাপসা প্রিন্টের অস্পষ্ট নম্বর তখন যেন জলজল করে আমার চোখে চোখ রেখে বলছে,দোস্ত,আমি এখানে। সত্যি বলতে কি ৩ লাখ ৮৪ হাজার কি:মি: দুরের ওই চাঁদটা সেদিন মধ্যদুপুরে এসেছিল আমার হাতের মুঠোয়। কোটি কোটি টাকা আমার না থাকলেও এখন বেশ স্বচ্ছলতা রয়েছে আমার। তবুও হৃদয় মানসে শ্রদ্ধার সাথে গেঁথে রয়েছে সেই ৫০ টাকা। বৌদির দেওয়া ৫০ টাকা।
-

করোনা থেকে সুস্থ হলেন বিখ্যাত লেখিকা রাউলিং
জে কে রাউলিং। নামেই যার পরিচয়। দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি তার। বিখ্যাত হ্যারি পটার সিরিজের লেখক তিনি। সম্প্রতি তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
তবে ভালো খবর হলো তিনি করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) স্কাই নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই সপ্তাহ ধরে করোনাভাইরাসে ভুগছিলেন জে কে রাউলিং। তবে এখন তিনি সুস্থ।
এক টুইট বার্তায় জে কে রাউলিং বলেন, ‘আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। দুই সপ্তাহ আমি করোনাভাইরাসের লক্ষণে ভুগেছি, কিন্তু পরীক্ষা করাইনি।’
টুইট বার্তায় তিনি একটি লিংক শেয়ার করে লিখেছেন, ‘দয়া করে এটি দেখুন, কুইন্স হসপিটাল ব্যাখ্যা করেছে কীভাবে এটি অনুশীলন করলে শ্বাস-প্রশ্বাসগত সমস্যা থেকে আরোগ্য পাওয়া যায়। এ কৌশল আমার সুস্থতায় খুবই সহায়ক হয়েছে। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।’
জে কে রাউলিং বলেন, ‘আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। আপনাদের সঙ্গে সেই কৌশলই শেয়ার করলাম, যা আমার ডাক্তার আমাকে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য কোনো বাড়তি খরচ নেই। নেই ক্ষতিকর প্রভাবও। সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন।
-

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে, ১৮৬১ – ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ – ২২শে শ্রাবণ,
১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, গীতিকার, সুরকার,
নাট্যকার ও দার্শনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন।
তিনি তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি প্রথম এশীয় হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তার সারা জীবনের কর্মে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তিনি বিশ্বকবি, কবিগুরু ও গুরুদেব নামে পরিচিত। তিনি বিশ্বের
একমাত্র কবি যিনি দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জন গণ মন উভয়টির রচয়িতাই রবীন্দ্রনাথ। বলা যায় তাঁর হাতে বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য,শিল্পকলা ও শিল্প চেতনা নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।
কলকাতার পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছিলেন মাত্র আট বছর বয়সে। ১৮৭৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম ছোট গল্প এবং নাটক লিখেন। এর আগেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত কাব্যের জন্ম দিয়েছিলেন যা ভানুসিংহ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।পারিবারিক শিক্ষা, শিলাইদহের জীবন এবং প্রচুর ভ্রমণ তাকে প্রথাবিরুদ্ধ এবং প্রয়োগবাদী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তিনি ব্রিটিশ রাজের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তার পুরো পরিবারের পতন এবং বাংলার বিভক্তিরেখার নিদর্শন তাকে দেখতে হয়েছিল। এদিক থেকে তার জীবনকে দুঃখী বলতেই হয়।
কিন্তু তার কবিতা, অন্যান্য সাহিত্য আর বিশ্বভারতী প্রতিণ্ঠা তার জীবনকে যে মহিমা দান করেছে তা আজীবন হয়তোবা টিকে থাকবে।
প্রাথমিক জীবন (১৮৬১–১৯০১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদা দেবীর ১৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন ১৩তম। জন্মের সময় তার ডাক নাম রাখা হয় রবি। ১১ বছর বয়সে তার উপনয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি ১৪ তারিখে ঠাকুর তার বাবার সাথে কলকাতা ত্যাগ করেন ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যান তারা। এর মধ্যে ছিল শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথের
নিজস্ব সম্পত্তি, অমৃতসর এবং হিমালয় অধ্যুষিত পাহাড়ি স্টেশন ডালহৌসি। সেখানে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী পড়েন, অধ্যয়ন করেন ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত। এছাড়াও তিনি কালিদাসের ধ্রুপদি কাব্যের সাথে পরিচিত হন ও এর বিভিন্ন পর্যালোচনা করেন .১৮৭৭ সনে তিনি প্রথম জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করেন। কারণ এ সময়েই তার কিছু সাহিত্যকর্ম প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্য ছিল মৈথিলি ভাষার সাংস্কৃতিক আদলে রচিত কিছু সুদীর্ঘ কবিতা। এ ধরণের কবিতা প্রথম লিখেছিলেন কবি বিদ্যাপতি। এই কবিতাগুলো সম্বন্ধে কৌতুক করে তিনি একবার বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে ভানুসিংহের (সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি যার নাম অনেক পরে পরিচিতি লাভ করেছে) হারিয়ে যাওয়া কাব্য সংগ্রহ। একই বছর তিনি লিখেন ভিখারিনী যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোট গল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৮৮২ সনে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যা সংগীত প্রকাশিত
হয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নামক বিখ্যাত কবিতাটি।
১৮৭৮ সনে ব্যারিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। তাকে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে পড়াশোনা করেন। কিন্তু ১৮৮০ সনে কোন ডিগ্রি লাভ ছাড়াই তিনি বঙ্গে ফিরে আসেন। ১৮৮৩
সনে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন বিয়ের সময় যাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। জন্মের
সময় মৃণালিনীর ডাক নাম ছিল ভবতারিণী (১৮৭৩ – ১৯০২)। তাঁদের পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়েছিল যাদের মধ্যে ২ জন শিশুকালেই মারা যায়।১৮৯০ সাল থেকে ঠাকুর শিলাইদহে তার বাবার সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। ১৮৯৮ সালে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা শিলাইদহে তাঁর সাথে যোগ দেয়। সেই সময় জমিদার বাবু নামে পরিচিত রবি ঠাকুর, পরিবারের আরামদায়ক জীবন ত্যাগ করে পদ্মার কোল জুড়ে বিপুল পরিমাণ এলাকা ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তার ভূমিতে বসবাসকারী গ্রাম্য অধিবাসীদের কাছ
থেকে খাজনা আদায় এবং তাদের সাথে কথা বলে আশীর্বাদ করা। বিভিন্ন স্থানে তার সম্মানে গ্রামের
লোকেরা উৎসবের আয়োজন করতো। এই বছরগুলোতে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো গল্প রচনা করেন। তাঁর তিন খণ্ডে রচিত বিখ্যাত গল্প সংকলন গল্পগুচ্ছের (যাতে মোট
৮৪টি ছোট গল্প রয়েছে) প্রায় অর্ধেক গল্প
এখানে থাকা অবস্থাতেই রচনা করেছেন। এই গল্পগুলোতে ব্যঙ্গ এবং আবেগের
সমন্বয়ে গ্রাম বাংলার সঠিক চিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।
শান্তিনিকেতন (১৯০১-১৯৩২) ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের
উদ্দেশ্যে শিলাইদহ ছেড়ে যান। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন মূলত একটি আশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যে। এই আশ্রমে তিনি গড়ে তোলেন একটি মার্বেল পাথরের মেঝেবিশিষ্ট মন্দির, একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়, বাগান এবং গ্রন্থাগার। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মৃত্যু ঘটে। ১৯০৫ সনের জানুয়ারি ১৯ তারিখে তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি মাসিক ভাতা ও বেতন পেতে শুরু করেন। এছাড়াও তিনি ত্রিপুরার মহারাজা, পারিবারিক গহনার
ব্যবসা, পুরিতে অবস্থিত বাংলো এবং নিজ সাহিত্যকর্মের সম্মানী; এই উৎসগুলো থেকে অর্থ পেতেন। প্রকাশনার সম্মানী হিসেবে তিনি প্রায় ২,০০০ টাকা পেতেন। এসময় তার সাহিত্যকর্ম দেশে-
বিদেশে বিপুল পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর ১৯০১ সনে নৈবেদ্য এবং ১৯০৬ সনে প্রকাশ করেন কাব্যগ্রন্থ খেয়া। একই সাথে তার কবিতাগুলোকে free verse-এ রূপান্তরের
কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৩ সনের নভেম্বর ১৪ তারিখে তিনি জানতে পারেন,
যে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
সুয়েডীয় একাডেমির ভাষ্যমতে তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করার কারণ তুলে ধরে। তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে মূল ভূমিকা ছিল তারই লেখা গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের সফল
ইংরেজি অনুবাদ যার ফলে পাশ্চাত্যের পাঠকেরাও তার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়েছে।
১৯২১ সালে ঠাকুর কৃষি অর্থনীতিবিদ লিওনার্ড কে এল্মহার্স্টের সাথে মিলে শান্তিনিকেতনের
নিকটে অবস্থিত সুরুল নামক গ্রামে পল্লী পুনর্নিমাণ সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন শ্রীনিকেতন। এই শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বরাজ আন্দোলনের একটি বিকল্প
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ
থেকে বিদ্বান ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহায্য
নিয়ে এখানে গ্রামের মানুষদের জন্য
বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত করেন
এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ
ঘটানোর প্রয়াস নেন। ১৯৩০-এর
দশকে তিনি ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক
বর্ণবিভেদ এবং বর্ণে বর্ণে ধরা-ছোঁয়ার
নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মতামত প্রচার শুরু করেন।
তিনি এই বর্ণবিভেদের বিপক্ষে বক্তৃতা,
কবিতা রচনা, বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে নাটক
রচনা এবং কেরালার একটি মন্দিরে এই
প্রথা ত্যাগের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তার
আন্দোলন পরিচালনা করেন। মূলত দলিতদের
সাধারণ সমাজে অবাধ প্রবেশাধিকারের সুযোগ
করে দেয়াই ছিল তার লক্ষ্য।
জনপ্রিয়তার বছরগুলোতে (১৯৩২-১৯৪১)
(মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪০
সাল)
জীবনের শেষ দশকের পুরোটা রবীন্দ্রনাথ
জনসমক্ষে ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এসময়
ছিল তুঙ্গে। ১৯৩৪ সালের ১৫
জানুয়ারি ভারতের বিহার রাজ্যে সংঘটিত
প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প
সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন
যে, এটি দলিতদেরকে বশীভূত করার জন্য
ঈশ্বরের একটি প্রতিশোধ। রবীন্দ্রনাথ এই
মন্তব্যের জন্য গান্ধীকে জনসমক্ষে তিরস্কার
করেন। এছাড়া বঙ্গের আর্থসামাজিক
অবস্থার অবনতি এবং কলকাতায় দরিদ্রতার
প্রাদুর্ভাবের কারণে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ
করেন। ১০০ লাইনের একটি মিত্রাক্ষর বর্জিত
কবিতায় তিরি তার এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ
ঘটান। দ্বিমুখী চিন্তাধারাকে ঝলসে দেয়ার এই
কৌশল পরবর্তিতে সত্যজিত রায় পরিচালিত
অপুর সংসার নামক চলচ্চিত্রে অনুসৃত হয়।
রবীন্দ্রনাথ এসময় তার লেখার সংকলন
১৫টি খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই সংকলনের
অন্তর্ভুক্ত ছিল পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক
(১৯৩৫) এবং পাত্রপুট (১৯৩৬)। তিনি prose-
songs এবং নৃত্যনাট্য রচনার মাধ্যমে তার
বিভিন্ন পরীক্ণ চালিয়ে যেতে থাকেন যার
মধ্যে রয়েছে “‘চিত্রঙ্গদা” (১৯১৪),
“শ্যামা” (১৯৩৯) এবং “চণ্ডালিকা” (১৯৩৮)।
এসময়ে রচিত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে “দুই
বোন” (১৯৩৩), “মালঞ্চ” (১৯৩৪) এবং “চার
অধ্যায়” (১৯৩৪)। জীবনের শেষ
বছরগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি বিশেষ
আগ্রহের পরিচয় দেন যার প্রমাণ তার রচিত
“বিশ্ব পরিচয়” (১৯৩৭) নামক একটি প্রবন্ধ
সংকলন। তিনি জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান
এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন,
তার সে সময়কার
কবিতা এবং সাহিত্যকর্মে বিজ্ঞানের
প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তার
বোধগম্যতা আমাদেরকে সে প্রমাণই দেয়। এই
সাহিত্যকর্মে উচ্চমানের প্রকৃতিবাদ
পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন
গল্পে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন
যার মধ্যে রয়েছে, “সে” (১৯৩৭), “তিন
সঙ্গী” (১৯৪০) এবং “গল্পসল্প” (১৯৪১)।
জীবনের শেষ চার বছর রবীন্দ্রনাথের শরীরের
বিভিন্ন স্থানে ব্যথা ছিল এবং তার এই
দুরারোগ্য অসুস্থতা মোট দুই বছর বজায়
ছিল। ১৯৩৭ সালের শেষ
দিকে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং এরপর
দীর্ঘ সময় মুমূর্ষু অবস্থায় কোমায় ছিলেন।
তিন বছর পর ১৯৪০ সালে আরেকবার ভাল
রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন যা থেকে আর
আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। এসময় রচিত
কবিতাগুলো তার জীবনের অন্যতম প্রধান
রচনা হিসেবে খ্যাত কারণ এর মধ্যে মৃত্যু
দুয়ারে তার পদচারণার আভাস প্রস্ফুটিত
হয়েছিল। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৪১ সালের
৭ আগস্ট তারিখে (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)
জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির উপর তলার
একটি কক্ষে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘরেই
তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তার
মৃত্যুবার্ষিকী এখনও বিশ্বের সকল প্রান্তের
বাংলাভাষীরা বিশেষ ভাবগাম্ভীর্যের
সাথে পালন করে থাকে।
ভ্রমণসমূহ
(চীনের
সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৪
সাল)
ঠাকুরের ভ্রমণের নেশা ছিল প্রখর। ১৮৭৮
থেকে ১৯৩২ সনের
মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের ৩০টিরও
বেশী দেশ ভ্রমণ করেন। এর
মধ্যে অনেকগুলো সফরেরই উদ্দেশ্য ছিল
ভারতবর্ষের বাইরে এবং অবাঙালি পাঠক
এবং শ্রোতাদেরকে তার সাহিত্যকর্মের
সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়া এবং তার
রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করা। যেমন ১৯১২
সালে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় তিনি তার এক
তাক বইয় নিয়ে যান এবং এই
বইগুলো বিভিন্ন মিশনারি ব্যক্তিত্ব,
গ্রান্ধী প্রতিজি চার্লস এফ অ্যান্ড্রুজ,
অ্যাংলো-আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার
ইয়েট্স, এজরা পাউন্ড রবার্ট ব্রিজেস,
আর্নস্ট রাইস প্রমুথ অনেককেই মুগ্ধ
করেছিল। এমনকি ইয়েট্স গীতাঞ্জলির
ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা লিখেছিলেন
এবং অ্যান্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে এসে তার
সাথে যোগ দেন। ১৯১২ সালের ১০ নভেম্বর
ঠাকুর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ভ্রমণে যান।
যুক্তরাজ্যে তিনি অ্যান্ড্রুজের
চাকুরিজীবী বন্ধুদের সাথে বাটারটন
এবং স্ট্যাফোর্ডশায়ারে অবস্থান করেছিলেন।
১৯১৬ সালের মে ৩ থেকে ১৯১৭ সালের এপ্রিল
মাস পর্যন্ত তিনি জাপান
এবং যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা করেন। এইসব
বক্তৃতায় তিনি জাতীয়তাবাদ- বিশেষত
জাপানী এবং মার্কিন জাতীয়তাবাদের
নিন্দা করেন। তিনি “ভারতে জাতীয়তাবাদ”
নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যাতে ভারতীয়
জাতীয়তাবাদের প্রতি বিদ্রুপ এবং এর
প্রশংসা উভয়টিই ছিল। বিশ্বজনীন
শান্তিবাদে বিশ্বাসীরা অবশ্য এর প্রশংসাই
করে থাকেন যেমন করেছেন রোমাঁ রোঁলা।
সেখান থেকে ভারতে ফিরে আসার পরপরই ৬৩
বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ পেরুভিয়ান সরকারের
আমন্ত্রণে সেদেশে যান এবং একই
সাথে মেক্সিকো যাওয়ার সুযোগটিও গ্রহণ
করেন। তার সফরের সম্মানে উভয় দেশের
সরকারই
শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী শিক্ষাঙ্গণের
জন্য ১০০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দেয়।
১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর তিনি আর্জেন্টিনার
রাজধানী বুয়েনস আয়র্স-এ যান। কিন্তু
সেখানে যাবার এক সপ্তাহের মাথায় অসুস্থ
হয়ে পড়ায় তাকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-
তে অবস্থিত Villa Miralrío-
তে নিয়ে যাওয়া হয়। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬
সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একই বছরের ৩০
মে তিনি ইতালির নেপ্লসে পৌঁছেন
এবং পরদিন ইতালির ফ্যাসিবাদী একনায়ক
বেনিতো মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ করেন।
উভয়ের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছিল।
কিন্তু ১৯২৬ সালের ২০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ
প্রথম মুসোলিনির বিরুদ্ধে কথা বলেন
এবং এর ফলে তাদের মধ্যকার সে সম্পর্ক নষ্ট
হয়ে যায়।
১৯২৭ সালের ১৪ জুলাই ঠাকুর অন্য দুইজন
সঙ্গী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার
কয়েকটি স্থানে চার মাসের সফরে যান। এই
স্থানগুলোর মধ্যে ছিল বালি, জাভা দ্বীপ,
কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম
এবং সিঙ্গাপুর। তার সে সময়কার
ভ্রমণকাহিনী যাত্রী নামক রচনায় স্থান
পেয়েছে। ১৯৩০ সালের
প্রথমদিকে তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকায়
বছরব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ
করেন। সফর শেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার
পর লন্ডন এবং প্যারিসে তার চিত্রকর্মের
প্রদর্শনী হয়। এসময়
তিনি বার্মিংহামে ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের
আশ্রয়ে অবস্থান করছিলেন।
এখানে বসে তিনি অক্সফোর্ড
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তার বিখ্যাত হিবার্ট
ভাষণ প্রস্তুত করেন। তার এই ভাষণের বিষয়
ছিল আমাদের ঈশ্বরের মানবতাবোধ
এবং মানুষ ও পরমাত্মার স্বর্গীয় রূপ।
তিনি লন্ডনের বার্ষিক কোয়েকার সম্মেলনেও
বক্তৃতা করেছিলেন। সেখানে তার বক্তৃতার
বিষয় ছিল ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের সম্পর্ক
যে বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি পরবর্তী দুই
বছর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন।
একইসাথে তিনি “dark chasm of
aloofness” নিয়েও কথা বলেছিলেন। তার
পরবর্তী সফর ছিল ডার্টিংটন হলে অবস্থিত
আগা খান ৩-এ। ডার্টিংটন হলেই
তিনি অবস্থান করেছিলেন। এরপর ভ্রমণ
করেন ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড
এবং জার্মানি। ১৯৩০ সালের জুন
থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়টা এভাবেই
কেটে যায়। এরপর যান সোভিয়েত ইউনিয়নে।
সর্বশেষে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে ইরানের
শাহ রেজা শাহ
পাহলভি তাকে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ
জানান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও
ইরানী কবি হাফিজের অতিন্দ্রীয়
ফরাসি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।
শাহের আমন্ত্রণে তিনি ইরানে যান। এই
ভ্রমণগুলোর মাধ্যমে ঠাকুর তৎকালীন সময়ের
আলোচিত এবং বিখ্যাত অনেকের
সাথে পরিচিত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হলেন হেনরি বার্গসন, আলবার্ট আইনস্টাইন,
রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ,
এইচ জি ওয়েলস এবং রোঁমা রোঁলা।
বিদেশে তার একেবারে শেষ সফরগুলোর
মধ্যে ছিল ১৯৩২ সালে ইরান, ইরাক সফর;
১৯৩৩ সালে সেইলন ভ্রমণ। তার সকল ভ্রমণ
সামগ্রিকভাবে তাকে মানুষে মানুষে বিভাজন
এবং জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অনুধাবন
করতে সক্ষম করে তুলেছিল।
সাহিত্যকর্ম
রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্য
হচ্ছে তার কবিতা এবং গান। অবশ্য উপন্যাস,
প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী এবং নাটক
রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতা ও
গান বাদ দিলে তার
সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা হচ্ছে ছোটগল্প।
তাকে বাংলা ভাষায় ছোটগল্প রচনাধারার
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার
সাহিত্যকর্মের ছান্দসিক,
আশাবাদী এবং গীতিধর্মী রূপ সহজেই
সকলকে আকৃষ্ট করে। সাধারণ বাঙালিদের
জীবনই ছিল তার প্রধান উপজীব্য।
উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ
আটটি উপন্যাস ও
চারটি উপন্যাসিকা লিখেছেন যার মধ্যে রয়েছ
চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় ও
নৌকাডুবি।
সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্প
(রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন উচুদরের
সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকর। তাঁর
লেখা ২,২৩০টি গাণ এখন বাংলা সংস্কৃতির
এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের গান
রবীন্দ্র সংগীত হিসাবে পরিচিত।
রবীন্দ্রনাথের গানকে আসলে তার সাহিত্য
থেক আলাদা করা মুশ্কিল। সেগুলোর
বেশিরভাগই কবিতা অথবা গল্প উপন্যাসের
অংশ, কিংবা অংম গীতি কবিতা বা নাটকের।
তারগানে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের
ঠুমরীর বিশেস প্রভাব লক্ষ করা যায়।
তবে মানব মনের প্রায় সকল অভিব্যক্তিই
তার গানে ধরা দিয়েছ বলে মনে করা হয়।
ষাট বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ রং তুলি হাতে নেন
আর সফলভাবে আয়োজন করেন তার
নানা প্রদর্শনীর। তাঁর প্রথম চিত্র
প্রদর্শনী হয় প্যারিস শহরে। দক্ষিণ
ফ্রান্সের এক শিল্পী তাকে এই প্রদর্শনীর
জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরে এই
প্রদর্শনী ইউরোপের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত
হয়।
নাটক
নাটকে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হয় ষোল
বছর বয়সে ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনুদিত মঁলিয়েরের বুর্জোয়া? (Le
Bourgeois Gentilhomme) নাটকে প্রধান
চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর প্রথম নাটক
বাল্মিকী প্রতিভা তিনি লেখেন বিশ বছর
বয়সে। এতে ডাকাত বাল্মিকী কিভাবে তাঁর
জীবনদর্শন পালটে স্বরসতীর
আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে রামায়ণ রচনা করেন
তা বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ
নানা ধরণের নাট্যশৈলী এবং ভাবের ব্যাপক
প্রকাশ ঘটান যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হচ্ছে কীর্তনের ব্যবহার এবং মাতাল
গানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ এবং আইরিশ
লোকসংগীতের সুর সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের
আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ডাকঘর,
যেখানে একটি বালক তার দৈনন্দিন আবদ্ধ
জীবন থেকে মুক্তি চায়
এবং অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে (যেটা তার দৈহিক
মৃত্যুকেই নির্দেশ করে)। সার্বজনীন
আবেদনমূলক ডাকঘরের এ
গল্পে (ইউরোপে যা প্রভূত সাড়া ফেলেছিল)
যে মৃত্যু দেখানো হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের
ভাষায়, “জাগতিক স্তুপিকৃত সম্পদ ও প্রচলিত
বিশ্বাস” থেকে “আধ্যাত্মিক মুক্তি”।
১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন রচনা করেন
যা তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক
হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। পরের
দিকে রচিত নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ রূপকের
বেশী ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে ডাকঘর
অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের
আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক চন্ডালিকা, যার
বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে একটি প্রাচীণ বৌদ্ধ
কিংবদন্তীকে ঘিরে যেখানে গৌতম বুদ্ধের
শিষ্য আনন্দ একটি আদিবাসী মেয়ের কাছ
থেকে কিভাবে পানি চাচ্ছেন তা বর্ণিত হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক
রক্তকরবী, যেখানে একজন লোভী রাজার
কথা বলা হয়েছে যিনি ধনী হওয়ার জন্য তার
প্রজাদের খনিতে কাজ করতে বাধ্য করেন।
নাটকের নায়িকা নন্দিনী সাধারণ
মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এসব অনাচারের
অবসান ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য
অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে চিত্রাংগদা,
রাজা, এবং মায়ার খেলা। রবীন্দ্রনাথের নাচ
ভিত্তিক নাটকগুলো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য
হিসেবে পরিচিত।
রাজনৈতিক মতাদর্শ
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিবিধ
দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তিনি ইউরোপীয়
ঔপনিবেশিকতার প্রতিবাদ করেন, এবং ভারতীয়
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দেন।
হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানতেন
বলে পরবর্তীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই
ষড়যন্ত্রের জন্য জাপানী সমর্থন লাভের
উদ্দেশ্যে তিনি জাপানের
প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট তেরাউচি ও প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমার সাথে আলাপ
করেন। তবে, একই
সাথে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের
বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং ১৯২৫ সালের
একটি প্রবন্ধে এই আন্দোলনকে চরকার
পাগলামী বলে আখ্যায়িত করেন।
দেশকে স্বাধীন করার জন্য অসহযোগ ও
সশস্ত্র আন্দোলনের
বদলে তিনি স্বনির্ভরতা ও জনমানুষের
আত্মিক উন্নতির উপরে যোগ দেন। তাঁর
মতে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অশুভ নয়,
বরং সামাজিক সমস্যার রাজনৈতিক রূপ।
তিনি ভারতবাসীকে এই শাসন
মেনে নিতে আহবান জানিয়ে বলেন, “there
can be no question of blind
revolution, but of steady and
purposeful education”.
প্রভাব
অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাচীন
আইরিশ এবং স্কটিশ সুর ও ছন্দের ব্যাপক
প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ,
“পুরোনো সেই দিনের কথা” গানটির মূল সুর
নেয়া হয়েছে স্কটিশ লোকগীতি “অল্ড
ল্যাং সাইন” হতে। এছাড়া তার অনেক গানেই
স্থানীয় বাউল গান, দক্ষিণ ভারতের
কর্ণাটকের উচ্চাঙ সঙ্গীতের প্রভাব
পরিলক্ষিত হয়েছে।
by
sm.salauddin -

সমতার পৃথিবী- করোনাভাইরাসের সাথে কথোপকথন
“আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমাদের নিজস্ব জীবন ছিল না, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু এখন থেকে চারশো কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে আমরা ছিলাম। তখনো এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়নি। জীবন্ত জগতের পূর্বশর্ত যে কোষ তাও আত্মপ্রকাশ করেনি। আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছি জীবন্ত কোষ সৃষ্টিতে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের চেয়ে কত উন্নত, শক্তিশালী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন্ত প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে এই ধরিত্রীতে। এসেছে আমাদের চেয়ে বহু উন্নত এক কোষী ব্যাকটেরিয়া। তারা সালোক সংশ্লেষণের কাজটি শুরু করে প্রায় তিনশো কোটি বছর আগে। সম্ভব করে অক্সিজেনময় পৃথিবী। তারই হাত ধরে পঁচাত্তর কোটি বছর আগে সবুজ শৈবাল আর পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর আগে বহুকোষী সবুজ পত্রাবলির উদ্ভিদরাজি ফুলে-ফলে পৃথিবীকে অপূর্ব সুন্দর ও বর্ণাঢ্য করে তোলে। পোকা-মাকড়, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখী, বানরকুল হয়ে সোজা হয়ে হাঁটা প্রবুদ্ধ মানুষের(হোমো সেপিয়ান্স) আগমন ঘটে গত চল্লিশ কোটি থেকে আড়াই লক্ষ বছরের মধ্যে। এই দীর্ঘ সময়ে আমরাও ছিলাম সবার মধ্যে। অনেকটা অপাঙ্ক্তেয় হয়ে। কারণ আগেই বলেছি আমরা কোন জীবন্ত সত্তা নই। অন্য জীবকোষের আনুকূল্যে তাদের ভেতরেই কেবল আমরা বেঁচে থাকতে পারি, বংশ বিস্তার করতে পারি। চারশ কোটি বছরতো কম নয়! কিন্তু তোমাদের প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ যেমনটা লিখেছেন, ‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি যে, মনে হয় যেন সেই দিন।’ আমরা সব দেখেছি। সকল প্রজাতি মিলে মিশে কিভাবে প্রাণময় এই সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুললো। আবার কীভাবে ‘সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব’ মানুষের হাতে তার ধ্বংস চলতেই থাকলো।”
“আমরা আবার এসেছি। কিছু কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিতে।”
“তোমাদের সভ্যতার ইতিহাসে বড় বড় রূপান্তরে তোমরা মানুষেরা নিজে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছো। বিনিময়ে কোটি কোটি ভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস করেছো। যেমন, তোমরা যখন গুহাবাসি, তখন পশু-পাখি-মাছ শিকার এবং বন্য শস্য-ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতে। তোমরা ছিলে প্রকৃতির অংশ। সেই তোমরা প্রায় ১২ হাজার বছর আগে পরিকল্পিত চাষাবাদ শুরু করে তোমাদের সভ্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করলে, বিনিময়ে বিলিন হয়ে গেল কোটি কোটি প্রজাতি। তারপর থেকে বর্তমান এই সময়ে পৃথিবীতে সাড়ে সাতশ কোটি মানুষ, যারা গোটা প্রজাতির মাত্র ০.১ ভাগ তারাই ধ্বংসের কারণ হয়েছো পৃথিবীর ৮৩ ভাগ বন্য প্রাণী ও ৫০ ভাগ উদ্ভিদের। একই সময়ে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মানব প্রজাতির ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা। তোমাদের বিজ্ঞানীরাই বলছেন- আধুনিক কৃষি এবং তোমাদের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক বন উজাড় ও বন্য আবাসের ধ্বংস এবং পানি, বায়ু ও পরিবেশ বিষাক্ত করার ফলে পৃথিবী তার চারশো বছরের ইতিহাসে জীবন্ত প্রজাতির ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির পর্যায় পার করছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রাণী গত পঞ্চাশ বছরে হারিয়ে গেছে বলে মনে করছেন তোমাদের বিজ্ঞানিরা।”
কথাগুলো বলছিল ‘কোভিড-১৯’ নামে পরিচিত করোনাভাইরাস। এমন নয় যে এই সত্যগুলো আমার অজানা ছিল, বা আগে অন্য কোথাও পড়িনি। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল আমার উদ্দেশ্যে কোভিড ১৯ এর কথা হয়তো শেষ হয়েছে, তখনই সে আরো মনে করিয়ে দিল জাতিসংঘের অধীন জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষার আন্ত-সরকার বিজ্ঞান নীতির প্লাটফর্মের আশংকা যে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে দশ লাখের মত প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে জীববৈচিত্র্যের এই ধ্বংস পৃথিবী নামের গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখ্য কারণ হিসেবে আধুনিক কৃষিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরো নাকি বলা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সাথে রোগ সংক্রমণের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, দ্রুত সংক্রমণ ঘটায় এমনসব রোগ-বীজাণু জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সাথে পাল্লা দিয়ে বংশ বিস্তার করে।
করোনাভাইরাসকে কী জবাব দেব? মনে পড়লো, ইতিমধ্যে সে প্রায় দেড় লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আমার পরিবার পরিজন আছে। এখনো সুন্দর এই পৃথিবীতে আরো কিছুকাল তাদের নিয়ে বাঁচতে চাই। ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই। তবে আপাতদৃষ্টিতে করোনাভাইরাসকে শত্রু মনে হলেও, কেন জানি মনে হচ্ছিল বাস্তবে এটি আমাদের শত্রু নয়। এমন একটি ধারণা নিয়েই তার সাথে চলে আমার কথোপকথন।
“আমরা মানুষেরা তোমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। তোমরাই বলেছো পুরো জীবন্ত নও তোমরা। কারণ শুধু অন্য কোন জীবন্ত কোষের ভেতরেই কেবল তোমরা বেঁচে থাকতে পার, বংশ বিস্তার করতে পার। তোমরা একটি আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক এসিড) ভাইরাস। আরএনএ’র কথা বলতে গিয়ে ডিএনএ (ডিওক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) এবং প্রোটিনের কথাও বলতে হবে। জীবকোষের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি বৃহৎ অণু। একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো প্রোটিন হচ্ছে জীবন্ত প্রজাতির সকল রহস্যের মূলে। গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আমাদের বিজ্ঞানিরা প্রমাণ করলেন প্রোটিন নয়, জীবনের মৌল রহস্য নিহিত আছে জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে ডিএনএ অণুর মধ্যে। এই অণুর উপাদানে এসিড যৌগ আছে। আর নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে বলে ডিএনএকে একটি নিউক্লিক এসিড বলা হয়। ডিএনএই হচ্ছে বংশগতির বাহক; ডিএনএই নির্দিষ্ট করে দেয় ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবতত্ত্বিক বিশিষ্টতা, তার আপন বৈশিষ্ট্য। ডিএনএ’র গঠন কাঠামো দেখতে পুরনো দালানের প্যাঁচানো সিঁড়ির মত। নিচ থেকে উপরে উঠে যাওয়া সিঁড়ির ধাপে ধাপে সঞ্চিত থাকে জীবনের সকল সংকেত। এসব সংকেত প্রথমে আরএনএ নামের আরেকটি অণু হয়ে প্রোটিন নামের অণুতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রজাতির সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হতে থাকে। জীবন্ত প্রজাতির সকল বৈশিষ্ট্য বা তথ্য বহন করে বলে ডিএনএকে তথ্যের প্রাণঅণুও (Information bimolecule) বলা হয়।
একটি প্রজাতির কোষে ডিএনএ’র গোটা পরিমাণকে জেনোম হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রজাতির পরিচয় তার জেনোম দিয়ে। এই জেনোমে সকল জেনেটিক তথ্য সাজানো থাকে। তোমাদের ভাইরাসের জেনোম খুবই ছোট। অন্যদিকে বহুকোষী উচ্চতর প্রজাতি যেমন, মানুষের জেনোম অনেক বড়। বিজ্ঞানিরা ‘হিউম্যান জেনোম প্রোজেক্ট’ নামের এক বিশাল গবেষণা, যা ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০০৩ সালে শেষ হয়, তার মাধ্যমে গোটা জেনোমে সঞ্চিত সকল তথ্যাদির ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ করেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত মানুষ তার জীবনের সকল রহস্য উন্মোচনের জন্য জেনোমের একটি ম্যাপ তৈরিতে সক্ষম হয়। হাতে একটি ম্যাপ থাকলে যেমন অজানা ঠিকানা বা অনাবিষ্কৃত পৃথিবীকে জানা সহজ হয়, তেমনি মানব জেনোমের ম্যাপ থাকার কারণে মানুষের জীবনের সকল রহস্য সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিপুল গতিতে মানুষ জানতে পারছে অজানাকে। এভাবে ডিএনএ সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানিরা দেখলেন ডিএনএ গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু আরএনএও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।”
কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। বোঝা গেলনা করোনাভাইরাস ডিএনএ-এর কাহিনী আদৌ আগের থেকে জানতো কিনা। তবে আমার কথাগুলো শুনে করোনাভাইরাস খুব একটা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হলো না।
“তোমরা যেহেতু আরএনএ ভাইরাস, তাই এবারে আরএনএ সম্পর্কেও কিছু বলবো। ডিএনএ’র মত আরএনএও একটি নিউক্লিক এসিড। উপাদান ও গঠনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে ভালই মিল থাকলেও এর গঠন কাঠামো অনেক সরল। আরএনএ এক ফিতা বিশিষ্ট। এই ফিতার মধ্যেই জমা আছে তোমাদের জেনেটিক তথ্য। শুরুতে বলেছি, ডিএনএতে সঞ্চিত সকল তথ্য প্রথমে আরএনএতে বাহিত হয়। তারপর আরএনএ থেকে সে তথ্য অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয়। তোমরা যেহেতু নিজেরা আরএনএ ভাইরাস তাই সরাসরি তোমাদের থেকে প্রোটিন তৈরি হতে পারে। সে যাই হোক জেনেটিক তথ্যের সুনিয়ন্ত্রিত প্রবহমানতার উপর নির্ভর করে দেহের সুস্থতা।”
“আরএনএ ও ডিএনএ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিন সম্পর্কেও বলতে হবে। জিন হচ্ছে জেনোমে ডিএনএ’র একটি টুকরো, যা ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ায় আরএনএতে রূপান্তরিত হয়। কয়েক ধরণের আরএনএ রয়েছে। যেমন, রাইবোসমাল আরএনএ (rRNA), ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) ও মেসেঞ্জার আরএনএ (mRNA)। ওইসব জিন, যাদের মধ্যে প্রোটিন তৈরির সংকেত রয়েছে, তাদের থেকে তৈরি হয় মেসেঞ্জার আরএনএ। শুধু মেসেঞ্জার আরএনএ’র তথ্য অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয়। বাকি রাইবোসমাল আরএনএ ও ট্রান্সফার আরএনএ প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে। প্রোটিন তৈরির জিনকে কোডিং জিন বলা হয়। এমন জিনের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মানুষের জন্য তার সংখ্যা বাইশ হাজারের মত। তোমাদের জন্য এই সংখ্যা মাত্র ১৫। মানুষের গোটা জেনোমের মাত্র দেড় ভাগ তথ্য কোডিং জিনের মাধ্যমে সকল প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তা হলে বাকি জেনোমের কাজ কী? সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে জেনোমের প্রায় ৮০ ভাগ নন-কোডিং জিন হিসেবে কাজ করে। এরা রাইবোসমাল আরএনএ (rRNA) ও ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) ছাড়াও আরো নানা ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরএনএ তৈরি করে। এসব আরএনএ প্রোটিন তৈরি করেনা বটে, কিন্তু জিনের নিয়ন্ত্রনে, তাদের আত্মপ্রকাশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”
আমার কথাগুলো শুনে করোনাভাইরাস হাসলো। তবে সে আমায় বাঁধা দিল না। বললো, “বলে যাও, শুনছি তোমার কথা।”
“পঞ্চাশের দশকে যখন ডিএনএ’র গঠন কাঠামো আবিষ্কৃত হল এবং প্রাণের উদ্ভব, তার স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব রক্ষায় মূল অণু হিসেবে ডিএনএ’র ভূমিকা জানা গেল, তখন বলা হয়েছিল, রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে ডিএনএ, ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে আরএনএ, এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। জেনেটিক কোডের এই গতি প্রবাহকে নাম দেয়া হয় ‘সেন্ট্রাল ডগমা’। ফ্রান্সিস ক্রিক যিনি জেমস ওয়াটসনের সাথে ডিএনএ’র গঠন কাঠামো আবিস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তিনি ‘সেন্ট্রাল ডগমা’-এর তত্ত্বটি হাজির করেন এবং বলেন সকল জীবন্ত প্রজাতিতে তা ক্রিয়াশীল শুধু নয়, এমন ‘সেন্ট্রাল ডগমা’ একমুখী। অর্থাৎ ডিএনএ থেকে তথ্য যাবে আরএনএতে এবং আরএনএ থেকে পাওয়া তথ্য অনুয়ায়ী প্রোটিন তৈরি হবে – এর অন্যথা হবে না। আরো পরিষ্কারভাবে বললে, প্রোটিন থেকে আরএনএ অথবা আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হবে না। পরে দেখা গেল ‘সেন্ট্রাল ডগমা’ মূলত অভ্রান্ত হলেও প্রকৃতি জগতে তার ব্যতিক্রমও আছে। আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরির নজির পাওয়া গেল তোমাদের মত ভাইরাস নামের জীবন্ত ও অজীবন্তের মাঝামাঝি এক সত্ত্বার মধ্যে। ট্রান্সক্রিপশনের উল্টো রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপশনের জন্য ক্রিয়াশীল ‘রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপটেইস’ এনজাইমের উপস্থিতি পাওয়া গেল তোমাদের মত ভাইরাসে। পরে দেখা গেল শুধু আরএনএতে সঞ্চিত তথ্য নিয়েই ভাইরাস থাকতে পারে। অর্থাৎ ডিএনএ ভাইরাস ছাড়াও আরএনএ ভাইরাস রয়েছে। শুধু তাই না, ডিএনএ ভাইরাস থেকে আরএনএ ভাইরাসের সংখ্যা অনেক বেশি। তোমরা করোনা তেমন একটি আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ নিয়ে এত কথা বললাম আসলে তোমাদের এ কথা জানাতে যে প্রকৃতি জগতে তোমাদের মত আরএনএ ভাইরাসের গুরুত্বের কথা আমরা মানুষেরা জেনেছি।”
“সকল ভাইরাসের মত তোমরা করোনা ভাইরাসেরও রয়েছে একটি বহিরাবরণ। প্রোটিন ও স্নেহ (লিপিড) দিয়ে তৈরি এই বহিরাবরণের আকৃতি হয় নানা ধরনের। দেখতেও ভারি সুন্দর। তোমরা দেখতে আমাদের দেশের কদম ফুলের মত। ভিরিয়ন নামের বহিরাবরণে রয়েছে দ্বিস্তর বিশিষ্ট লিপিড যার মধ্যে গেঁথে আছে পর্দা বা মেমব্রেন প্রোটিন, মোড়ক বা এনভেলাপ প্রোটিন ও স্পাইক প্রোটিন। ভিরিয়নের ভেতরে থাকে জেনেটিক উপাদান। তোমাদের করোনার জন্য তা আরএনএ। ভিরিয়নের বাইরে পেরেকের আকৃতি বিশিষ্ট প্রোটিন রয়েছে। তোমাদের যে ছবিটির সাথে সবাই পরিচিত, সেখানে এমন আকৃতির প্রোটিনের উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। এদের স্পাইক প্রোটিন বলা হয়, যার বাইরের দিকের ফোলানো অংশ বা মুকুটটির জন্য তোমাদের আমরা নাম দিয়েছি করোনা ভাইরাস। তুমি জানবে হয়তো, ল্যাতিন ভাষায় মুকুটকে বলা হয় করোনা। আশা করি এই সুন্দর নামটি তোমাদের পছন্দ হয়েছে। আগে বলেছি, তোমরা শুধুমাত্র অন্য একটি জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরে বেঁচে থাকো ও বংশ বৃদ্ধি কর। কিভাবে তোমরা অন্য কোষে প্রবেশ করো, তা আমরা জেনেছি। যখন কোন জীবকোষের উপর তোমরা বসো, তখন তোমাদের স্পাইক প্রোটিনের সাথে ওই জীবকোষের angiotensine-converting enzyme2 (ACE2) নামের বহিরাবরণ প্রোটিনের সংযোগ ঘটে। এই সংযোগ যথাযথ হলে ওই কোষের একটি প্রোটিএস এনজাইম সংযোগকৃত স্পাইক প্রোটিনকে কেটে ফেলে ও সক্রিয় করে। এর ফলে তোমরা এন্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবকোষে সহজেই প্রবেশ করতে পার। তা হলে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কোষে তোমাদের প্রবেশে আমরা সাহায্য করি।”
“যতদূর আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা ছিলে চীনের উহানে। গত ৩০ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ‘The Lancet’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উহানে একটি সিফুড মার্কেট, যেখানে বাদুড়, পেঙ্গোলিন (বনরুই্), সিভেট (গন্ধগোকুল) ও অন্যান্য বন্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়, সেখান থেকে ভাইরাস-জনিত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ৯ জন চীনা নাগরিকের থেকে নেয়া নমুনায় তোমাদের দেখা মেলে। আমরা নাম দিয়েছি কোভিড-১৯। এই ভাইরাসের জেনোমের সাথে বাদুড়ের দেহের ভাইরাস যা ২০০৩ সালে সার্স ভাইরাস হিসেবে মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটিয়েছিল তার জেনোমের মিল পাওয়া যায়। বাদুড় বা অন্য কোন প্রাণী থেকে মানব দেহে সংক্রমনের পর এই ভাইরাস অতি দ্রুত মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গবেষণা পত্রে জানা যায় কিভাবে কোষের ACE2 surface protein-এর সাথে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের সংযোগের মাধ্যমে আমাদের কাছে নতুন তোমরা এই করোনা ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পার।”
“পৃথিবীতে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রজাতির বাদুড় আছে। পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে। বাদুড় ও অন্যান্য প্রাণীদেহে প্রায় ছয় লাখের ওপর তোমাদের সমগোত্রীয় অজানা ভাইরাস বসবাস করে। যে তোমরা ছিলে বাদুড়ের দেহে, মিলে মিশে; একে অন্যের ক্ষতি করোনি কয়েক কোটি বছর ধরে, সেই তোমরা কেন বাদুড়ের দেহ ছেড়ে মানুষ বা মানুষের গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগি, মাছের দেহে প্রবেশ করলে? শুধু তোমরা কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস নও, মানুষের দেহের দুই তৃতীয়াংশ সংক্রামক ব্যাধি যাদের মধ্যে তোমরা ছাড়াও রয়েছে সার্স, মার্স, ইবোলা, এইডস, জিকা, এইচ১এন১, রেবিস ইত্যাদি রোগের কারণ যে বিভিন্ন ভাইরাস তারা এসেছে বন্য প্রাণী থেকে অথবা তাদের মাধ্যমে আক্রান্ত অন্য প্রাণী থেকে।”
“এবারে এমন একজন বিজ্ঞানীর কথা বলবো, যিনি বহু বছর ধরে তোমাদের নিয়ে কাজ করছেন। মধ্য চীনের উহানে কর্মরত এই ভাইরাস বিশেষজ্ঞ শি জেং লি। চীনের বনাঞ্চলের পাহাড়ে-পর্বতে প্রাচীন বা পরিত্যক্ত গুহায় তিনি সন্ধান করেন বাদুড়ের। যোগসূত্র বের করতে চান বাদুড়ের দেহে বসবাস করে যে ভাইরাস তার সাথে মানুষের দেহ সংক্রমণকারী ভাইরাসের কোন মিল আছে কিনা। সম্প্রতি ‘ব্যাট ওমেন’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠা এই নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী বাদুড়ের গুহায় কয়েক ডজন সার্সের মত ভাইরাসের সন্ধান পান। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে আরো অনেক ভাইরাস সেখানে আছে। তার কথা সত্য হয়েছিল।”
“৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, সকাল ৭টা। উহান ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিতে রহস্যময় রোগীর স্যাম্পল এসেছে। মুহূর্তেই ফোনে ডাক পড়লো শি জেং লি-র। ইন্সটিটিউটের পরিচালক বললেন, উহানের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রে নিউমোনিয়ার লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হওয়া দুজন রোগীর দেহে নতুন করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী শি’র গবেষণাগারে তা প্রমাণিত হলে, তা হবে মহা বিপদবার্তা। কারণ ২০০২-২০০৩ সালে এই ধরণের সার্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮০০ রোগী মৃত্যুবরণ করেছিল। ভাবনায় পড়লেন শি ও তার গবেষণা দল। যে সব বাদুড়ের গুহায় করোনার মত ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, তাদের অবস্থান তো মধ্য চীনের উহান থেকে বহু দূরে, দক্ষিণ চীনের গুয়ান্ডং, গুয়াংশি এবং ইউনান অঞ্চলে। তা হলে কি তার গবেষণাগার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন এই করোনাভাইরাস? উৎসের সন্ধান শুরু হলো। এর মধ্যেই তোমরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে হুবেই প্রদেশে, উহান যার রাজধানী। অল্প কয়েক দিনেই শি’র গবেষণা দল নতুন করোনা ভাইরাসের সাথে মিল খুঁজে পেলেন ২০১৩ সালে ইউনান প্রদেশের শিতো গুহায় পাওয়া হর্সশু বাদুড়ের করোনাভাইরাসের সাথে। এই অঞ্চলের গন্ধগোকুল প্রাণীর দেহে পাওয়া করোনা ভাইরাসের সাথে ৯৭ ভাগ মিল খুঁজে পাওয়া গেল দুটো ভাইরাসের জেনোমের। অন্যদিকে উহানের বন্যপ্রাণীর খোলা বাজারে খাঁচায় আবদ্ধ বাদুড় এবং বনরুই-এর দেহে পাওয়া করোনাভাইরাসের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া গেল নতুন ভাইরাসের জেনোমের। ‘ব্যাট ওমেন’ আবার প্রমাণ করলেন বাদুড় কিংবা তার থেকে সংক্রামিত অন্য পশু থেকে তোমরা করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে মানব দেহে।”
“এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাবে প্রায় বার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন্স) এবং তাদের সভ্যতা। মানুষের এমন বিরুদ্ধাচরণ জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে। বিশেষ করে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রথম শিল্প বিপ্লব (১৭৬০ – ১৮৩০) শুরু হওয়ার পর থেকে। এর পর এল বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উৎপাদন বহুগুন বাড়িয়ে দেয়ার দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব (১৮৭০-১৯০০)। ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনে অটোমেশন তৃতীয় শিল্প বিপ্লব সূচনা করে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তার শেষ পর্যন্ত তা চলে। ডিজিটাল বিপ্লব নামেও পরিচিত তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে চলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে সকল প্রযুক্তির মেলবন্ধনের মাধ্যমে তাদের সীমানা মুছে ফেলা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষকে যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের বিপুল সংগ্রহশালা গড়ে তোলা ও তার অবাধ প্রাপ্তির সাথে যুক্ত হচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন। যাদের মধ্যে রয়েছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ বা যে কোন প্রজাতির জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয়া, ন্যানো প্রযুক্তি, আইওটি (IOT বা ইন্টারনেট অব থিংগস), থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কমপিউটিং ইত্যাদি। নতুন উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে অচিন্তনীয় গতিতে মানব সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে প্রকৃতি ও তার প্রাণ বৈচিত্র্য সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ধ্বংস হচ্ছে।
‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের’ প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যকর চেয়ারম্যান ক্লউস শোয়াব (তাঁকে একজন পরিবশবান্ধব ভাল মানুষ বলতে পার) ২০১৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপর ‘ফরেন অ্যাফেয়ার্স’ সাময়িকীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। ‘The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond.’ শিরোনামে এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, প্রযুক্তির একজন উৎসাহী প্রবক্তা হয়েও এই ভাবনা আমার আসে, যে আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে যেভাবে জড়িয়ে ফেলছে, তাতে মানুষ তার অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও সামর্থ্য, যেমন সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে ফেলে কিনা। স্মার্ট ফোনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, ‘এই ফোনের অবিরাম ব্যবহার আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ- বিরাম, চিন্তা ও অর্থপূর্ণ বাক্যালাপের জন্য কিছুটা সময়ও বরাদ্দ রাখবে কিনা’। তার প্রবন্ধের ইতি টেনেছেন তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, ‘শেষ বিচারে মানুষ ও তার মূল্যবোধই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সামর্থ্য আছে মানুষকে হৃদয়হীন রোবোটে পরিণত করার। কিন্তু মানুষের রয়েছে সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিপদে নেতৃত্ব দেয়ার অপার ক্ষমতা, যা ব্যবহার করে মানুষ সমষ্টিগতভাবে এক অভিন্ন লক্ষ্যে নিজেদের উন্নিত করতে পারে মানবিক ও নৈতিক সচেতনতার এক সুউচ্চ শিখড়ে’।”
“আমরা হোমো স্যাপিয়েন্স বা প্রবুদ্ধ মানুষ অভিধায় নিজেদের পরিচিত করেছি। এই আমরাই কিভাবে তোমাদের বাধ্য করেছি আমাদের কিংবা আমাদের গৃহপালিত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে আমাদের কঠিন রোগে আক্রান্ত করতে সে সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দেব। ব্রাজিলের উত্তর অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের বিশাল যে বনভূমি ছিল বাদুড় ও অন্যান্য বন্য পশুর আবাসস্থল, তা উজাড় করে গড়ে তোলা হয়েছে সাদা রঙের গরুর খামার। চারদিকে অ্যামাজনের ঘন সবুজের মাঝখানে সাদা রঙের গরুর পাল সহজেই চোখে পড়ে। যে অ্যামাজনের রেইন ফরেস্টকে বলা হত পৃথিবীর ফুসফুস, কারণ বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে বাতাসে ছেড়ে দিত অক্সিজেন এই বনের ঘন উদ্ভিদরাজি, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে সেই অ্যামাজন গড় কার্বন শোষণের বদলে কার্বন নির্গমনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। ভেবে দেখেছো প্রকৃতি ও সারা বিশ্বের জন্য তা হবে কত মারাত্মক।”
“চীনের গুয়ান্ডং প্রদেশের কিনউয়ান কাউন্টি এলাকায় বনভূমি পরিষ্কার করে বিশাল শূয়রের খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মধুপুর এবং গাজীপুরের গজারি বন উজার হয়েছে। সেখানে জায়গা নিয়েছে পোলট্রি, মাছের প্রকল্প এবং টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্প। এই অঞ্চলের বনভূমি ছিল বন্য গাছ-গাছালি, পশু প্রাণী, বাদুড়, পাখি, অণুজীব ও ভাইরাসের আবাসস্থল। এর বাতাস ছিল নির্মল, নদী-খাল-ঝরনা ও নিচু জলাভুমির পানি ছিল বিশুদ্ধ টল টলে। এই প্রকৃতির মাঝখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বোধটি ছিল যে এই বনভূমি তাদের বেঁচে থাকার জন্য বড়ই প্রয়োজন, তাই তাকে রক্ষা করতে হবে। খোঁজ নিলে জানা যাবে বন উজাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের জন্য বনভূমির মানুষজনেরা নয়, মুখ্যত দায়ী সরকারী বনবিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি- যারা রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধুপুর এবং গাজীপুরের বড় অংশ এখন আর বন্য পশু-পাখি ও অণুজীবের আবাসস্থল নয়, সেখানে বাতাসে মুরগির বিষ্ঠার গন্ধ। মাছের খামারে মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পানিতে দেয়া হয় কৃত্রিম খাবার, যাতে রয়েছে শরীরের দ্রুত বর্ধনের জন্য হরমোন, রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য নানা ওষুধ ও উচ্চ শক্তির এন্টিবায়োটিক। এই পানিও দুর্গন্ধময়। কালচারের মাছ ছাড়া এই পানিতে অন্য কোন প্রজাতি বাঁচতে পারেনা। এই অঞ্চলে নদী-খাল-জলাভূমির পানি আলকাতরার মত। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টসের বিষাক্ত কেমিক্যাল এই পানিকে অনুপযুক্ত করেছে শুধু বন্য পশু-পাখি-অণুজীবের জন্য নয়, এখানে বসবাসরত সাধারণ গরিব মানুষের জন্যও। এইসব বড় বড় স্থাপনার মালিকদের অবকাশের জন্য অবশ্য জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছে ঘন বন আচ্ছাদিত সুদৃশ্য রিট্রিট, ভূতল থেকে উত্তোলিত পরিস্কার পানি।”
“পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও আবাসস্থলের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা হোমো স্যাপিয়েন্সরা ধ্বংস করেছি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমি- তার প্রতিবেশ। এক সময়ে এই বনভূমিতে বিচরণ করতো বন্য মোরগ, বরাহ, গয়াল, বাদুড়। তোমরা ভাইরাস তাদের কোন ক্ষতি করেনি। যখন বন উজাড় হলো, বাস্তুচ্যুত হলো বন্য পশু-পাখি-অণুজীব, তখন বাদুড় ও অন্যান্য বন্য পশু-পাখির দেহে সহঅবস্থান করতো তোমাদের মত যে অসংখ্য ভাইরাস, তারা কিভাবে বাঁচবে, নিজেদের বংশবিস্তার করবে? লক্ষ কোটি বছর ধরে যে নিরাপদ আবাসে তারা বেঁচে ছিল, তা এখন অরক্ষিত। বাদুড়, বনরুই – এসব মানুষের খাদ্য তালিকায় এসেছে। বন থেকে ধরে এনে বাজারে ছোট খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে তাদের। মানুষের খাবারের টেবিলে চলে যাবে তারা। কী করণীয় ছিল ভাইরাসের, তোমাদের? তোমরা মানুষের দেহে আশ্রয় খুঁজেছো, সংক্রমিত করেছো খামারের শূয়োর, মুরগি ও মাছ। বন্য পশু-প্রাণীর কোষে তোমরা শুধু সহ-অবস্থান করতে, নিজেদের জীবন বাঁচাতে। আশ্রয়দাতাকে মেরে ফেলতে না। ওই সব পশু-প্রাণির রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা তা নিশ্চিত করতো। কিন্তু মানুষ বা খামারের পশু-পাখি-মাছ – এদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাতো তোমাদের মত নতুন ভাইরাসকে মোকাবেলার জন্য গড়ে ওঠেনি। তাই কিছু দিন পর পর নতুন নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ ও খামারে পালিত প্রাণী দলে দলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে নিতান্ত অসহায় ভাবে।”
“মানুষকে কী বার্তা দিচ্ছ করোনাভাইরাস? মারণ ক্ষমতার দিক থেকে তোমরা ইতঃপূর্বে আমাদের পরিচিত ইবোলা, নিপা, সার্স, মার্স ভাইরাসের চেয়ে কম কার্যকর। কিন্তু মানুষের দেহে প্রবেশের পর তোমরা অতি দ্রুত গতিতে মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়। সারা পৃথিবীর মানবকুলের মধ্যে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছো। প্রতিরোধের বা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা আমরা মানুষ এখনও গড়ে তুলতে পারিনি। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গৃহবন্দী করেছি নিজেদের। যানবাহন, উড়োজাহাজ, কল-কারখানা, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছি। যে গতিতে চলছিল চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, তা আজ বড়ই মন্থর। তবে তোমাদের একথাও জানিয়ে রাখি, ভাল মানুষও এই পৃথিবীতে আছে। প্রকৃতি তথা পৃথিবীকে বাঁচাতে চান এমন বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, নীতিপ্রণেতা, শিল্পী, সমাজসেবক রাজনীতিবিদ- এরা সবাই কতবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর গোটা সম্পদের ৮৫ ভাগ যে ১০ ভাগ মানুষের হাতে, যাদের হাতের মুঠোয় শক্তিমান পরাশক্তির সরকার – তারা তোয়াক্কা করেনি ওইসব সাবধানবাণী। এখন তোমরা এসে বাধ্য করেছে মহা শক্তিশালী আমেরিকা ও তার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, মোদীর ভারত ও কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের লকডাউন-শাটডাউনে যেতে। তথাকথিত সভ্যতার চাকাকে মন্থর করতে। পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ড্রোন, দুর্বলের উপর পরাশক্তির চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞার অস্ত্র – কিছুই বশ করতে পারেনি অতি ক্ষুদ্র করোনা ভাইরাস তোমাদের। মহা আতংকে আছে মহা শক্তিধর পরাশক্তি। যে সুবচন শোনা যায়নি এসব শক্তিধরদের মুখে এতকাল, নিতান্ত কাবু হয়ে তারা শরণাপন্ন হচ্ছে বিজ্ঞানীদের, ছুটছে টোটকার পেছনেও, দুহাত তুলে প্রার্থনা করছে যেন কোন অলৌকিক শক্তি এই যাত্রা তাদের উদ্ধার করুক। এতদিন কল্যাণ রাষ্ট্রের যে সামাজিক সুবিধাদি এরা ক্রমাগত কর্তন করেছে সমাজের ৮৫ ভাগ সম্পদ ভোগকারী ১০ ভাগ মহা বিত্তবানদের স্বার্থে, তারা আজ শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাতের কথা বলছে। কর্মহীন ব্রিটেনবাসীকে বেতনের ৮৫ ভাগ দেয়া ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে’ শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছেন করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসা প্রধান মন্ত্রী বরিস জনসন। ট্রাম্পের মুখেও অন্য সুর।”
“হাজার হাজার বছর ধরে চীনা সভ্যতায় ঐতিহ্যগত খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল বন্য প্রাণী। যে ব্যবসার কাজে যুক্ত আছে এক কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ, যে ব্যবসায় খাটে প্রায় সাড়ে ছয়শ হাজার কোটি টাকা এবং যে কারণে কখনো তা বন্ধ করা যায়নি, তোমাদের আক্রমণের ৫৫ দিনের মাথায় তা সম্পূর্ণ বন্ধের আইন জারিতে এগিয়ে এলো চীনা সরকার। ২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ তারিখ। চীনা সরকার গবেষণায় ওষুধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া বন্য প্রাণী ধরা, ভক্ষণ বা রপ্তানি করার উপর নিষেধাজ্ঞার আইন জারি করে। অবশ্য ট্র্যাম্প, যাকে নোয়াম চোমস্কি (তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতির একজন সুহৃদ) দেখেন এক সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানসিক রোগী ও ভাঁড় হিসেবে, তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং সরকারের মত এমন বলিষ্ঠভাবে প্রকৃতির পক্ষ নিতে।”
এক টানে অনেক কথা বলে ফেলেছিলাম। করোনা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, “দেখা যাচ্ছে, যে কথা মনে করিয়ে দিতে আমি ফিরে এসেছিলাম, তার অনেকটাই তুমি অনুধাবন করতে পারছো।”
“আমি নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক, নীতিপ্রণেতা, শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক, লেখকরা কি বলছেন তোমাদের সম্পর্কে? শুনে তোমরা খুশিই হবে।”
“ভারতের বরেণ্য ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায় লিখেছেন “করোনা শক্তিধরদের নত হতে বাধ্য করেছে। পৃথিবীকে সাময়িক ভাবে হলেও থামিয়ে রাখার যে কাজ অন্য কেউ কখনো পারেনি, তা সম্ভব করেছে করোনা। আমাদের মন এই ভাবনায় এখনো আচ্ছন্ন আছে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবার; যে গভীর ছেদটি ঘটে গেছে, তাকে আমলে না নিয়ে ভবিষ্যৎকে অতীতের সাথে আবার জোড়া লাগাবার। কিন্তু যে বিশাল পরিবর্তনটি ঘটে গেছে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। করোনার এই সময় আমাদের সামনে হাজির করেছে আমাদেরই সৃষ্ট মহা দানবীয় ব্যবস্থা যা পৃথিবীকে সমূহ ধ্বংসের শেষ সীমায় নিয়ে যাবে, তার সম্পর্কে খোলা চোখে নতুন করে ভাববার। নতুন পৃথিবীতে প্রবেশের যে পথটি খুলে গেছে, তা ধরে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি আমাদের কুসংস্কার, ঘৃণা, লোভ, ডেটা ব্যাংক, অকেজো চিন্তা, মৃত নদী, ধোঁয়াটে আকাশকে পেছনে ফেলে। সাথে খুব বেশি কিছু নেবার দরকার নেই। হাল্কা হয়েই আমরা পথ চলবো আরেকটি পৃথিবীর স্বপ্ন নিয়ে। তার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেব।”
মার্কিন ভাষাবিদ ও দার্শনিক নোয়াম চোমস্কির কথা তোমাকে আগে জানিয়েছি। তিনি বলেন, “করোনা ভাইরাসের ভাল দিকটি হচ্ছে মানুষ হয়তো ভাবতে শুরু করবে কেমন পৃথিবী আমাদের চাই। … করোনা-পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন আগমন ঘটতে পারে হিংস্র স্বৈর সরকারের, অন্যদিকে ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের বিপরীতে সূচীত হতে পারে সমাজের এমন মৌলিক সংস্কার, যা নিশ্চিত করবে মানুষের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবিক বিধান।”
লন্ডনের থিবা মারান্ডোকে তুমি চিনবে না। কোটি কোটি ভাল স্যাপিয়েন্সের একজন সাধারণ সদস্য। সেদিন কথা হচ্ছিলো তার সাথে। কত সহজেই না থিবা বললো, “যদি এক ভাইরাসের কারণে গোটা পৃথিবী থেমে যেতে পারে, তা হলে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজাতির বিলুপ্তি, বিষাক্ত কিটনাশক, প্লাস্টিক, বন উজাড়, সবুজ পৃথিবীকে মরুভূমি বানানো, দারিদ্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্বল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির বিনাশ ইত্যাদি ইতাদি ইত্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এত কঠিন কেন হবে?”
“আরো একটি ভাল খবর দেব তোমাদের।” এ কথাটি বলতে বলতেই খেয়াল করলাম যে করোনার মুখে হাসি। কথোপকথনের শুরুতে তার মুখের কঠিন অভিব্যক্তি আর নেই।
“রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ পায়াস ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণিত, পদার্থ বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও জ্ঞানতত্ত্ব চর্চার জন্য পন্টিফিকাল একাডেমি অব সায়েন্সেস (পিএস) ১৬০৩ সালে রোমের প্রিন্স ফ্রেডেরিকো চেসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘একাডেমি অব লিঙ্কস’ এবং তার প্রধান হিসেবে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে পিএস। অতিসম্প্রতি এই একাডেমির পক্ষ থেকে পাঠানো ৬৭ জন বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, যাদের অধিকাংশই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত, তাদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে করোনার এই সময়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার নির্ধারণে তাদের পাঁচ দফায় প্রস্তাব করেছেন, সংকট মোকাবেলায় আশু সাড়া ও কাজ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা, গরিব ও দুঃস্থদের রক্ষা করা, সকল দেশের মধ্যে বৈশ্বিক নির্ভরতা ও সাহায্য নিশ্চিত করা এবং সকলের মধ্যে সংহতি ও সহমর্মিতা শক্তিশালী করা। চার্চের পক্ষ থেকে এলেও অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে বিজ্ঞান ও মানবিকতারপ্রতি চার্চের অঙ্গীকারের স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই বিবৃতিতে।”
“করোনা, তোমরা তো ভাল করেই বুঝেছো যে বিজ্ঞান ও মানুষের সহজাত মানবিকতা তোমাদের কিংবা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়। চার্চের পাঠানো উপরের বিবৃতিকে তাই তোমরাসহ সবার জন্য ভাল খবর বলেছি। পৃথিবী ও মানুষের উপর তোমাদের একচ্ছত্র রাজত্বের এই সময় কিভাবে বদলে দিচ্ছে মানুষের হাতে আক্রান্ত পৃথিবীকে, তার জলবায়ু ও প্রতিবেশকে, তা নিচের ছবিটি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে।”
“তোমাদের আগমনের আগে পরে এক মাসের ব্যবধানে স্যাটেলাইট থেকে তোলা চীন দেশের পাশাপাশি দুটো ছবি দেখে তোমাদের ভাল লাগবে। বাম পাশের ছবিতে করোনার আগে নাইট্রোজেন ডায় অক্সাইডে চীনের দূষিত ভূমণ্ডল। এক মাসের ব্যবধানে দূষণ-মুক্ত চীনের চিত্র। প্রধান পরিবেশগত সূচকসমূহ যা গত অর্ধ শতাব্দী ধরে ক্রমাগত খারাপের দিকে গেছে, তা বর্তমান লকডাউনের এই সময়ে হয় স্থিত অবস্থা বা উন্নতি করছে। কার্বন নিঃসরণের জন্য প্রধানত দায়ী চীনে ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকে মধ্য মার্চ পর্যন্ত সময়ে তা কমে গেছে প্রায় ১৮ ভাগ। ধারণা করা হচ্ছে ইউরোপে ও আমেরিকাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ কমে যাবে। পৃথিবীতে শব্দ দূষণ কমে গেছে, বায়ু নির্মল। তাই পাখির কল-কাকলীতে চারদিক মুখরিত। ভ্রমর সুন্দর হয়ে ওঠা ফুলে গুঞ্জন করছে।”
সত্যি বলতে কি এতো কথা বলে অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। করোনাও অনেকক্ষণ ধরে চুপ। জিজ্ঞেস করলাম, “কিছুই কি আর বলার নেই তোমার?” জবাব দ্রুতই এলো।
“সারা পৃথিবীতে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছি, তোমাদের আতঙ্কিত করেছি। তোমরা নিজেদের গৃহবন্দি করেছো, লকডাউন, শাটডাউনে গেছ। কিন্তু তা কেন, কোন উদ্দেশ্যে করেছি? তোমাদের মানুষের কথাগুলো শুনে আমিতো ভালই আশা-ভরসা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, আমাদের কারণে মানুষের মৃত্যু, কষ্ট, নানাবিধ সংকট – এসবের বাইরেও আরো গভীর চিন্তা তোমাদের মাথায় ভিড় করছে। তাতো করবেই। চিন্তা করাই তো হোমো সেপিয়েন্সের কাজ। করোনার ‘দুঃসময়’ কেটে যাবার পর অতি দ্রুত তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাবান শক্তিধরেরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। মানুষ ও প্রকৃতির উপর তাদের অন্যায় শাসন আবার চাপিয়ে দেবে, এমনসব দুশ্চিন্তা তোমাদের ভাবিয়ে তুলছে। তার কারণও আছে। অতীতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বিপদ কেটে যাবার পর আবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। যা তোমাদের বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তকদের কঠিন চিন্তায় ফেলেছে, তা হলো, এবারে ভুল করলে মহা বিপদ। গোটা সেপিয়েন্সের বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা। ইতোমধ্যে ট্রাম্প ও তার ভাবশিষ্য ‘ট্রপিক্যালের ট্রাম্প’ হিসেবে পরিচিত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর বেশ কিছু উন্মাদ সিদ্ধান্ত তেমন সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলছে।”
“আমাদের আরেকটি ক্ষমতার কথা তোমরা জান। তা হলো আমরা সহজেই নিজেদের রূপ পরিবর্তন করতে পারি। প্রকৃতি আমাদের সেভাবেই সহজ করে তৈরি করেছে। আমরা আরএনএ ভাইরাস। ডিএনএ’র সাথে তুলনায় আমাদের গঠন খুবই সরল। তাই সহজেই আমাদের গঠনে মিউটেশন হতে পারে। বিরূপ পরিবেশে আমরা সহজেই মিউটেশনের মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার পথ বের করি। আমাদের এই সামর্থ্যের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম এজন্যে যে আমাদের বিরুদ্ধে নতুন ভ্যাকসিন বা আমাদের বিরুদ্ধে ওষুধ বের করেই যে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। সাময়িক কালের জন্য তোমাদের মনে হবে তোমরা জিতে গেছো। কিন্তু হে মানবকুল, এবারেও যদি তোমাদের শিক্ষা না হয়, তবে এর পরের বার আমরা আসবো আরও ভয়ংকর হয়ে। তা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত হোমো স্যাপিয়েন্সরা পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়।”
“তোমরা তো হোমো স্যাপিয়েন্স বা প্রবুদ্ধ মানুষ। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতি। সেজন্যেই পৃথিবী ও তার প্রকৃতি জগতকে তোমরা শাসন করছো। তার সমূহ সর্বনাশও করছো তোমরা। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এই পৃথিবী থেকে তোমাদের বিলুপ্তি ঘটলে প্রকৃতি জগতের কী কোন ক্ষতি হবে? না, কিছুই হবে না। বরং মানুষের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে প্রকৃতি স্বউদ্যোগে তার ক্ষতগুলো নিরাময় করে তুলবে। অন্যদিকে সালোক সংশ্লেষণে রত উদ্ভিদরাজি যদি বিলুপ্ত হয়, যদি এই কাজে নিয়োজিত এক কোষী সায়ানোব্যাকটেরিয়া বিলুপ্ত হয়, যদি উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পরাগায়নে সতত নিয়োজিত কীট-পতঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলেতো প্রাণময় পৃথিবী বিরাণভূমিতে পরিণত হবে। সেজন্যেই বলছি এবারে দানব হোমো স্যাপিয়েন্সরা যেন অতীতের মত আবারো পৃথিবী শাসনের সুযোগ না পায় সে ব্যাপারে তোমাদের অতি দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। সময় তোমাদের হাতে কম। আমরা করোনাভাইরাস, প্রকৃতি জগতের সবচেয়ে নগন্য এক সত্তা। খুব বেশি সময় ট্রাম্পের মত আগ্রাসী মানুষদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না আমরা। তোমাদের বিজ্ঞানীরা আমাদের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন তৈরির জন্য দিনরাত কাজ করছে। আমাদের দ্বারা আক্রান্তদের সারিয়ে তোলার কার্যকর ওষুধও বের হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মেধা, শ্রম ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন ও ওষুধ যখনই ট্রাম্পের মত বা কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের হাতে পড়বে, তখনই তারা প্রকৃতির বিপদ সংকেতকে আর তোয়াক্কা করবে না। আমি ভেবে দেখেছি, খুব বড় জোর ছয় মাস পরাশক্তি তোমাদের মত ভাল মানুষদের কথা শুনবে, তাকে গুরুত্ব দেবে। তাই পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। যা মেনে চললে প্রকৃতিজগত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা করোনাসহ সকল প্রজাতি মিলেমিশে গড়ে তুলবে সমতার পৃথিবী।”
গভীর মনযোগে করোনার কথাগুলো শুনছিলাম। ঠিক করলাম কথা আর বাড়াবো না। যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। তার শেষ কথা কানে ভাসছে। করোনা বললো-
“তুমি বলছিলে দার্শনিক নোয়াম চমস্কি’র কথা। মানুষ অজেয়, করোনা মহামারীতে মানুষ জয়ী হবেই এমন একটা প্রপঞ্চ প্রায় শতভাগ হোমো স্যাপিয়েন্সের আছে। চমোস্কি-র মত দার্শনিকও হয়তো এমন চিন্তার বাইরে নন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে মানুষের জয়ী হওয়া নয়, প্রকৃতির জয়ী হওয়ার ভাবদর্শনে বিশ্বাসী হয়ে যদি মানুষ লড়াইটি চালায়, তাহলেই মাত্র সমতার পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেদিন সত্যিকার অর্থেই হোমো স্যাপিয়েন্স হয়ে উঠবে মানুষ প্রজাতি।”
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন : ইউজিসি অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সুত্র : বিডিনিউজ২৪.কম -

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
সনৎকুমার সাহা
তাঁর জন্মশতবর্ষ-সূচনালগ্নে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কৃতজ্ঞ স্মরণ। তাঁর নেতৃত্বের প্রেরণাই সম্ভব করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ত্যাগের মহিমায় তা উজ্জ্বল। গণমানুষের চেতনায় তার ব্যাপ্তি এবং সর্বতোভাবে নৈর্ব্যক্তিক পরার্থকামনায় তা সংহত। তবে তাঁকেও মাড়াতে হয়েছে অভিজ্ঞতার কাঁটা-বিছানো পথ। হ্যাঁ-নার দ্বন্দ্বের পর্যায়ক্রমিক বহুমুখী বিস্তার, পরস্পরের সংস্রব ও সংঘাত – এসব এড়িয়ে নয়, বরং তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে ঠেকে শিখে বাস্তবে ভালো-মন্দের বহুমাত্রিক চেহারায় স্থান-কাল-পাত্রের স্বরূপ চিনে নিতে নিতে সমগ্রকে ধরবার ও তার কল্যাণময় রূপ খোঁজার সাহসী পদক্ষেপে তাঁর ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া। ভয় পাননি। ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’ – জীবন দিয়ে তিনি এই মূল্যমানেই আস্থা রেখে গেছেন। দাম দিতে হয়েছে চূড়ান্ত। ব্যক্তির মাপে নয়, গোটা বাঙালি বাস্তবতার মাপে। তাঁকে নিয়ে আমাদের অর্জনের গুরুত্বও বিপরীত দিক থেকে এমন দেখায়। ‘আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ’ – যদি আগামীতে এই জেগে ওঠা তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার সার্থকতা খোঁজে, তবেই তাঁকে মনে করা, মনে রাখা অর্থবহ হয়। অবশ্য খুরের ধারের মতো পথ দুর্গম। কখনো কখনো সামনে কেবল বৃহৎ অনিশ্চয়, অথবা, নিশ্চিত আত্মগ্লানির মনোহর মসৃণ সোপান। মুখোমুখি হবার দায় এখন, এবং ভবিষ্যতের সব ‘এখন’ এই বাংলার মনুষ্যপদবাচ্য প্রতিটি সচেতন-সমর্থ জনের। তিনি যে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর অকালছিন্ন জীবনসংগ্রামে, তাতে মিলতে পারে পথের সঞ্চয়। স্থান ও কাল বহুমুখী সম্ভাবনার দৃশ্য রচনা করে চলে এগোবার কথা ভাবতে পারে সংশ্লিষ্ট মানবসমুদয়। তাদের কাছে তাঁর কীর্তিকথা তাই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের আত্মস্বরূপ বোঝার জন্যেও জরুরি।
তবে কোনো মহামানব হবার বায়না তিনি মেটান না। ‘যে আছে মাটির কাছাকাছি’, এমন এক মানুষই ছিলেন তিনি। তাদের ভেতর থেকে, তাঁর মতো অসংখ্যজনের জীবনের স্পন্দনে সাড়া দিয়ে, তাদের মনে সাড়া জাগিয়ে এক অখ্যাতজনের মতো তাঁর বেড়ে ওঠা। একসময় প্রবাদপুরুষে পরিণত হওয়া। তা তাঁকে গণবিচ্ছিন্ন করেনি। বরং গণমানুষের জীবনভাবনায় একাত্ম হয়ে তাদের সঙ্গে অভিন্নতার যোগসূত্র রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা নির্বিশেষ হবার বিরল বৈশিষ্ট্য তাঁকে দিয়েছে। তাঁকে বোঝার জন্যে তাঁর কালের মাত্রাটাও আমাদের মাথায় রাখা জরুরি। এবং সবটাই নিরাসক্ত মনে। যা ঘটে, তাই বিধিলিপি, অদৃষ্টের কাছে এমন আত্মসমর্পণে কোনো গৌরব নেই, যথেষ্ট আত্মাবমাননা আছে। প্রতিটি মুহূর্ত অসংখ্য সম্ভাবনা তুলে ধরে। জনসমুদয়ের পরস্পরবিচ্ছিন্ন, সংযুক্ত, একক, বহুদলীয়, বহুমুখী উদ্যোগ ও কার্যপরম্পরা সেসবের পরিণামে বিভিন্ন জীবনপ্রবাহে গতি আনে, প্রকৃতির স্বরূপও বস্তুগ্রাহ্য আকার পায়। পেয়ে চলে অবিরাম। তারই প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যক্তিপ্রতিভা যদি অসামান্যের রাজটীকা মাথায় নিয়ে বিকশিত হয় অথবা বিধ্বস্ত হয় সমূহ বিনাশে, তবে তাকে ওই সম্ভাবনারাশির একটির ঘটনারূপ বলে মেনে নিই; যদিও পরিণামে তা থেকে আরো বহুবিচিত্র সম্ভাবনা গজাতে পারে। ব্যাপারটি দাবা খেলায় প্রতিপক্ষের সামনে পরপর দান দেবার মতো। বিপুল ব্যক্তিপ্রতিভা অবশ্য কখনো কখনো অনিশ্চয়তার যোগসাজশেই মাথা তুলে এগিয়ে এসে দেশ-কালের আপন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে নিজের অনপনেয় ছাপ রেখে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মানবসমুদয়ের ইতিহাসের গতিপথও হয়তো তাতে বদলে যায়। কিন্তু এর সবটাই বহু মানুষের সমূহ আচরণ সঙ্গে করে তাতে বাড়তি উপাদানের জোগান দিয়ে। ধ্বংস বা সৃষ্টি, অনুরাগ বা বিরাগ, উন্নয়ন বা অবনয়ন, অথবা সবগুলোর মিশ্রণ মিশে থাকে মানবযাত্রায় – এককে এবং সমষ্টিতেও। Ôwhole centuries of follies and noise and sinÕ যেমন অনিঃশেষ, তেমনি ভালোবাসা, তৃপ্তি, আনন্দও। সব মিলিয়ে অবশ্য মানুষ আপন সক্ষমতার সম্ভাবনাকে ক্রমাগত প্রসারিতই করে। যদিও সংক্রান্তি পুরুষ বা মানবীরও বস্তুসিদ্ধ আবির্ভাব ঘটে কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের বিস্ফোরণে। ইতিহাসযাত্রায় ইতিহাসস্রষ্টা মানব-মানবীদেরও আমরা পথের বাঁকে বাঁকে এইভাবে পাই। এবং সবটাই বিরতিহীন চলমানতায় দুর্জ্ঞেয় কেলাসনের পরিণাম। যদিও এও বাস্তব। এই চলমানতাকে যদি কোনো আচার-বিচারের ছকে-বাঁধা-খোপে পুরে তাতে চিরকালের ছাপ মেরে দিতে চাই, তবে তাতেই ঘটে নিশ্চয়তাবিলাসী সিদ্ধান্তবাগিশদের সর্বজ্ঞ সাজার ভ্রান্তি। তার খেসারত দিতে হতে পারে ওই খোপে আঁটা সব মানুষকেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।
এই কথাগুলো মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধুর কীর্তিকথায় আবার নজর দিই। বাঙালি, বাংলাদেশ – এই ধারণা বা প্রত্যয়গুলোও অনিবার্যত সেখানে প্রাসঙ্গিক।
দুই
তাঁর যাত্রা শুরুতেই ‘বঙ্গবন্ধু’ হয়ে নয়। এটি তাঁর অর্জন। ক্রান্তিলগ্নে এই ভূখণ্ডে জনগণের চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনায়। জীবন বাজি রেখে সব ভয় তুচ্ছ করে অসীম মনোবল নিয়ে একাগ্র সাধনায় এগিয়ে যাবার অনমনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দেশবাসীর প্রকাশ্য স্বতঃস্ফূর্ত সর্বসম্মত ঐকান্তিক ঘোষণায় তিনি পান এই পরিচয়। জন্মসূত্রে পাওয়া নামকে তা ছাপিয়ে যায়। যদিও ওই শেখ মুজিবুর রহমান তলিয়ে যায় না। নিত্যদিনের চলায় পথের বাঁকে বাঁকে নিজেকে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে আঘাত-প্রত্যাঘাতের সব চিহ্ন গায়ে নির্বিকার ফুটিয়ে তুলে তা ক্রমাগত উজ্জ্বল হয়। তিনি কিছুই গোপন করেন না। অতিমানব হন না। বরং মানুষের সীমানায় ধ্যান-ধারণার বৃত্তে থেকে, আবার বৃত্ত ভেঙে সহজ সরলতায় সাহসী পা ফেলে সামনে এগিয়ে চলেন। ‘গোপন হিংসাকপট রাত্রিচ্ছায়ে’ হানা দিয়ে এই চলার ইতি টেনেছে। তাঁর দীপ্তি কিন্তু ম্লান হয় না। যদিও সাপ-লুডো খেলার মতো পথে ওঠা-পড়ার শেষ নেই। বাস্তব ভোল পালটায়। বহুমুখী স্বার্থবাহী মতলবের শাখা-প্রশাখা নানা দিকে ছড়ায়। তারপরেও যে ধ্রুবপদ তাঁর জীবনসংগ্রামে উদ্ভাসিত হয়, জীবনের অনিবার্য দ্বান্দ্বিকতায় তা এক প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। বহু পথ ঘুরে ঘটনার দৃশ্যপট বদলে যাওয়া সত্ত্বেও। ‘বঙ্গবন্ধু’ – নামাবলি গায়ে পথ-সংকীর্তন অথবা ক্ষমতাকেন্দ্রে অসহিষ্ণু দাপট কিন্তু তাঁর মহিমা বাড়ায় না। বরং কী করে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন, এই অভিযাত্রার অনুসরণেই তাঁর অনন্য বিকাশ ধরা পড়ে। বাংলাদেশ তার যৌক্তিক ও ভাবগত সত্তার স্বরূপ খুঁজে পায়।
জন্ম তাঁর এই বাংলায় ফরিদপুরের অতিসাধারণ এক গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়।
একই রকম আর পাঁচটা গ্রামের মতো বিশেষত্বহীন। চেনা-জানা-মাখামাখি-ঝগড়াঝাঁটি সব গায়ে-গায়ে লাগা। গতানুগতিক জমিজমা-ব্যবসাপত্র নিয়ে কোনো পরিবার সম্পন্ন, কোনোটা বা পড়তি। তার ভেতরেই আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার জাল। শেখ পরিবার তুলনায় বড় – লতায়পাতায় ছড়ানো। এমনটি অবশ্য কোনো ব্যতিক্রম নয়। সব গ্রামেই এমন। সাম্প্রদায়িক দূরত্ব ছিল। অনেকটা চাক বেঁধে। তবে বাইরে মেলামেশা সাধারণত অবাধ। যদিও অন্তঃপুরে সংস্কারের গণ্ডি ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। কারো কারো মনোবেদনার সংগত কারণ। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠত সামান্যই। কারণ এমনই ছিল দেশাচার। অবশ্য বিভেদের সচেতনতা একটু একটু করে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তাঁর শৈশবেই। তা বাইরে থেকে আমদানি। নগরজীবনে স্বার্থের দ্বান্দ্বিকতা ছায়া ফেলে গ্রামে। গণমানসে তার দখল প্রসারিত। কারণ তফাৎগুলো মৌরসিপাট্টায় চলে আসে তর্কাতীত ও প্রতিকারহীন। যদিও সবটাই অমূলক।
উনিশ শতকের বাংলায় হিন্দু গৌরবের পুনর্জাগরণের অহংকার, বিশেষ করে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে বেশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনে প্রভুশক্তির তুলনায় নিজেদের ঐতিহ্য যে ফেলনা নয়, এটা জানার ও দেখাবার তাগিদটা যেন বাড়ে। য়োরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় ও রেনেসাঁসের ইতিহাস তাতে প্রেরণা জোগায়। য়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজের বিশেষ বিশেষ ঘরানায় তার অনুমোদনও জোটে। সব মিলিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবোধের একটা ভাবমূর্তি আকার পেতে শুরু করে, যদিও কেউ ভেবে দেখে না, স্ববিরোধ তার থেকে যায় গোড়াতেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন কীর্তি শ্লাঘনীয় হলেও তাকে হিন্দু, অথবা, ঘটনাপরম্পরায়, আর্য পরিচয়ে তুলে ধরা সংজ্ঞা নির্ণয়ে এক গুরুতর ভ্রান্তিকেই প্রশ্রয় দেয়। এ যেন শূন্যের ওপর প্রাসাদ নির্মাণ। অথচ, প্রাসঙ্গিক সময়ে তারই ছটায় দিগ্বিদিকে তুমুল আলোড়ন। প্রাচীন ওই কীর্তি অবশ্যই অতুলনীয়। কিন্তু তাতে হিন্দুত্বের বড়াই অমার্জনীয় অপরাধ। ওই অবদানের ঐশ্বর্যে, অথবা ওই সময়ের জীবনভাবনায় বা জীবনযাপনের নির্দেশনায় কোথাও ‘হিন্দু’ শব্দের অস্তিত্ব নেই। না আছে কোনো শাস্ত্রে, না শিল্পে বা সাহিত্যে। আসলে ওটা ধার করা শব্দ। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে আরব সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে এ-ভূখণ্ডে প্রথম তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।
‘স’-এর উচ্চারণ ওই বিদেশি ভাষায় না থাকায় তাঁরা সিন্ধু নদের এপারে সবাইকে বলেন হিন্দু। তখন থেকে এই শব্দের আত্তীকরণ। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে, ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে, আল-বেরুণী যে বিখ্যাত বই রচনা শেষ করেন (আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্র অনুবাদে নাম ভারততত্ত্ব), তাতেও হিন্দে বা হিন্দুদের আচার, বিচার, ধর্মাচরণ, দর্শন ইত্যাদি নিয়েই তাঁর কারবার। ওই সিন্ধু নদকে প্রারম্ভিক রেখা ধরে আরো আগে একই কারণে গ্রিক অভিযাত্রীরা তাকে বলে ইন্ডাস। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে উপমহাদেশের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে গ্রিক রাষ্ট্রদূত ও পরিব্রাজক মেগাস্থেনেস তাঁর অভিজ্ঞতার যে-বর্ণনা রেখে যান, তার নাম ‘ইন্ডিকা’। ‘হিন্দু’ বা ‘ইন্ডিয়া’, কোনোটিই ভেতর থেকে গজিয়ে ওঠা পরিচয় নয়। এবং দুটোই বৈচিত্র্যনির্ভর। বাইরের অভিঘাত আত্মস্থ করা তার ঐতিহাসিক নিয়তি। পরিচয় পৌরাণিকও হতে পারে। যেমন, ‘ভারত’। কিংবদন্তির দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-পুত্র ভরতের ধারাবাহিকতায় যে-মানবধারা, তাকে, এবং তার আবাসের বিস্তারকে এই নাম চেনায়। আজকের, অথবা, আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায়, বিশ শতকের ব্রিটিশ ভারতের সীমা তা ছাড়িয়ে যায়। তার রাজনৈতিক মানচিত্র, ভাঙা-গড়ার পালা কিন্তু চলে অবিরাম। তাতে মিশ্রণ অনিবার্য। ভূপ্রকৃতি, জীবনচর্চা, সংস্কৃতি, এসব নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় আকর্ষণ অবশ্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে কাজ করে চলে। কালের বৃহত্তর পরিসরে কেন্দ্রও সরে সরে যায়। ধারাবাহিকতার রেশ থেকে যায় যদিও। ছয়শো খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে যে ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ পাই, তাতে গান্ধার ও কম্বোজ ছিল হিন্দুকুশ পেরিয়ে আজকের আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়া ভূখণ্ডে। পরে শক-হুনদলের অভিযানও ওইসব অঞ্চল থেকে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে কুশান সম্রাট কনিষ্কর রাজধানী ছিল পুরুশপুর বা আজকের পেশোয়ারে। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার বর্তমান পাকিস্তানের প্রায় সবটাই গ্রাস করে রাজস্থানেও প্রসারিত হয়েছিল। গ্রিক ও পারসিক সংযোগের ধারাবাহিকতা পাই আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় থেকে। তুর্কি মোগল ও আরব সংযোগ অবাধ হয় পরে দ্বাদশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে। সেটিও যে নির্দ্বান্দ্বিক ছিল, তা নয়। পাঠান-মোগল পারস্পরিক বিদ্বেষ নির্মমতম হানাহানি ডেকে আনে বারবার। এছাড়া ১৩৯৮ সালে সমরখন্দ থেকে তৈমুর লং, ১৭৩৯-এ পারস্য থেকে নাদির শাহ ও পরপরই ১৭৪৬-১৭৬৩-র ভেতর পাঁচবার আফগান যুদ্ধবাজ আহমদ শাহ আবদালি দিল্লি দখল করে হত্যা ও লুণ্ঠন শেষে আপন আপন দেশে ফিরে যান। তুর্কো-আফগান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬-১৩১৬), অভিবাসী মোগলরা ষড়যন্ত্র করছে, এই সন্দেহবশে গণহত্যা চালিয়ে তাদের সমূলে উৎপাটিত করেন।
তবে প্রায় চার হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় জানা-অজানা বিবিধ সংযোগরেখা ধরে এই ভূখণ্ডের মানববসতি আলগা সুতোয় বাঁধা এক ধরনের পরিচিতি পেয়ে যায় – যদিও তা বহু বৈচিত্র্যে, বহু বৈপরীত্যে ভরা। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যেমন, তেমন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অতিক্রম করেও। জীবনযাপন প্রণালি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পছন্দ-অপছন্দ, নৈকট্য-দূরত্ব, এসব তার অবয়বের নানা দিক, নানা মাত্রা। অস্বীকার করা যায় না, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্ব তাকে কার্যকরভাবে চেনায়। যদিও তা কোনো প্রামাণ্য বা অনুমোদিত চিরকালীন বাস্তবতা নয়। প্রবহমান মানবসত্যই তেমনটির অন্তরায়। তাছাড়া, কী দেখতে চাই, কেমন দেখতে চাই, কে দেখে, এগুলোর ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস সাজানোয় পর্ব বিভাগ, বা ম্যাক্স মুলারের এখানে আর্য সভ্যতার উঁচুদরের বিকাশ দেখে প্রশংসায় গদগদ হওয়া, এর কোনোটিই চূড়ান্ত বিচারে যথার্থ নয়। অনেক ক্ষতির বীজও তারা কালের গর্ভে বুনে দেয়। হিন্দু ও ভারত সমার্থক হলে ওই প্রবাহের অর্থবহ বিচার হয়তো সম্ভব। তার আবেগঘন উচ্চারণ শুনি ইকবালের কণ্ঠে ‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুসিতা হামারা – ।’ কিন্তু হিন্দু ধর্ম বলে বা হিন্দু সংস্কৃতি বলে কোথাও আলাদা গরিমা আরোপ করলে তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসচর্চাও সংকীর্ণতায় ভোগে। একই রকম কেউ যদি যুদ্ধজয়ের ঐতিহ্যে বাড়তি গৌরব দাবি করে বসে। গণমানুষের ধারার আংশিক পরিচয় হয়তো তাতে মেলে।
ইতিহাসের ধারায় দূরতর অতীতে উপমহাদেশের প্রায় সমস্তটায় সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখি সম্রাট অশোক, আলাউদ্দিন খিলজি ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময়। কলিঙ্গ ছাড়া আর কোথাও অশোক যুদ্ধাভিযান করেননি। দাক্ষিণাত্যে বা সিংহলে তিনি বুদ্ধবাণী পৌঁছে দিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেন। তারপরেও দক্ষিণে কেরালা অঞ্চল তাঁর ধর্মাভিযানের বাইরে থেকে যায়। একই রকম আলাউদ্দিন খিলজি ও আওরঙ্গজেবও দক্ষিণ ভারতের কিছু প্রান্তীয় ভূখণ্ডে পা ফেলেননি। তবে দুজনের বেলাতেই সাম্রাজ্যবিস্তার তার ধ্বংসেরও কারণ। আলাউদ্দিন খিলজি রাজ্যজয় শেষ করে দিল্লি ফিরে আসতে আসতেই দখল প্রায় সবটাই তাঁর হাতছাড়া হয়। আর আওরঙ্গজেব যুদ্ধের খরচ মেটাতে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপান। তাতে যে-বিদ্রোহ ছড়ায়, তা সামলাবার সামর্থ্য পরবর্তী মোগল সম্রাটদের ছিল না।
সব মিলিয়ে এইটুকু বোধহয় বলা যায়, পুরো ভূখণ্ড একক অধিকারে ‘ভারতবর্ষ’ নামে ব্রিটিশ শাসনের শেষ নয় দশকের আগে কোনো সময়েই ছিল না। ওই ব্রিটিশ পর্বেও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ছিল। যেমন দেশীয় বেশ কটি রাজ্যে স্বাধিকার ছিল স্থানীয় রাজা বা নবাবের; এবং পণ্ডিচেরি ও চন্দননগর, ছিটমহল দুটো ফরাসি মালিকানায়, আর, গোয়া, দমন, দিউ – এই তিনটি সমুদ্রবন্দর পর্তুগিজ অধিকারে। তারপরেও বহু ভাষা, বহু ধরন, বহু ধর্মাচরণের বিচিত্র সমন্বয়ে সভ্যতার একটা ভারসাম্য কালপ্রবাহে গড়ে উঠেছিল, যাকে একই বৃত্তের বলে চিনে নেওয়া যেত। রাষ্ট্র বা রাজ্য শাসনে বহুলতা ও বিভিন্নতা তাতে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সময়ের ধারাবাহিকতায় শতরঞ্চির নানা রং ও ছাপের মতো তারা ফুটে ওঠে। মিশে যায়। তবে একই সঙ্গে কিন্তু উপমহাদেশের বিশাল বিস্তারে বিপরীত দুই প্রান্তের জীবনভাবনা ও জীবনযাত্রার ধারায় বিচ্ছিন্নতার ও বৈসাদৃশ্যের ধরনই অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিক অভিঘাতে অমোচনীয় আকারে স্থায়ী রূপ পেয়ে যেতে পারে। আমরা জানি, এখানে উত্তর পশ্চিম খণ্ড, যা আজ পাকিস্তান, তারই প্রবেশের নানা পথ দিয়ে দূর অতীত থেকে প্রাক-ব্রিটিশ পর্ব পর্যন্ত ‘রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে’ বহুবিচিত্র স্রোতে আগ্রাসী অভিযাত্রী দল বারবার হানা দিয়ে ভেতরে ঢুকে স্থায়ী বসতি গড়েছে। মহাভারতের যুদ্ধভূমি সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। আলেকজান্ডার, কনিষ্ক, গুপ্ত-পর্বে শক, হুন যোদ্ধাবাহিনী, পরে পাঠান, মোগল, তুর্কি-পারসি বসতি ও রাজ্যস্থাপনে উচ্চাভিলাষীরা, সবাই এসেছেন এই পথে। শুরুতে যাযাবর আর্যরাও। তাই অস্ত্রের ঝনঝনানি ও জোরজবরদস্তির পাশবিক আড়ম্বর এ অঞ্চলে সভ্যতার ঐতিহ্যে মেশে। উলটোদিকে পুবের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-প্রাগজ্যোতিষপুর অঞ্চল তুলনায় শান্ত, পরস্পরসংলগ্ন ও গণমানুষের আকারে-প্রকারে সমজাতীয়। মূলত অস্ট্রোমোঙ্গলীয়। আর্য ও সেমিটিক মিশ্রণ নিতান্তই ক্ষীণ, এবং কাল বিচারে অর্বাচীন। সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ প্রাচীনতর ও মূলত কৃষিনির্ভর। জনগণের পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রবল। মেজাজে ও আচরণে সংগত কারণেই ব্রিটিশ ভারতের পূর্বপ্রান্ত ও উত্তর-পশ্চিম খন্ডের জনবসতিতে অমিলই বেশি। ধর্মবিশ্বাসে ও আচরণে মোটাদাগে কোনো ঐক্যরেখা অধিকাংশের ভেতরে টানা যেতে পারে। কিন্তু সেই রেখা উপমহাদেশ ছাড়িয়ে
পুবে-পশ্চিমে বহুদূর যায়। এবং এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে কটি দেশ নিয়ে বিশাল এলাকাজুড়ে যে জনবসতি তা ইতিহাসের ধারায় পারস্পরিক হানাহানিতে অবিরাম মত্ত। বিপুল মানব-বিপর্যয়ের শেষ নেই, সেখানে এখনো।
তবে ব্রিটিশ ভারতে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল ছিল গোটা ভূখণ্ডে একই প্রশাসনিক কাঠামোয়। উনিশ শতকের সাতের দশকেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলা রেল যোগাযোগে বাঁধা পড়ে। টেলিগ্রাফের তার আন্তর্জাতিক তথ্য সরবরাহে এই অঞ্চলগুলোকে সরাসরি কার্যকরভাবে যুক্ত করে প্রায় সমসময়ে। তাই উভয়ের ভেতর ভাবনার আদান-প্রদান, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বা বিদ্বেষ, স্বার্থের মিল-অমিল, এসব বস্তুগ্রাহ্যভাবে আগের চেয়ে বেড়ে যায় অনেকগুণ। ব্যক্তির পর্যায়ে যেমন, তেমনি সমষ্টির ভাবনাতেও। একরৈখিকভাবে নয়। বহু রেখার পারস্পরিক যোগাযোগে; কাটাকাটিতেও। এবং তা চলমান। সার্বিক বোঝাপড়াও কোনো স্থিরবিন্দুতে অবিচল থাকবে, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। মানব বাস্তবতা সব সময়েই এমন।
তবে প্রযুক্তি বিপ্লব যেমন নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে তেমনই অনিশ্চয়তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি দুই-ই বাড়ায়। এ ভূখণ্ডে শুরু তার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে। ঔপনিবেশিক স্বার্থ তাতে ইন্ধন জোগায় অবশ্যই। কিন্তু এখানে জনগণের চিন্তায় ও কাজে পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াও হয় বিপুল।
কথাগুলো মনে রাখি শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক পল্লিবালকের ক্রমাগত বেড়ে ওঠায় অর্জন ও বিসর্জনে মানুষী পূর্ণতার দিকে যে-অভিযান, তাতে বিপত্তি ও সিদ্ধি, বিনাশ ও গৌরব, – সব মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিতার সীমা ও বিস্তার যতটুকু পারি বোঝার আন্তরিক চেষ্টায়। তাঁর কাল ও পরিবেশ যেমন তাঁর আপন সত্তার ভিত্তি রচনা করে, তেমনি আপন বলিষ্ঠতায় তাদের ওপরও তিনি তাঁর গভীর ছাপ এঁকে রেখে যান। প্রবলভাবে তা প্রাসঙ্গিক থাকাতে এই দেশেরও কল্যাণ। অবশ্য বহু মানুষের দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিটি বর্তমানে তা বর্তায়। কী করি, কীভাবে করি, এসব সিদ্ধান্ত নেবার অনিবার্য চাপ মাথায় নিয়ে চলতে হয় প্রাপ্তবয়স্ক সব সক্ষম মানুষকেই। এবং তা সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রবহমান। ‘আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ’ – এই অলিখিত বাণী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। তবে জাগা-না-জাগার ওপর তাঁর কোনো হাত থাকে না। সামনের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় ব্যক্তি ও সমষ্টি কে কখন কীভাবে সাড়া দিই, এ তার ওপর নির্ভর করে। যদিও উভয়েই বহন করে জেনে-না-জেনে অতীতের চলমান ঐতিহ্য। তাতে অনাসৃষ্টির বিপন্নতাও। তাঁর মতো কাউকে আক্ষরিক অর্থে অনুকরণ করে চললেই দেশ আবশ্যিকভাবে জেগে ওঠে না। কারণ বাস্তব কখনোই এক জায়গায় থাকে না। সমূহ জীবনের পরিবর্তনশীল ছকে হাঁ-না-র সমীকরণরাশিতে সৃষ্টিশীল সমাধানের দুঃসাহসী উদ্যোগে সব বিপদ তুচ্ছ করে কোনো আড়াল না রেখে এগিয়ে যাবার প্রেরণাতেই মেলে তাঁর জীবনে জীবন লাভ করার প্রয়াস। এতে যদি তাঁর সময়ের কোনো জরুরি পদক্ষেপ পালটাতে হয়, তবুও। সৃষ্টিশীলতায় শ্রেয়োচেতনাই তাঁকে অনুসরণের মন্ত্র জোগায়। সমকালের অনিবার্য তাগিদ ওই শ্রেয়োচেতনায় ছাপ ফেলে। তাঁর বেলাতেও এমন ঘটেছে।
আগেই বলেছি তাঁর জন্ম টুঙ্গিপাড়ায়। পরিবারের নাম-ডাক সেখানে যথেষ্ট। দু-পুরুষ আগে থেকে ইংরেজি শিক্ষার চল। তাঁর এক দাদা ‘খানসাহেব’ও হয়েছিলেন। বাবা সেরেস্তাদার। সেই সুবাদে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, তখনকার এইসব ছোট শহর তাঁর কর্মস্থল। টুঙ্গিপাড়ার হালচালের বৃত্তেই। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এসব জায়গায়। তবে তা নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় হৃৎপিণ্ডে সমস্যা ধরা পড়ে। তাতে পড়াশোনায় দু-বছরের ছেদ। পরপরই চোখ আক্রান্ত হয় গ্লুকোমায়। তার জন্যেও স্কুলে পড়াশোনায় বাধা। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। পরে সেখান থেকে যথারীতি বিএ পাশ করেন। এই যে ধরাবাঁধা শিক্ষাজীবন এতে কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর মনের বিকাশ হয়ে চলেছে পরিপার্শ্বের ঘটনাস্রোতে বহু উত্তেজনার প্রভাবে। নিষ্ক্রিয়ও তিনি থাকেন না; সর্বান্তঃকরণে ওই কর্মপ্রবাহে জড়িয়ে পড়েন। নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে অকপটে তিনি জানান, ছেলেবেলায় খুব ডানপিটে ছিলেন। খেলাধুলা করা, গান গাওয়া আর খুব ভালো ব্রতচারী নাচা, এসবে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। ছেলেদের একটা দল ছিল। নেতা ছিলেন তার। হুড়-হাঙ্গামায় জড়াতেন। যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন এসবে ছেদ পড়ে। একমাত্র কাজ কেবল বিকেলে সভায় গিয়ে বক্তৃতা শোনা। স্বদেশি আন্দোলনের যুগ। তার উত্তেজনা তাঁর ভেতরেও ছড়ায়। সুভাষ বোসের কর্মকাণ্ড তাঁর কিশোরমনে দাগ কাটে। বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হতো আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ। এছাড়া মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। তিনি সবগুলোই পড়তেন। কৌতূহল মিটত। জাগতও। মনের দরজা খুলে যেত। ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী, সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। মুসলিম লীগের সভা করতে তাঁদের গোপালগঞ্জে আসা। ছোট শহরে বিপুল আলোড়ন। আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্বে শেখ মুজিব। তখনই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত।
শহীদ সাহেব কলকাতা ফিরে তাঁকে চিঠি দেন। জানান, কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনিও সাড়া দেন। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা ফলপ্রসূ সম্পর্কের শুরু এইভাবে।
১৯৩৯-এ তাঁর প্রথম কলকাতা দর্শন। তখন আবার সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সংস্পর্শে আসা। তিনি গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের সংগঠন গড়ে তোলার অনুমোদন নিয়ে ফেরেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় ও প্রত্যক্ষ সংযোগে দুটোতেই সফল হন। বিয়াল্লিশে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন, ভর্তি হন ইসলামিয়া কলেজে। আর থাকেন বেকার হোস্টেলে। অচিরেই হয়ে ওঠেন মুসলিম ছাত্রলীগের অপরিহার্য নেতৃস্থানীয় একজন। সাংগঠনিক দক্ষতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠা তাঁকে আলাদা করে চেনায়। সোহরাওয়ার্দী তাঁর আদর্শ। চিন্তায় প্রাগ্রসর। পাকিস্তান তাঁর স্বপ্ন, যেখানে তাঁর বিশ্বাস, ওই সম্ভাব্য রাষ্ট্রের নামহীন জনগণ মান্যতা পাবে।
তবে ওই কালপর্বে গোটা মানববিশ্বই খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাত আমাদেরও বিপন্নতায় হতবিহ্বল করে। পাশাপাশি গোটা উপমহাদেশজুড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ এবং তারই অনুষঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্র নির্মাণের দুর্দম উদ্যোগ। প্রতিটি কাণ্ডই ব্যক্তি ও সমষ্টির চিন্তায় ও কর্মে আলোড়ন জাগায়। তা অভূতপূর্ব। প্রাপ্তির প্রত্যাশার সঙ্গে মিশে থাকে ক্ষত ও ক্ষতির লাঞ্ছনা। শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবন আকস্মিকতার একাধিক অকল্পনীয় আঘাতে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়; যদিও তাদের সম্ভাবনারাশি লালন করেছি আমরাই। এখানে, এবং সবখানে।
মুসলিম লীগ, এবং মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন শেখ মুজিব। দেখেন পঞ্চাশের মন্বন্তর, লক্ষ লক্ষ মানব-মানবীর শহরের পথে পথে পড়ে থাকা শব – প্রতিবাদহীন, উদ্যমহীন, সান্ত্বনাহীন বোবা অভিযোগ, আরো আসে ফেউ-এর মতো কা-জ্ঞানহীন উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, – মানুষে-মানুষে একত্র বসবাসের সুদীর্ঘ অভ্যাসে পুঞ্জীভূত ঘৃণার উৎকট পাশবিক উন্মত্ততা, নিরপরাধ আকস্মিক জন্মদাগ নির্ধারণ করে কে কার বৈরী, পরিণামে সব মানুষের মনোজগতে গজিয়ে ওঠে অসংখ্য অদৃশ্য প্রতিরোধের দেওয়াল, পরস্পর নির্ভরতা হারিয়ে যায় অবিশ্বাসে।
মন্বন্তরের সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণসরবরাহমন্ত্রী। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে শেখ মুজিব পথে নেমেছেন ত্রাণ বিতরণে। নির্বিশেষ অসহায় মানব-মানবীর মৃত্যুতাড়িত মুখ তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। হয়তো তখনো স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এর প্রভাব তাঁকে পরে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার সংকল্পে প্রেরণা জুগিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর একটা পৈশাচিক বিভীষিকা। অসহায় মানুষ উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হাতে নির্বিবেক দাবার ঘুঁটি। রাজা-মন্ত্রী-পাত্র-অমাত্যদের দখল বাড়াতে ওই সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে ঘুঁটিগুলো অনায়াসে বলি দেওয়া যায়। স্বার্থের অর্থবহ জগতে তারা অবান্তর। এর আকস্মিক, হতে পারে কোথাও থেকে অদৃশ্য সুতোর টানে সুপরিকল্পিত, হামলায় জনজীবনে শান্তি ও সুস্থিতি উচ্ছন্নে যায়। শেখ মুজিব তখন দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দাঙ্গা প্রতিরোধে। কে কোন সম্প্রদায়ের, তার বাছ-বিচার করেননি। এই অকরুণ অমানবিক-কাণ্ডের অভিশাপ চেতনায় বহন করে তিনি তখন আপন হৃদয়ের ধরাবাঁধা সীমা অতিক্রমের সাহস ও শিক্ষা দুই-ই অর্জন করেন।
বাংলা মুসলিম লীগে তখন মোটাদাগে দুই ধারা : একটি প্রাচীনপন্থী সামন্ত ভূস্বামীদের ধ্যান-ধারণার অনুসরণে, অন্যটি আধুনিক শিক্ষা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে গণমুখী চেতনা বিকাশের পক্ষে। প্রথমটির নেতৃত্বে খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরউল আমীন, শাহাবুদ্দীন ও এই রকম মানসিকতা যাঁদের, তাঁরা। দ্বিতীয়টিতে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও তাঁদের প্রখর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ অনুসারীরা। তবে অধিকাংশ সুবিধাবাদী যখন যেদিকে সুযোগ, তখন সেদিকে ভিড়তেন। সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন শেখ মুজিব। অবশ্য পাকিস্তান কায়েম করার লক্ষ্যে কারো মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তারই টানে অন্যান্য দল থেকেও বিভিন্ন সময়ে অনেকে মুসলিম লীগে এসে যোগ দেন। সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তাঁর সেরা কীর্তি, ‘ঋণ সালিশি বোর্ড’ করে বাংলার কৃষকদের অনেকখানি মুক্ত করা। এজন্যেই তিনি অমর। তাঁর পরবর্তী কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্তিই বাড়ে। অনেক দুর্দিনের তাঁরা সঙ্গী।
সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের একটা বড় সীমাবদ্ধতা ছিল, তখনকার পূর্ব বাংলায় শক্ত কোনো ভিত গড়ার সুযোগ তাঁরা পাননি। আবুল হাশিমের বাড়ি বর্ধমান। তাঁর খ্যাতির উৎস সেখানেই। আধুনিক ভাবধারায় লালিত এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। তাঁর বড়ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতার হাতেগোনা সেরা চিন্তাবিদদের একজন। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমালোচক। বিষ্ণু দে, যামিনী রায়, অতুল বোস, সত্যেন বোস, সুধীন দত্ত, এঁরা ছিলেন তাঁর দৈনন্দিন আড্ডার সঙ্গী। ব্যারিস্টার হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর খ্যাতিও ছিল ভারতজোড়া। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা এখানে হটা-বাহার। খ্যাতি তাঁদের মিলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপস করেই প্রতিভা তাঁদের নির্বাপিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও ওই রাষ্ট্রের শক্তি-কাঠামোর কায়েমি স্বার্থচক্র তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য করেছে। নতুন রাষ্ট্রে তাঁরা উদ্বাস্তু। আসেন তার জন্মের পর দু-বছর পার করে। রাজনৈতিক ডামাডোলে সোহরাওয়ার্দী একবার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল পুতুলনাচের একটা পালা। যে-সুতোর টানে পুতুল নাচে, তা শক্ত হাতে ধরা থাকে পর্দার অন্তরালে। এই অন্তরালও যখন অবান্তর মনে হয়, তখন ‘বন হতে’ টিয়ে বেরোয় ‘সোনার টোপর মাথায় দিয়ে’। উনিশশো আটান্ন সালে। সেনাশাসন, স্বৈরাচার ও রাষ্ট্র মিলেমিশে একাকার। কায়েমি স্বার্থের গোপন মুখ সব প্রকাশ্যে দাঁত বের করে। পুরনো ফন্দির অভ্যস্ত ছ্যাঁচড়ামিও তার সঙ্গে জোটে। নিজ ভূমে মানুষ পরবাসী হয়ে পড়ে। লোভ ও লাভের বেসাতি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কুরে কুরে খায়।
অবশ্য সমূহ পতনের শুরু ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার লগ্নেই। অনেকের কাছে ছিল মুসলিম লীগ ও রাষ্ট্র সমার্থক। রাষ্ট্রক্ষমতার হুকুমতেই স্মরণীয় খিলাফতের প্রতিফলন। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব, কারণ যা-ই হোক, ঘটনা হিসেবে এই উপমহাদেশে অভূতপূর্ব নয়। অখণ্ড ভারতবর্ষের ধারণা, আগেই দেখেছি, একক প্রশাসনিক ক্ষেত্র হিসেবে ব্রিটিশ শাসনের আগে কখনো আকার পায়নি। তা সত্ত্বেও ভূখণ্ডটির মানববসতি সংযোগে ও মিশ্রণে খোলামেলা একটা ভাবরূপ তৈরি করতে পেরেছিল। শংকরাচার্য, মীরাবাঈ, কবির দাদু, রজ্জব, নানক, খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মহাত্মা লালন শাহ, এঁদের অবদান ও গৌতম বুদ্ধের দেশনা তাতে সমন্বয় ঘটায়। রাজ্য বা সাম্রাজ্য কখন কার দখলে, এর ছাপ তার ওপর সামান্যই পড়ে। পাকিস্তান স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারত। কিন্তু এখানে ক্ষমতার দখলদার যখন যে হয়েছেন, তখনি সে রাষ্ট্রকে তাত্ত্বিকভাবে বিশেষ এক ধর্মের অনুশাসনের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছে। এতে স্ববিরোধেরও জন্ম। পশ্চিমখ- নিশ্চিতভাবে হরপ্পা, মহেনজোদারো, কুরু-পা-ব কথা ও গান্ধার শিল্পের উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে। তা সে করেনি। অন্যদিকে, আগ্রার তাজমহল, দিল্লির লাল কেল্লা, কুতুব মিনার, দক্ষিণে সালার জং জাদুঘর, হায়দার আলী বা টিপু সুলতানের স্মৃতি, এদের কোনোটিকেই সে নিজের বলতে পারে না। ফলে যে কূপমণ্ডূকতা তাকে গ্রাস করে, তা থেকে তার রেহাই মেলে না। পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের আবেগ-ঋদ্ধ সমর্থন ছিল একশভাগ খাঁটি। কিন্তু তাতে উপমহাদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অখণ্ড উত্তরাধিকারে দ্বিধাহীন আস্থাও ছিল একই রকম প্রবল। তাঁর জীবনই যদি তাঁর বাণী হয়, তবে তাতেই ঘটে এর প্রতিফলন। এবং তা ক্রমাগত বিবর্তিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে বৃহত্তর মানবিক দায়িত্ববোধের ধারায়। কঠিন ছিল যাত্রাপথ। তিনি বিচলিত হননি। নতিস্বীকারও করেননি।
তিন
উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। সময়ের প্রেক্ষিতে ছিল তা নিতান্ত অভিনব। ব্রিটিশ ভারতের দুটো প্রান্তীয় অংশ ছেঁটে নিয়ে তাদের এক করা। মাঝখানে দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান। স্থলভাগ, এবং সবটাই ভারতে। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার ফলে এমন। গণমানুষের আদিম অনুভূতিতে এ সাড়া জাগায় যথেষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক সম্পূর্ণতা ও সামর্থ্য অর্জনে এর অবদান সামান্য। কখনো বা নেতিবাচক। বিষয়টি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর যে নজরে পড়েনি, তা নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, ‘আজ থেকে এই স্বাধীন রাষ্ট্রে কেউ মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান বা এই রকম কোনো ধর্মসূত্রে পরিচিত হবে না। আমরা সবাই পাকিস্তানি।’ কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। এমনকি একই ধর্মাবলম্বী কে সাচ্চা আর কে সাচ্চা না, এ নিয়েও সেখানে এখনো বিতর্ক প্রবল। অখণ্ড পাকিস্তান পর্বেই লাহোরে সেনাবাহিনী নামিয়ে কাদিয়ানিদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় তখন থেকে তারা অমুসলিম। শরিয়া আইন চালু হওয়ার পর অসহিষ্ণুতা আরো বাড়ে।
পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগে তরুণ কর্মী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের উৎসাহে ও কর্মকাণ্ডে কোনো ঘাটতি ছিল না। বিষয়টিকে তিনি দেখেছিলেন বাংলায় সংখ্যাগুরু মুসলমান কৃষক-শ্রমিকদের তুলনায় হীন ও অসহায় অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে। অন্যদের জাত-পাত নিয়ে বাছ-বিচারও তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, পাকিস্তান এইসব বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। মনোজগতের বদ্ধ কপাট সব খুলে দেবে। সোহরাওয়ার্দীর মেধা, ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও কর্মদক্ষতা তাঁকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁকেই তিনি তাঁর নেতা মেনেছিলেন। আশা করেছিলেন, অখণ্ড বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনে যিনি প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর ধারাবাহিকতা এই পূর্বাঞ্চলে বজায় থাকবে। কিন্তু তা হয় না। অন্তর্দলীয় চক্রান্তে কোণঠাসা হলেন সোহরাওয়ার্দী। পূর্ব বাংলার ভূমিপুত্র তিনি নন। কলকাতার অভিজাত মুসলমান পরিবারে বাংলা ভাষার চল তেমন ছিল না। তাঁর বেলাতেও এমন। নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলিতে এসব তাঁর বিরুদ্ধে যায়। তাছাড়া নগদ প্রাপ্তির আশায় অনেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকচক্রের কাছে তিনি ‘অবাঞ্ছিত’ হয়ে পড়েন। পাকাপাকি পাকিস্তানে আসেন স্বাধীনতার বছরদুই পরে। তাও এখানে নয়, করাচিতে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই শেখ মুজিব কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসেন। বিএ পাশ করেছেন ইসলামিয়া কলেজ থেকেই। ঠিক করেন, আইন পড়বেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তিও হলেন। তবে মুসলিম লীগে তাঁর সাংগঠনিক কাজ বেড়ে গেল আরো। খাজা নাজিমউদ্দীন মুখ্যমন্ত্রী। মওলানা আকরম খাঁ দলীয় সভাপতি। তাঁরাই সর্বেসর্বা। অ্যাডহক কমিটি গড়ে ছড়ি ঘোরান। তাতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ শেখ মুজিবের আপনা থেকে খারিজ হয়ে যায়। অবশ্য মুসলিম ছাত্রলীগে কর্মতৎপরতা তাঁর আগের মতোই থাকে। জনসম্পৃক্ততাও বাড়ে। অসাধারণ বক্তা বলে অচিরেই তাঁর নাম ছড়ায়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ক্ষমতালিপ্সু সাম্প্রদায়িক গণবিচ্ছিন্ন সুবিধাভোগী একটা চক্রে পরিণত হতে থাকে। শাসনক্ষমতা তাদের হাতে। অথচ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞান দুটোরই বড় অভাব। নির্ভর করতে থাকেন তাঁরা আমলাদের ওপর, বিশেষ করে যাঁরা আইসিএস। এঁরা প্রায় সবাই তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের। এর বিষময় ফল ভুগতে হয়েছে এই বাংলার মানুষকেই। বিপরীতে ওই ফল ভুগতে হয়েছে বলেই তাদের বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে বারবার। সেখানে শেখ মুজিবের প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব মহীরুহ হয়ে ক্রমশ আকাশ ছুঁয়েছে। পাকিস্তানের মোহ ভাঙতে তাঁর দেরি হয়নি। ওই রাষ্ট্রযন্ত্রও বারবার তাঁকে নির্যাতনে নির্যাতনে ধ্বংস করতে চেয়েছে। তিনি হার মানেননি।
পাকিস্তান কায়েমের পর এক বছরও পার হয়নি, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র প্রস্তুতিকরণ সভার (কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি) বৈঠক বসে তখনকার রাজধানী করাচিতে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সদস্যরাও উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানি সভ্যদের সঙ্গে সমস্বরে সহমত প্রকাশ করেন। এটাও খেয়াল করবার, কোনো কোনো নামজাদা পশ্চিম পাকিস্তানি দলীয় সদস্য তখন পূর্বাঞ্চল থেকে মনোনীত হয়েছেন, এবং এখানকার প্রতিনিধিদের কারো কারো হীনমন্যতা ছিল এতই প্রবল যে ওই বহিরাগতদের কাছে নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণে তাঁদের কথা শতগুণ বাড়িয়ে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। ওই সভায় রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটির সংশোধনী এনে তখনকার কংগ্রেস সদস্য কুমিল্লার ধীরেন দত্ত যোগ করেন, শুধু উর্দু নয়, সেই সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, বাংলাই এখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা। সেখানে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী খারিজ করে দেওয়া হয়। সেখানে প্রতাপশালী বঙ্গসন্তানরাও তাতে গলা মেলাতে কসুর করেননি। কিন্তু এই ঘটনাই সূত্রপাত করে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ-যাত্রার, এবং তাতে অগ্রণী ভূমিকা থাকে ছাত্রসমাজের। তখনো দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা দশের কোঠায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্প্রদায় ফলে গণমানসে বিশেষ গুরুত্বের। তাদের কাছে খবরটা পৌঁছুলে সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জেলা শহর-কলেজগুলোয় যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, তা অপরিণামদর্শী কর্তাব্যক্তিদের ছিল চিন্তারও বাইরে।
শেখ মুজিব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আপসহীন ছাত্রনেতা ও অসাধারণ বক্তা। শিক্ষানবিশির পর্ব কেটে গেছে পাকিস্তান আন্দোলনে কলকাতায়। তখন কিন্তু হাজতবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। শুরু হলো তা পাকিস্তানে, দেশটি সৃষ্টির ক-মাসের ভেতরেই। প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা তাঁরই মুসলিম লীগের হাতে।
নেতৃত্বে খাজা নাজিমউদ্দীন। সেই শুরু। তারপর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তাঁর মুক্তিতে পূর্ণতা পাবার আগ পর্যন্ত কারাগারেই কেটেছে তাঁর বেশিরভাগ সময়। অবশ্য পঞ্চাশের দশকে স্বল্পপরিসরে মন্ত্রীও ছিলেন। এবং জেলে, অথবা জেলের বাইরে, যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েছে। একসময় বাংলা, বাঙালি, শেখ মুজিব একবিন্দুতে সমার্থক হয়ে উঠেছে।
ছাত্র নেতৃবৃন্দ ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ঘোষণার মাধ্যমে সারাদেশে প্রতিবাদ মিছিল, পথসভা ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপনের আহ্বান জানায়। ওইদিনই পিকেটিংয়ে নেতৃত্ব দেবার সময় তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন আরো একদঙ্গল ছাত্র। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরও বাদ পড়েনি। প্রথম কারাবাসের মেয়াদ ছিল তাঁর পাঁচদিন। ১৯ মার্চ কায়েদে আজম ঢাকা এসে আবার সরকারি সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সাধারণ জনসভাতে একবার, বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে আর একবার। দুবারই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে ছাত্ররা। বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। পরে প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভায় শেখ মুজিবও গলা মেলান। ‘সংগ্রাম পরিষদের’ পালে জোর হাওয়া লাগে। তার আবেদন দেশে ‘ছড়িয়ে গেল সবখানে’।
১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পরলোকগমন করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান যেমন ছিলেন, তেমনি থাকলেন। তবে ক্ষমতার রাশ পুরোপুরি চলে গেল তাঁর হাতে। অবশ্য নাজিমউদ্দীনের ব্যক্তিত্বহীন সম্মতি ছিল সবেতেই। বাংলায় খাদ্য আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন, সব ক্ষমতার দাপটে স্তব্ধ করে দেবার প্রদর্শনী আরো জোরেশোরে চলতে থাকল। এদিকে পূর্ব বাংলায় নাজিমউদ্দীনের জায়গায় সরকারপ্রধান হয়ে বসেছেন নূরুল আমীন। আসলে তিনি আজ্ঞাবহ দাস। ব-কলমে আসল ক্ষমতা আইসিএস মুখ্য সচিব আজিজ আহমদের হাতে। জনগণের সেবা নয়, পাকিস্তানি উন্নাসিকতায় দখলদারিত্ব বজায় রাখাই তাঁর লক্ষ্য। শোনা যায়, বায়ান্নয় ভাষা-আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন নূরুল আমীনের নামে তিনিই। সরকারপ্রধানের তা মুখ ফুটে বলার সাহসটুকুও ছিল না। কারণ, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের ওপর গোপন নথি তিনি তৈরি রাখতেন। লিয়াকত আলী খানের কাছে তাঁর গুরুত্ব ছিল তুলনায় বেশি। সম্ভবত সেনাবাহিনীর দফতরেও। পরে আইয়ুব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এই রকমই ইঙ্গিত দেয়।
এদিকে শেখ মুজিবের ভাগ্যে জুটল বারবার জেলে যাওয়া ও জেলা থেকে বের হওয়া। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় তিনি টানা প্রায় তিন বছর নিরাপত্তা আইনে বন্দি। ওই অবস্থাতেই তিনি জেলখানার জানালা দিয়ে বাইরে ‘বাংলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে’র মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ২১ ফেব্রুয়ারি ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ বলে পালন করা হবে, আর, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মুক্তির জন্য তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। তিনি সরকারকে জানিয়ে দেন, তিনি লিখছেন, ÔEither I will go out of the jail or my deadbody will go out.Õ টানা বারোদিন অনশনের পর তাঁর মুক্তি জোটে।
আগেই অবশ্য বের হয়ে এসেছেন তিনি পুরনো মুসলিম লীগ থেকে। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’। সভাপতি মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিব যুগ্ম সম্পাদক। ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ নামটা অবশ্য অনন্যপূর্বা নয়। কিছু আগে পশ্চিম পাকিস্তানেই পীর মানকী শরীফ এই নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। তবে ‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগে’র আবির্ভাব একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এই নামেই এর গঠনতন্ত্রের অনুমোদন। পরে বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের অভিঘাতে যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ১৯৫৫ সালের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে এর সাম্প্রদায়িক পরিচয় মুছে দেওয়া হয়। দলের নাম তখন থেকে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’। মওলানা ভাসানী তখনো সভাপতি। তবে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৭-তে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে যান। পরে হোসেন সোহরাওয়ার্দী হন সভাপতি, শেখ মুজিব থেকে যান সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর জীবনাবসানের পর দলের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছেষট্টিতে বিখ্যাত ছয় দফা দাবি নিয়ে এই বাংলার মানুষের সামনে তিনি হাজির হন। দেশের প্রবহমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অনমনীয় দুঃসাহসী নেতৃত্ব শিখর স্পর্শ করে। আত্মসুখ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে এই বাংলার গণমানুষের কল্যাণের জন্যে হাতে কিছু না রেখে জীবন কর্মের পথে উৎসর্গ করা, এটাই তাঁকে আর সবার থেকে আলাদা করে চেনায়। তবে তাঁর দৃষ্টি পুরোটাই ছিল এই বাংলাকেন্দ্রিক। তত্ত্বের কচকচিতে তিনি মাথা ঘামাননি। ক্ষমতাকে দেখেছেন তিনি লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হিসেবে।
সে-লক্ষ্য আত্মসুখ নয়। তা ‘ওই সব ম্লান মূক মূঢ় মুখে’ ভাষা জোগানো, আশা ‘ধ্বনিয়া তোলা’র পথ দেখানো। এবং সবটাই বাস্তব জীবনচর্চায়। সেখানে নির্বিবেক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের শোষণ ছিল সবটাই প্রত্যক্ষে। তাঁর লড়াইয়ের আহ্বানে প্রধান লক্ষ্য ছিল তারাই। যতই দিন গেছে, ততই তাঁর আন্দোলন জমাট বেঁধেছে। শাসক-শোষক চক্র যতই তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়েছে, ততই সাধারণ মানুষের আস্থার আবেগ তাঁর ওপর বেড়েছে। তবে বাস্তবতার এক নির্মম কৌতুক, তাঁর রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর কাছে যতই বেদনার হোক, এর কারণেই কিন্তু আওয়ামী লীগের সর্বেসর্বা হয়ে তিনি এই বাংলার মুক্তির পথে জনসমুদয়কে পরিচালিত করার সুযোগ পান। সোহরাওয়ার্দী প্রকৃতপক্ষে বাংলার গণমানুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন না।
শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন সমাজে উঁচুতলার একজন। পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাত বলয়ে তাঁর যোগাযোগ ছিল সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। পাকিস্তানের অখ-তা তাঁর কাছে প্রাথমিক প্রত্যয়ের মতো ছিল। প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়ে তিনি সমঝোতাতেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। বাংলা থেকে সম্পদ পাচার তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।
একই সময়ে শেখ মুজিব পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রের অমানবিক নির্মমতায় ও স্বার্থান্ধ লোভের বিকট মুখব্যাদানে বীতশ্রদ্ধ হতে হতে তা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার কথা ভাবতে শুরু করেন। শুরুতেই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তাকে মাথায় নিয়ে নয়, তবে এই বাংলার মানুষের অধিকার ও কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে।
আসলে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান একটা ভারসাম্যহীন রাষ্ট্র। আধুনিক গঠনতন্ত্রের কোনো উপাদানই সেখানে তখন আকার পায়নি। তাদের বিকাশ ঘটেনি এখনো। বরং কায়েমি স্বার্থের ধারাবাহিক শক্তি সঞ্চয়ে তারা রুগ্ন ও বিশৃঙ্খলই থেকে গেছে। এক সুসংহত ও সুশৃঙ্ঘল সেনাবাহিনী ঐতিহ্য-পরম্পরায় ও উত্তরাধিকার সূত্রে তার ছিল। ব্রিটিশ ভারতের কিছু উচ্চপদস্থ আমলাও তার জুটেছিল। আর ছিল সমাজব্যবস্থায় কর্তৃত্বপরায়ণ ভূস্বামীদের অচলায়তন। পিরামিডের মাথায় এরা পরস্পর আত্মীয়তা সূত্রে বেশিরভাগ আবদ্ধ। গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সুস্থ আয়োজনের এরা অন্তরায়। এই পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন এখনো ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ককে অটুট রাখা যায় বোধ হয় ধর্মীয় মৌলবাদের অলৌকিক বন্ধনে। তাই তার দখলদারির প্রতিযোগিতাও সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজের তৃণমূল স্তরেও তার রণধ্বনি বাজে। কায়েমি স্বার্থ জিইয়ে রাখায় এ জরুরি। আমাদের এই বাংলায় ব্যাপারটা গুণগতভাবে ভিন্ন। অমন পরাক্রমশালী কোনো চক্র এখানে গড়ে ওঠেনি। মুসলিম লীগের শাসনে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগে লালায়িত অতিউৎসাহী ফোড়ে বাহিনী একটা গড়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু তারা ছিল শুধু নাচের পুতুল। মূল পাকিস্তানি চক্র তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিল। নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন থেকে শুরু করে মোনেম খান, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী বা মাহমুদ আলী, সবাই এই জাতের।
বিপরীতে শেখ মুজিব যখন দেখেছেন, ওই শোষকচক্রের কাছে এই বাংলা খণ্ড শুধুই শোষণক্ষেত্র, তার ভাষা ও সংস্কৃতি হতমান, তখনই তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন, সামনে থেকে তাকে প্রত্যাখ্যানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঘৃণা থেকে নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ থেকে। এই বাংলার ঐতিহ্য তাকে লালন করে এসেছে। আর্য বা সেমেটিক রক্তের একক ঐশ্বর্য সে ধারণ করে না, যদিও তার মিশ্র সত্তায় তাদের প্রবাহও সে মান্য করে। এতে কোনো হীনমন্যতায় তিনি ভোগেন না। বরং এইটিই তাঁর কাছে ক্রমে হয়ে উঠেছে প্রকৃত গৌরবের। ‘মানুষ যদি হবি তবে কায়মনে বাঙালি হ’ – এই বাণীর সারমর্ম বাস্তবের অভিজ্ঞতায় তিনি সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন। তার সুরক্ষা তাঁর জীবনসংগ্রামের ব্রত হয়ে উঠেছে।
১৯৫৪-র প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের স্মরণীয় বিজয় শাসকদলের কর্মকাণ্ডে জনগণের বিপুল বিরাগের সন্দেহাতীত প্রতিফলন। তবে কার্যত প্রতীকীই থেকে যায়। বিপরীতে শাসক স্বার্থের নোংরা চক্রান্তে নির্মম বর্বরতার কুৎসিত চেহারাটাও খোলা চোখে ধরা পড়ে। নির্বাচনের পরপরই আদমজী পাটকলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিক দাঙ্গার পেছনে পাকিস্তানি অপশক্তির কারসাজির কোনো আড়াল ছিল না। কলকাতায় শেরে বাংলার স্মৃতির আবেগে দেওয়া বিবৃতির কদর্থ করে তাঁকে দেশদ্রোহীর কাতারে সাজানোও ছিল উদ্দেশ্যমূলক। এইসব অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারায় নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জাঁদরেল সেনা অফিসার জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে আপৎকালীন সব ক্ষমতা দিয়ে গভর্নর করে পাঠায়। দখলদারদের কূটচালে গণতন্ত্রের চর্চা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারে শেখ মুজিবও মন্ত্রী ছিলেন। অচিরেই তাঁর ঠাঁই হলো আবার কারাগারে। অবশ্য ক্ষমতার দখলদাররা পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে এলে তাঁকে তখনকার মতো মুক্তি দেয়। তিনি কিন্তু কোনো আপস করেন না। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের শাসন ও শোষণ থেকে ওই কাঠামো বজায় রেখে মুক্তি যে সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে তখন তিনি প্রায় নিশ্চিত।
তবে চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে নির্বাচনে নামায় তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল এই পাঁচমিশালি তরকারিতে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকবে না। আমাদের বাংলার স্বার্থের ব্যাপারে কেউ কেউ উদাসীন থাকতে পারে। সুযোগসন্ধানীদের কায়েমি স্বার্থচক্রের কাছে বিকিয়ে যাবার আশঙ্কাও কম নয়। তিনি চেয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ একক শক্তিতে নির্বাচনী লড়াইতে নামুক। কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাদের আপসকামিতায় তা সম্ভব হয়নি। পরের ক-বছরে এর কুফল বিকট হয়ে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে।
১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। পাশাপাশি করাচিতে গণপরিষদে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব প্রস্তাব করেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে পূর্ব বাংলা করা হোক। কারণ, ‘বাংলা’ শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য …’ তখন তা ছিল অরণ্যে রোদন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যে তিনি স্থির থাকেন। বিচলিত হন না।
এদিকে পাকিস্তানের শক্তিবলয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সেনাবাহিনী ও আমলাচক্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে থাকে। গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছিলেন ডাকসাইটে আমলা। জানা যায়, দুজনই ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের বিশ্বস্ত। দুজনেরই অনুপ্রবেশ ঘটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। পরে গোলাম মোহাম্মদ হন গভর্নর জেনারেল; আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী। সব ঘুঁটি পছন্দমতো সাজিয়ে নানা জায়গায় প্রয়োজনমতো বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে ১৯৫৮ সালে (৭ অক্টোবর) তখনকার গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে যোগসাজশে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব জবরদখল করেন। মুসলিম লীগ ও প্রতিক্রিয়াশীল সব প্রতিষ্ঠান এই কুৎসিত অপকর্মকে স্বাগত জানায়।
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থের অবস্থানকেই এ নিষ্কণ্টক করতে চায়। এই বাংলার ওপরও তার দখল প্রবলভাবে জারি হয়। সুবিধালোভী মোসাহেব জুটতেও দেরি হয় না। কিন্তু আপন অবস্থানে অটল থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান।
সামরিক শাসনে দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ। শুধু সেটুকুতেই অনুমোদন, যাতে থাকে সেপাই রাজের স্তবগান। এদিকে দুবছর আগে শেখ মুজিবের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। তা থেকে তারা সরে আসে না। খেসারত তো তার জন্যে দিতেই হয়। ওই বছরের (১৯৫৮) ১১ অক্টোবর নিবর্তনমূলক আদেশে তাঁকে আটক করে একের পর এক মিথ্যা মামলা চাপিয়ে তাঁকে বন্দি রাখার পালা অবিরাম চলে। ১৯৬০-এর শেষে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তাঁর মুক্তি জোটে। আইয়ুববিরোধী জনমত ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি গোপন তৎপরতাও শুরু করেন। নিকৃষ্ট শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পূর্ণ স্বাধীনতার বিকল্প যে কিছু থাকছে না, এ-কথাও তাঁর মনে হয়। তবে এটাও মাথায় রাখেন, গণচেতনায় তা তখনো নিরাকার এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাবার মতো বাস্তব পরিস্থিতি নিতান্তই অনুপস্থিত। সেপাই-রাজত্বে ডাণ্ডা-আইনে বাক্-স্বাধীনতা খণ্ডিত; প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ।
’৬২-র ফেব্রুয়ারিতে জননিরাপত্তা আইনে তিনি গ্রেফতার হন। তবে ২ জুন সামরিক শাসনের অবসান ও আইয়ুবখানি বুনিয়াদি গণতন্ত্র চালু করার বিধি ঘোষণার পর ১৮ জুন তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার শুরু হলে প্রথমেই তিনি এই জাল গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানান। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কিছু হয় না। আওয়ামী লীগ অবশ্য দৈনন্দিন কার্যক্রমে ফিরে আসে। তবে পাশাপাশি মধু জোগাড়ের লোভে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে কনভেনশন মুসলিম লীগেও স্বার্থান্বেষী চক্র সারাদেশেই ভনভন করতে শুরু করে। ১৯৬৫-র পরোক্ষ নির্বাচনে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে এই বার্তা শোনালেন, তিনি জনগণের নেতা। ফেউ বাহিনীর হুক্কাহুয়াতে কান ঝালাপালা হতে থাকে। ’৬৫-তে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ এনে শেখ মুজিবকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি ছাড়া পান। অনুমান, আইয়ুব খানের সাজানো নির্বাচন যাতে ভণ্ডুল না হয়, সেই জন্যেই তাঁকে জেলে পোরা। এত প্রতিকূলতা তাঁকে দমাতে পারে না। তিনি বরং আরো জেদি হন; আর সবার ভেতরে লড়াইয়ের মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে থাকেন। ’৬৬-র ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে বিরোধীদলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। ১ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ৬ দফা দাবির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এই ৬ দফাতে আছে – ১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে একটি ফেডারেল কাঠামোয় পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার অধীনে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা; ২. কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের সরাসরি অধীনস্থ বিষয় শুধু দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক রাষ্ট্র সম্পর্ক; অবশিষ্ট সব বিষয় স্টেট অর্থাৎ, প্রাদেশিক সরকারগুলোর নিজ নিজ আওতায়; ৩. মুদ্রাব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি প্রতিটি প্রদেশের আলাদা-আলাদা নির্ধারণ। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা পাচার রোধ; ৪. প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা আদায় ও ব্যবহারের অধিকার, ফেডারেল সরকারের প্রাপ্য অংশ সেখান থেকে সরাসরি কেন্দ্রে প্রেরণ; ৫. বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি-রফতানি আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব এখতিয়ারে এবং ৬. পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব প্যারামিলিটারি বা রক্ষীবাহিনী গঠন। দলের সভাপতি হয়েই তিনি এই বাংলার সর্বত্র ৬ দফার প্রচারে নামেন। সরকার নিশ্চেষ্ট বসে থাকে না। ওই এক বছরেই প্রথম তিন মাসে তাঁকে আটক করে আটবার। তিনি পরোয়া করেন না। বাস্তব অবস্থায় প্রতিটি দফার ন্যায্যতা গণচেতনায় সঞ্চারিত হতে থাকে। তাঁর ওপর জনসাধারণের আস্থা ক্রমাগত বাড়ে। জনপ্রিয়তা তাঁর আকাশমুখী হয়। পাশাপাশি ছাত্র-আন্দোলনেও গতি আসে। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব-মোনেম চক্র তাদের জেল-জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রম তাতে প্রবলভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর ভাবমূর্তি তখন শুধু নেতার নয়, ত্রাতারও। মরিয়া হয়ে শাসকচক্র তাঁকে এক নম্বর আসামি করে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক মিথ্যা অভিযোগপত্র সাজিয়ে জেলখানা থেকেই তাঁকে আবার গ্রেফতার করে সেনানিবাসে আটক করে রাখে। সহ-অভিযুক্ত ছিলেন সেনাবাহিনীর ও প্রশাসনের বাঙালি সদস্য কজন। কঠোর প্রহরায় ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে তাঁদের বিচারকাজও শুরু হয়। তবে এতে ভীমরুলের চাকে যেন ঘা পড়ে। বিক্ষোভে ফেটে পড়তে থাকে বাংলার জনগণ। সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দিয়ে বেপরোয়া গুলি ছুড়েও তাদের আর বাগে আনা যায় না।
এদিকে ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ দফা দাবি নিয়ে তারা আন্দোলনে নামে। ৬ দফা দাবি তাতেও ছিল। বাকি কটি ছিল শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রগতিশীল পরিবর্তনের আশায়। তখন কাগজে-কলমে সেনাশাসন ছিল না, – যদিও মেকি গণতন্ত্রের আড়ালে তা-ই ছিল কার্যকর। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন পথে নামে; আর তখনই প্রচ্ছন্ন সেনাশাসনের মুখোশ খসে পড়ে। ২০ জানুয়ারি ঢাকার রাস্তায় তাদের গুলিতে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদ। শেখ মুজিবকে মুক্ত করার দাবি তো ছিলই। এবার যোগ হলো পাকিস্তানি অপশাসন থেকে মুক্তির আকাক্সক্ষা। গোটা দেশে তা দাবানলের মতো ছড়ায়। ক্ষমতাসীনরা তা গায়ের জোরে নির্মূল করার চেষ্টা করে। কারফিউ দিয়ে জুলুম, ধর-পাকড়, খুন হয়ে দাঁড়ায় নিত্যদিনের ঘটনা। গণআন্দোলন একরকম গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তাকে ঠেকাবার ক্ষমতা আর তাদের থাকে না। শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকারে তারা বাধ্য হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি নিরুপায় অবস্থায় তারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। শেখ মুজিব কিংবদন্তি নায়কের মতো কারাগার থেকে নিঃশর্ত মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসেন। পরদিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গণমানুষের পক্ষে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সভা উপস্থিত লাখ লাখ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে তাঁর ‘বঙ্গবন্ধু’ নাম ঘোষণা করে। তখন থেকে এই নামটি একমাত্র তাঁর। ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি পাকিস্তানের এই পূর্বাঞ্চলকে ‘বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত করার আহ্বান জানান। কোনো ফাঁকা আওয়াজে নয়। কারণ তাঁর পেছনে তখন এই অঞ্চলের বিপুল মানবসমুদয়। রাজনৈতিকভাবেও তিনি অন্তত এখানে চালকের আসনে। তাঁর প্রেরণায় গণআন্দোলনের অভিঘাতে দোর্দণ্ড প্রতাপ আইয়ুব খানের দর্প ধুলোয় লুটোয়। গোঁফ নামিয়ে লেজ গুটিয়ে তিনি যবনিকার অন্তরালে চুপসে যেতে বাধ্য হন। তবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন অথবা করতে বাধ্য হন আরেক সেনা মাস্তান ইয়াহিয়া খানকে। এছাড়া বোধহয় অন্য কোনো উপায় খোলা ছিল না। ততদিনে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা সেনাচক্রের কুক্ষিগত। কায়েমি স্বার্থের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব তার অঙ্গুলি হেলনে ওঠে-বসে। কোনো উপেক্ষা সে সহ্য করে না। এখনো অবস্থা বর্তমান পাকিস্তানে গুণগতভাবে ভিন্ন নয়।
তখন দেশব্যাপী ক্ষোভ ও অসন্তোষকে আয়ত্তে আনার একটা পথ খুঁজছিলেন ইয়াহিয়া খান। তিনি ঘোষণা করলেন, এক বছরের ভেতরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন হবে। নির্বাচনে বিজয়ীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী সুবোধ বালকের মতো ব্যারাকে ফিরে যাবে। ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের হাতে না থাকলে তারা যে স্বেচ্ছায় তা কখনোই করে না, আজ পর্যন্ত আমরা তা বারবার দেখেছি। অবশ্য এখন যা পাকিস্তান, যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গৌরবের সঙ্গে যুদ্ধজয় ও লুণ্ঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যার শুরু অষ্টম শতকে, সেখানে গণচেতনায় এর বিরূপতা কখনোই প্রবলভাবে ফোটে না। বেসামরিক সরকার তৈরি হলে তাকে টিকে থাকতে হয় সেনাশক্তিকে সেলাম ঠুকে। বহিরাগত লিয়াকত আলী খান অন্যের ওপর তাঁবেদারি পছন্দ করতেন, যার প্রকাশ ঘটেছে একাধিকবার পূর্ব বাংলাকে হেয় করার নানা আচরণে। কিন্তু ভেতরের সরল সমীকরণে নজর দেননি। তার মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে নিজের প্রাণ দিয়ে। ইয়াহিয়া খান হয়তো ভেবেছিলেন, নাকের সামনে মুলো ঝুলিয়ে অবস্থাটা বাগে আনি। তারপর নির্বাচনের ফলাফল পাশার চালে দান দিয়ে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের ভেতর ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিয়ে উলটে দিতে কতক্ষণ। ভালো মানুষ সেজে জনসংখ্যার অনুপাতে দুই ইউনিটের সদস্য সংখ্যা স্থির করার দাবিও তিনি মেনে নেন। কারণ, তিনি জানতেন পাকিস্তানের একতা ও অখ-তার বুলি আউড়ে আপৎকালে সেনাশাসনের দাওয়াইটা তাঁর হাতে সব সময়েই আছে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর এই চালই তিনি জান্তব আক্রোশে চেলেছিলেন।
তখন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে সম্পূর্ণ মানবিক দায়িত্বে জনসংযোগের কর্ম-কাঠামো তাঁরা রচনা করেন। লক্ষ্য পুরোটাই এই বাংলার মানবসমষ্টির কাছে তাদের নির্যাতন ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরা; কীভাবে সরকারি বিধি-বিধানের সুযোগ নিয়েই এই অঞ্চলের সম্পদ পাচার হয়ে যায় অপরাংশের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানদের হাতে, তা ধারাবাহিক তথ্য সাজিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’ – এই শিরোনামে পোস্টার ছেপে আওয়ামী লীগের পক্ষে দেশের সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। সবই বাস্তব তথ্যনির্ভর। সাধারণ মানুষের চোখ খুলে যায়। এদিকে নির্বাচনের ঠিক আগ দিয়ে ১২ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ও বিষয়-সম্পদের বিপুল ক্ষতিতে পাকিস্তানি শাসকদের তুমুল ঔদাসীন্যে গণঅসন্তোষ আরো বাড়ে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত করে দুর্গত এলাকায় ত্রাণের কাজে হাত লাগাতে দলবল নিয়ে ছুটে যান। তিনি মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠেন। পরে ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এখানে বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টিই জিতে নেয় আওয়ামী লীগ। সাধারণ পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেই সরকার গঠনের অধিকার তিনি পান। ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সদ্যনির্বাচিত ওই দলের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অঙ্গীকারবদ্ধ হন।
কিন্তু পাকিস্তানের দখলদার শক্তি তা সফল হতে দেয় না। নানা ধানাই-পানাই করে তারা কালক্ষেপণ করতে থাকে, এবং জাতীয় সংসদে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানারকম টালবাহানা এখানে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলে। একই সঙ্গে কোনো ঘোষণা না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সমরসজ্জার ব্যাপকতায় তাদের দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়। প্রকাশ্যে চলে আলাপ-আলোচনার অভিনয়। এসব আওয়ামী লীগের ওপর স্নায়ুর চাপ বাড়াবার কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।
উত্তেজনার এই তুঙ্গপর্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব স্থৈর্যে-সাহসে পূর্ণ বিভায় উদ্ভাসিত হয়। জনগণও অতুল আস্থায় সাড়া দেয়। এমন পরিস্থিতিতেই আমরা পাই তাঁর ’৭১-এ ৭ই মার্চের ভাষণ। এমন বলিষ্ঠ-আবেগদীপ্ত কিন্তু সংযত, সাহসী ও সম্পূর্ণ বক্তৃতা বিরল। কোনো সাজানো-গোছানো লিপিবদ্ধ তৈরি ভাষণ এ নয়। সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সুচিন্তিত। বাড়তি কথা একটিও নেই। কিন্তু বলবার কথা কিছুই বাদ পড়ে না। অখ- পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে এ বক্তৃতা, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন আহ্বান আছে, বাঙালির অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশ আছে; কিন্তু কোথাও তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনার কোনো সুযোগ নেই। তিনি গোটা পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগুরু সদস্যের নেতা। সেই অধিকার তিনি বিস্মৃত হন না। তাঁর সব নির্দেশই সবার জন্য প্রযোজ্য। আমাদের এই ভূখণ্ডে সরাসরি প্রত্যক্ষে। অন্য খণ্ডের নাগরিকদের জন্যেও সমান জরুরি। সাড়া দেওয়া-না-দেওয়া তাদের ব্যাপার। আমরা কিন্তু সাড়া দিই। ৭ থেকে ২৫ মার্চ দেশের সব নাগরিক-কর্মকাণ্ড তাঁর ঘোষিত নির্দেশ অনুযায়ী অক্ষরে-অক্ষরে পরিচালিত হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও তা অমান্য করেন না। ভয়ে নয়, তাঁর ভাষণের অন্তর্নিহিত নৈতিক ও বিধিসম্মত অনুজ্ঞায়। তাঁর সংগ্রামী প্রতিভা এই সময়ে শিখর স্পর্শ করে। পরবর্তী কটি বছর তারই অনুসরণ। অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্নতর। দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট অনচ্ছ। তিনি নির্ভর করেন আপন মনোভূমিতে জাগ্রত কল্যাণচিন্তা ও সদিচ্ছার ওপর।
চার
২৫ মার্চ রাতে অস্ত্রে-বর্মে সুসজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুধু ঢাকায় নয়, অন্যত্রও নিরীহ-নিরস্ত্র বাংলার জনগণের ওপর হিংস্র উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। গণহত্যার এই শুরু। আত্মসমর্পণ যদি না করি, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণাই তখন একমাত্র বিকল্প। সেইসঙ্গে তখন হানাদার প্রতিহত করার সার্বিক প্রয়াস। জাতির তখন অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর আকাক্সক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং প্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয়টিই বেছে নেন। তিনি ঘোষণা করেন, ‘আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। … পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।’ টেলিফোন-বেতারে এই বাণী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাৎক্ষণিক যতদূর সম্ভব প্রচারিত হয়। ওই রাতে পাক বাহিনীর আগ্রাসন তুঙ্গে। কিন্তু এই বাংলার মানুষ মাথা নত করে না। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত উচ্চারণ ছিল : ‘… রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। …’ এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসে উন্মুখ জাগ্রত জনতা। দুঃখবরণ, দুঃখভোগ, একটানা অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবন, কিছুই তাদের মনোবল ভাঙতে পারে না। এদিকে অন্তঃসারশূন্য কাপুরুষোচিত দাপটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বীরপুঙ্গবেরা বঙ্গবন্ধুকে আটক করে তাদের খাসতালুকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখে। পাশাপাশি সামরিক ক্যাঙ্গাকোর্টে, যেখানে বাদী ও বিচারক একই সত্তার দুই অবতার, তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করে, যদিও বিরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তা তাৎক্ষণিক কার্যকর করতে পারে না। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম কিন্তু প্রত্যাশিত আধার পেয়ে যায়। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বিপ্লবী সরকার ঘোষিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় মেহেরপুরের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা সদ্যনির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে শপথগ্রহণ করে। তাতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু স্থায়ী রাষ্ট্রপতি। মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থাকে এই সরকারের হাতে।
এদিকে দেশের ভেতরেও সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ বশংবদ ঠেঙাড়ে বাহিনীসহ হানাদারদের ‘তেড়ে মেরে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা’ – নীতি বিফলে যায়। তাদের পাশবিকতার মাত্রা বাড়ে। কিন্তু ভেতর থেকে-বাইরে থেকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যান তাদের মনোবল ভেঙে দেয়। মরিয়া হয়ে তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। স্থানীয় ঘাতক-দালালরা থাকে উৎসাহী সহায়ক অপশক্তি। ক্ষত ও ক্ষতি দুই-ই বাড়ে। প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশছাড়া হয়। কিন্তু কেউ হাল ছাড়ে না। অবশেষে ৩ ডিসেম্বর শুরু হয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। একদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রবাহিনী, অন্যদিকে স্থানীয় সাগরেদদের নিয়ে সুসজ্জিত পাকসেনারা। দু-সপ্তাহ না পেরোতেই জবরদস্ত পাকবাহিনী ও তাদের স্যাঙাতদের ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট অবস্থা। নিরুপায় হয়ে ১৬ ডিসেম্বর তারা পরাজয় মেনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। পাকবাহিনীর তিরানব্বই হাজার সেনা তাদের সব হুকুমদারকে নিয়ে মিত্রবাহিনীর হাতে কয়েদ হয়। অবশেষে বাংলাদেশ মুক্ত। সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম। (যাঁদের জন্ম ১৯৭১-এর পরে, তাঁদের জন্যে এই কথাগুলো বলা। ’৭১-এর স্মৃতি যাঁদের আছে তাঁদের কাছে এ পুনরাবৃত্তি।)
পরিস্থিতি এমন, যেখানে বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে ব্যবস্থা নেবার কোনো সুযোগই আর পাকিস্তানের থাকে না। তিনি এক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈধ প্রধান। ওই রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত। বিপরীতে সেনাপতি থেকে শুরু করে পদাতিক পর্যন্ত তিরানব্বই হাজার পাকসেনা মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দি। বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি না দিলে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে পাকিস্তান অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
সে-দেশেও ক্ষমতার সাময়িক রদবদল ঘটে। সামরিক শাসন উঠে যায়। বেসামরিক নির্বাচিত সরকারে জুলফিকার আলি ভুট্টো হন প্রধানমন্ত্রী।
বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লিতে যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় অবতরণ করেন। এ যেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান কাণ্ডারির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
কৃতজ্ঞ জাতি তাঁকে বরণ করে নেয় ‘জাতির পিতা’ বলে। তিনি কিন্তু ফিরেই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করতে চান। সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পর্বতপ্রমাণ বাধা। প্রধান প্রধান সড়ক, সেতু বিধ্বস্ত। শিক্ষাঙ্গন দীর্ঘদিন প্রায় অচল। লুণ্ঠনে ও অপচয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তহবিল তলানির কোঠায়। জনগণের আশা বিপুল। ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন?’ – এতদিন তারা তা জেনেছে। এখন সেই শোষণ নেই। লুণ্ঠন নেই। তাই প্রত্যেকেই হিসাব কষে আপন-আপন শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনার। অতি প্রকটভাবে যাঁরা স্থায়ী নিয়োগে পদোন্নতির আশা করেন, তাঁদের ভেতর। এমনকি বিচার বিভাগেও। মুনসেফ আশা করেন জেলাজজ হবেন। জেলাজজ উঠতে চান হাইকোর্টে। (এমন কাউকে কাউকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সামনে তখন এ-জাতীয় আবদার করতে দেখেছি। অবশ্য ১৬ ডিসেম্বরের আগ দিয়ে)। আরো একটা সংকট তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা দেশান্তরি হয়ে পাকিস্তানি শাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন, এবং যাঁরা তখন দেশে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কে। সংশয়ের বাতাবরণ একটা আপনা থেকে গজিয়ে ওঠে। অতি গভীরে থাকে আমাদের ওই প্রজন্মের হয়ে ওঠার ঐতিহ্য। ব্যক্তিস্বার্থও নাক গলায়।
এই অগোছাল সময়ে বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্য জনসভায় বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে অন্তত তিন বছর তিনি কাউকে কিছু দিতে পারবেন না। সবার সম্মিলিত উদ্যোগে ও পারস্পরিক সহযোগিতাতেই কেবল এই আপৎকাল উত্তরণ সম্ভব। সকলের সহযোগিতা তিনি চান। বন্যার ঢলের মতো বাস্তব প্রবণতাগুলো কিন্তু সংযত হয় না।
আরো গভীর একটা অসুখ মুক্তিযুদ্ধের কারণেই কিন্তু সংক্রমিত হতে থাকে। যুদ্ধে যারা যোগ দেয়, তাদের অনেকের হাতে মারণাস্ত্র। যারা এর বিরোধিতা করে পটপরিবর্তনে তখন ঘাপটি মেরে থাকে, তাদেরও অনেকের হাতে। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দেন, অবৈধ সব অস্ত্র তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে যেন জমা দেয়। সামান্য অংশই তার জমা পড়ে। অস্ত্রের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। যার হাতে তা থাকে, তাকে তা প্রভুত্বকামী করে তোলে। এই প্রভুত্বের লড়াই তখন সামনে চলে আসে। দেশের ভেতর বিশৃঙ্খলা নানাদিকে ছড়ায়। এমনকি এলাকার দখল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের ভেতরেও। স্বাধীনতাবিরোধীরাও ঘোলাজলে মাছ শিকারে মাতে। কোথাও কোথাও রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে মুক্তাঞ্চল ঘোষিত হয়। সাধারণ মানুষ দিশেহারা। উপায়ান্তর না দেখে স্বল্পশিক্ষিত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দিয়ে বঙ্গবন্ধু রক্ষীবাহিনী গঠন করে তাকে মাঠে নামাতে বাধ্য হন। এর ফল সব জায়গায় ভালো হয় না। অনেকের ভেতর বিরূপতা জাগে। তবে মনে রাখা সংগত, রক্ষীবাহিনী গড়বার দাবি ছয় দফাতেই লিপিবদ্ধ ছিল। সার্বিক সদিচ্ছারই প্রকাশ ঘটে একে গড়ে তোলায়।
প্রকৃতির বিরূপতাও একটা ব্যাপার। তিয়াত্তর-চুয়াত্তর, পরপর দুবছর কাটে খরায় ও বন্যায়। আশানুরূপ ফসল মেলে না। আবার নির্ভরতা বাড়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর। সুযোগ বুঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোক্ষম চাল চালে। কিউবার সঙ্গে বাংলাদেশ বন্ধুত্ব করছে এই অজুহাতে তাদের খাদ্য সরবরাহ-জাহাজের মুখ তারা মাঝদরিয়াতেই ঘুরিয়ে দেয়। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যায় না।
আর একটা সংকট প্রকট হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে; সূত্রপাত কিন্তু আরো আগে আইয়ুব-মোনেম জামানায়। ছাত্রসমাজে দখলদারি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (এনএসএফ) নামে একটা পেটোয়া বাহিনী তারা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বাড়তে দেয়। অলিখিত নির্দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পড়ুয়া সন্তানরা তাতে ভিড়তে বাধ্য হয়। আসল ক্ষমতা থাকে এক মাফিয়া চক্রের দখলে। তাদের বিরোধিতা কেউ করলে তাকে মারপিট-নির্যাতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুরু ’৬২-তে মার্শাল ল তুলে নেবার পর থেকে। চরমে ওঠে ’৬৪-৬৫-তে। ’৬৯-এর ১১ দফাকেন্দ্রিক সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনে তারা বুদ্বুদের মতো হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু জোর যার মুল্লুক তারের যে সংস্কৃতি তারা চালু করে, তা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। স্বাধীনতার পর মারণাস্ত্রের ঝনঝনানিরও শুরু। শাসকশক্তির আনুগত্যই সেখানে নিয়ন্তার ভূমিকায়। যদিও দখলদারির প্রতিযোগিতায় সেখানে অন্তর্দলীয় কোন্দলও প্রকট। ভোলা যায় না ওই সময়ে এক ছাত্রনেতার নির্দেশে একই দলের অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ সন্দেহে সাতজন ছাত্রকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে মেরে ফেলার ঘটনার কথা। ওই ছাত্রনেতা অবশ্য পরে সমর শাসনের কালে সেনানায়কের কাছে দাসখৎ লিখে তাঁর দলে যোগ দেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলে ওই সময়ের এমন ছাত্র আরো চোখে পড়বে।
বাস্তব অবস্থা যখন এমন, তখন বঙ্গবন্ধু অনুভব করেন, সংসদীয় গণতন্ত্র এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট উপযোগী নয়। তিনি মনে করলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সব শক্তিকে একত্র করে মিলিত চেষ্টায় অগ্রসর হলে হয়তো সুফল মেলা সম্ভব। তাতে যদি একক আওয়ামী লীগের বিলুপ্তি ঘটে, তবুও। তাই পঁচাত্তরের শুরুতেই তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা ঘোষণা দেন; এবং ২৫ জানুয়ারি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করে প্রগতি ও সমতার পক্ষে যাঁরা, তাঁদের সমন্বয়ে একটি মাত্র সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের বার্তা দেন।
প্রকৃতপক্ষে এ একদলীয় নয়, একাভিমুখী যৌথ শাসন। কিছুদিন আগে তাঞ্জানিয়ায় জুলিয়াস নায়ারের রাষ্ট্রশাসনে এ-রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। আরো আগে যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল টিটোও এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগের পরিণতি কী হতে পারত, আজ সে নিয়ে শুধু জল্পনা-কল্পনাই সার। কারণ ওই বছরের ১৫ আগস্ট ঘটে ইন্দ্রপতন। সামরিক বাহিনীর ভেতর থেকে এক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। শুধু তাঁর দুই কন্যা বাইরে থাকায় রেহাই পান। নিহত হন সপরিবারে তাঁর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি। একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। তবে ওই উদ্যোগ (বাকশাল) দুঃসাহসী ছিল কি না এবং তা বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় সময়োচিত ছিল কি না, এসব প্রশ্ন করাই যায়। যদিও সবই পশ্চাদ্দৃষ্টিতে সম্ভাবনার বিচার-বিশ্লেষণ। এবং আবশ্যিকভাবে অসম্পূর্ণ। তবে সরষের ভেতরেই যে ভূত ছিল এ তো সাদাচোখেই দেখা যায়। খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, দুজনই ছিলেন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তাঁদের হিংস্র বাংলাদেশ-বিদ্বেষের আরো পরিচয় মেলে ওই বছরই ৩ নভেম্বর ঘাতকদের জেলখানার ভেতরে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার তিন সদস্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অনুমতি দেওয়ায়। বহুরূপী আরো কতজন ছিলেন, তা কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায়। তবে আক্ষেপ কিছুতেই যায় না, যখন জানতে পাই সেনাবাহিনীর এক হন্তারকের নিত্য যাতায়াত ছিল বঙ্গবন্ধুর বাসগৃহে, – এবং তা তাঁর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে। এটা তো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে হবার কথা নয়, উৎস নৈর্ব্যক্তিক সামষ্টিক অস্বীকার। এমন অমানবিক ঘৃণার বসতি এখনো এদেশে আছে। কখনো সুযোগ পেলে ছোবল দেয়; কখনো বা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। সুযোগ অবশ্য তৈরি করি আমরাই। লোভের রাজ্যে পৃথিবী সুযোগময়। যার যার মতো তাই খুঁজি। নইলে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে যিনি রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন, পরে তিনি বিএনপির পক্ষে সংসদ সদস্য হতে যাবেন কেন?
বঙ্গবন্ধু যে নির্মম হতে পারেন না, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা মনে করেও এবং তাঁর প্রবাদতুল্য স্মরণশক্তি, যে-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন, দুটো বিরল সৎগুণই কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁর বিপক্ষে যায়। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগে শিক্ষানবিশির সময় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন অনেকে। পরে যে-দলই করুন তাঁদের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা আগের মতোই থেকে যায়। অথচ তারা একেকটি বিষধর সাপ। খোন্দকার মোশতাকের কথা আগেই বলেছি, এছাড়াও ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ সবুর, শাহ আজিজুর রহমান ও এই রকম আরো অসংখ্যজন তাঁর উদারতার সুযোগ নেন বারবার। কলকাতা জীবনে তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ। তাঁর স্মরণশক্তি স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁদের ওপর তাঁকে কঠোর হতে দেয়নি। অপশক্তির শিকড় আলগা হয় না। দেশ কিন্তু তার দাম দেয়।
অথবা এমনও হতে পারে, জনগণ যে তাঁকে ‘জাতির পিতা’র মর্যাদা দিয়েছে, তিনি হয়তো (‘হয়তো’ই, কোনো বাস্তব তথ্য-প্রমাণ আমার হাতে নেই) তার সমস্তটার যোগ্য হয়ে উঠতে চেয়েছেন। মনে আছে, শিক্ষাঙ্গনে ও দেশের কোনো কোনো স্পর্শকাতর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ওই সময়ে যখন অস্থিরতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তখন ঢাকায় এক বৃহৎ জনসভায় তিনি আবেগরুদ্ধ স্বরে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ‘তোমরা আমারে জাতির পিতা বানাইছ। আমার কথা তোমাদের শুনতে হবে। ওইসব বাড়াবাড়ি আর করবে না। নইলে …।’ এ যেন এক গোষ্ঠীপিতার বাইবেলীয় অনুজ্ঞা। সুযোগসন্ধানী অনুসারীরা তাঁর কথা শোনেনি। তিনি কিন্তু কঠোর হতে পারেননি। ‘পিতা’ তো তিনি ভালো-মন্দ মিলিয়ে সমগ্র জাতির।
তবে যুগান্তকারী জাতীয় বিপ্লব ও উত্থানের কালে এমন বিয়োগান্ত পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী নয়। বিপুল আশা ও তা পূরণে নানা বাধা-বিপর্যয় মানব অভিজ্ঞতায় বারবার আসে। সংশ্লিষ্ট জনসমুদয়কে সাধারণ-স্তরে টেনে নামায়। যে ফরাসি বিপ্লব মানব সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে দেয়, কিংবদন্তিতুল্য তার সব অধিনেতাই পরের দশ বছরে পারস্পরিক বিরোধে গিলোটিনে কাটা পড়েন। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস কম শোচনীয় নয়। গৃহযুদ্ধ, পরে স্ট্যালিনের উত্থান বিপুল নিস্তব্ধ হাহাকারের জমাট স্তূপ ভবিষ্যতের কাঁধে চাপিয়ে যায়। বিপ্লব তার সব সন্তানকে গিলে খায় – এমন প্রবাদের বাস্তব উদাহরণ যেন এসব। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ঔপনিবেশিকতার অবসানের কালে প্রায় সব দেশে অবিসংবাদী জাতীয় নেতাদের ভাগ্যে জুটেছে অসম্মানের অবসান। ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তোর অভ্যুত্থানে ঘটে জাতির জনক সোকার্নর অপমানজনক বিদায়। আলজেরিয়ার অসাধারণ স্বাধীনতাসংগ্রামী বেন বেল্লা ও বেন খেদ্দাও বিতাড়িত হন স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে। কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা তো নিশ্চিহ্ন হন স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্তেই। আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ইতিহাস আরো নির্মম, নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতায় ও বঞ্চনায় আকীর্ণ। জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবের কথা তো আরো করুণ। বর্ণবৈষম্যবিরোধী আপসহীন স্বাধীনতাসংগ্রামী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে রাষ্ট্রপতির আসনে বসেন প্রায় তিন দশক আগে। অসমর্থ হয়ে পড়লেও গদি আঁকড়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত গত বছর তাঁর দেশের জনগণই তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নামায়। আমাদের বঙ্গবন্ধু কখনো আত্মমর্যাদা হারাননি। ঘাতকরা যখন হানা দেয়, তখনো না। তাঁর নাম উচ্চারিত হয় আয়ারল্যান্ডের ডি ভ্যালেরা, কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা বা চিলির আইয়েন্দের সঙ্গে সমলয়ে। তবে ইতিহাসের গতি কোথাও সরলরেখায় নয়। প্রতিটি কালবিন্দু নতুন। অতীতের প্রেরণা বা হতাশা তার সঙ্গী সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের দায় ও দায়িত্ব তার নিজের। আজ আমাদের প্রেক্ষাপট কেমন সেদিকে তাকানোও তাই জরুরি। এবং তা বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের অশেষ ঋণের কথা মাথায় রেখেই।
বাস্তবের অতি সরলীকরণে অনেক সময় তার কাঙ্ক্ষিত রূপটি ফুটে উঠতে দেখি। তাতে তৃপ্তিও পাই। কিন্তু ভেতরের উলটাপালটা চোরা স্রোতগুলো আড়ালে চলে যায়, অথবা তাদের দেখতে চাই না। এতে আবেগ হয়তো আমাদের তুষ্ট হয়, অথবা তা ভেঙে পড়ে। কিন্তু তার পূর্ণস্বরূপ আড়ালেই থেকে যায়। ’৫৪-র প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছে, এখানে আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, একথা আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলে থাকি। কিন্তু মানুষের মনোজগতে ও আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে-শক্তির তারা প্রচ্ছদ ছিল, গঠনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় যাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না, তাদের মূল ভেতর থেকে পুরোপুরি উৎপাটিত হয়েছে, একথা কি আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি? আমরা দেখি ৯২-ক ধারা ততদিনই বলবৎ ছিল, যতদিন না যুক্তফ্রন্টের ভেতরে ফাটল ধরানো যায়। তাতে সফল হলে তারপরে তো বাজার বুঝে দান দিয়ে সময় মেপে ঘোড়ার হাতবদল। যুক্তফ্রন্ট রসাতলে যায়। ’৫৮-তে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে আসলি চিজ বেরিয়ে আসে। তা আদি মুসলিম লীগের নতুন অবতার। দশ বছর রাজত্ব করে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করে ‘ডিকেড অব রিফর্মস’। তাতে এ-অঞ্চলের ছিঁচকেদের কোমর দুলিয়ে নাচ দেখাতে তর সয় না। তবে সবকিছু ভেস্তে যায় ৬ দফা, ১১ দফার ডাকে। মুসলিম লীগ-পসন্দ ইমানদাররা ঘাপটি মেরে থাকে।
’৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর ’৭২-এর সংবিধান তারা আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করে না। মুসলিম লীগের নতুন অবতারদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার পরও কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা বাংলাদেশের আদি সংবিধানে পুরোপুরি ফিরে যেতে পারিনি। ফিরে যাওয়া নাকি সময়োচিত নয়। বোঝা যায়, মুসলিম লীগ এখনো আমাদের মনোজগতে একখণ্ড জমি আঁকড়ে পড়ে আছে। শুধু এখানে নয়, বিশ্বাসীদের সহিংস রাজত্ব অন্যত্রও।
আজকের বাংলাদেশ অনেককে আশান্বিত করে। জাতীয় আয়ে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা সাতের ওপর। এটা উন্নয়নের লক্ষণ বই কি! মোট আয়ে সেবা খাতের দখলে শতকরা প্রায় বায়ান্ন ভাগ। শিল্প ও শিল্প-সম্পর্কিত খাত থেকে আসে শতকরা তিরিশের মতো। কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কাজ থেকে শতকরা আঠারো ভাগের এদিক-ওদিক। উন্নত অর্থনীতির লক্ষণ কিছু কিছু ফুটে ওঠে বই কি! কিন্তু জাতীয় কল্যাণের ছাপ তাতে পড়ে কি? সেবা খাতে আমাদের আয় বৃদ্ধি বহুলাংশেই কি উৎপাদনের গুণ ও পরিমাণগত পরিবর্তনের চেয়ে খরচের অপ্রয়োজনীয় অথবা লোকদেখানো খাত সৃষ্টি করে দ্রব্যগুণ অপরিবর্তিত রেখে তার দামে তারতম্য ঘটাবার ফল না? এতে মানুষের প্রকৃত তৃপ্তি কতটুকু বাড়ে? মানছি, কাজের পরিসর বড় হয়। এমনটি না হলে বেকারত্বের চেহারায় আমরা আতঙ্কিত হতাম। কিন্তু মূলে আমাদের সত্য সমৃদ্ধি কতটুকু হয়? দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বেলাতেও প্রভাবশালী মধ্যস্বত্বভোগী চক্র প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এটাও আয় বাড়া সত্ত্বেও কল্যাণ না বাড়ার লক্ষণ। মানুষের মতিগতি বদলে যেতে থাকে। সবটাই তার শুভ নয়। কিন্তু অর্থনীতি ক্রমশ অশুভ শক্তির খপ্পরে চলে যাওয়া শুরু করে।
অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল অবশ্য পরাক্রমশালী দেশগুলোও। যুক্তরাষ্ট্রে মারণাস্ত্র খাতে উৎপাদন যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই সেখানে ধসে পড়বে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য মারণাস্ত্রের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনাও সেখানে সম্ভব হয় না। এতে জনকল্যাণ কতটা বাড়ে, এ-প্রশ্ন তোলা কি অস্বাভাবিক? এসব প্রশ্ন অবশ্য বঙ্গবন্ধুর কালে আমাদের জন্য ছিল অবান্তর। সব মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচুক, এই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সেখানে তাঁর আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ ছিল না।
একাত্তরে আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আমাদের হাতের একটি তুরুপের তাস। অন্যটি পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে রফতানি আয়। দুটোই কিন্তু আজ অবান্তর প্রায়। সহজলভ্য বিকল্পে বাজার ছেয়ে যাওয়ায় পাট আর আমাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক হাতিয়ার নয়। এদিকে জনসংখ্যা বেড়ে আজ ষোলো কোটি ছাড়িয়েছে, যদিও বৃদ্ধিহার কমে দাঁড়িয়েছে এখন বার্ষিক
১.৫-এর মতো। বিশ বছর পরে এই জনংখ্যা বিশ কোটি ছাড়াবে। জলবায়ু দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করায় এর ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে আমাদের কি কোনো ভাবনা আছে? বনখেকো-নদীখোকো চক্রের আগ্রাসন কিন্তু ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। সব শহরে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় ভরাট করে উঠছে বহুতল ভবন। বিশ বছর পর দেশ কি বাসযোগ্য থাকবে? বঙ্গবন্ধুকে মাথায় নিয়ে এর উত্তর খোঁজার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই। কারণ মানুষ অতীত থেকে প্রেরণা পেলেও বাস করে বর্তমানে। দায় তার ভবিষ্যতের কাছে।
শুরুতে এই ভূমণ্ডলে কালযাত্রার একটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। তাতে দেখেছি, কারণ যা-ই হোক মিশ্রণের ধারা এখানে বহমান। এবং সব ধারণাই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিবর্তমান। উৎসে ফেরা জীবনের ধর্ম নয়। বরং উৎসারণে বিবিধ ভাবনার সংযোজন ও সমন্বয় তাতে গতি ও বিস্তার আনে। যখন এ-ভূভাগ ব্রিটিশ উপনিবেশ, তখনো। পাকিস্তান পর্ব পেরিয়ে ঘটে এখানে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তাতে বৃহত্তর পরিমণ্ডলের চলমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি খণ্ডিত হয় না। বরং বাংলাদেশ তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই যোগ করায় নেতৃত্বে থাকেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর দ্বন্দ্বময় জীবনে থাকে তারই প্রতিফলন। তিনি মাথানত করেন না। অর্জিত মূল্য কিছু প্রত্যাখ্যানও করেন না। আমাদের বাংলাদেশের অণুতে অণুতে মিশে আছে যে-জীবনরস, তিনি তারই পূর্ণতা খোঁজেন। কোনো আপস করেননি। ব্যর্থও হননি। পরবর্তী প্রজন্মের এটিই মনে রাখবার। যদিও মুক্তমনে মূল্য সংযোজনের দায় তার নিজের। এই সংযোজন কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। রাষ্ট্র ও ঐতিহ্য কদাচিৎ সমার্থক। আমরা দেখেছি, একমাত্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্ব ছাড়া কোনোকালেই পুরো উপমহাদেশ এক রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য হয়নি। এতে বহুবৈচিত্র্য নিয়ে মানবসমুদয়ের দেওয়া-নেওয়ায় কোথাও কোনো বাধা পড়লেও তা স্থায়ী হয়নি। বহুমিশ্রণে আপন পরিচয় আলাদা চিনিয়ে দিয়ে এই বাংলাও তার অবদান সগৌরবে তুলে ধরতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।
00 কালি ও কলম ( শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিয়ক মাসিক পত্রিকা) হতে সংগৃহিত।
-

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম
আখতার হামিদ খান
নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত, এমনকি বহির্বিশ্বেও বহু ভাষায় ব্যাপ্ত। কেননা, বাংলা সাহিত্যের বিপ্লবাত্মক কাব্যচেতনার তিনি প্রধানতম কবি। যদিও এটিই তাঁর প্রধান পরিচয় নয়। তিনি শুধু কবিতাতেই বিপ্লব-বিদ্রোহের কথা উচ্চারণ করেননি। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যম-প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সঙ্গীতেও তাঁর বিপ্লবাত্মক চেতনার বিপুল উপাদান ছড়িয়ে আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর অনন্য মৌলিক কীর্তির বিশ্লেষণ এ যাবৎ আমরা খুব কমই করতে পেরেছি। তাই দ্রষ্টব্য, তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্মের গবেষণায় এ যাবৎ বিষয় ও বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে কম, বরঞ্চ কোন রচনা কোথায়, কার অনুরোধে কখন রচিত এবং কে তা উদ্ধার করেন এই বিতর্কেই অর্ধশতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।
নজরুল নিছক রস সঞ্চারের জন্য সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেননি। জাতির প্রতি তাঁর একটি কমিটমেন্ট ছিলো। দেশকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করা, গরিব মানুষের-শ্রমজীবী দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অত্যন্ত সচেতনভাবেই আত্মনিয়োগ করে ছিলেন তিনি। বলতে কি, একবারে শূন্য হাতে শুরু হয়েছিলো তাঁর এই সংগ্রাম কলম ছিলো একমাত্র সঙ্গী। করাচির সেনানিবাস থেকে ছাড়া পেয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতা এসে সরকারি চাকরির সুযোগ উপেক্ষা করে, সচ্ছল অর্থনৈতিক জীবনের হাতছানিকে মাড়িয়ে অনিশ্চিত সংগ্রামী জীবন-ই বেছে নিলেন কবি। দেশকে মুক্ত করার জন্য কেবল বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের কথাই বললেন না, সমাজের কুসংস্কার-বন্ধন, জরা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও মৌলবাদীদের ফতোয়াবাজির মর্মমূলেও কুঠারাঘাত করলেন।
‘আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, নজরুল চর্চা মানে কেবল জন্মজয়ন্তী পালনকে বোঝায় না। অথবা নজরুলের গানের প্রসার দ্বারাও নজরুল চর্চার ব্যাপকার্থের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা চলে না।’
বাঙালি মুসলমান এই নজরুল ইসলামের রচনাতেই সেদিন প্রথম দেখতে পেয়েছে যে, তার মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফের ভাষা আরবি একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। তার উপর সমকালে একমাত্র মুসলমান লেখক ছিলেন নজরুল ইসলাম, যে তাঁর স্বজাতি ও স্বধর্ম সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীল থেকেও চূড়ান্তভাবে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর এসব ভূমিকা, সেইসঙ্গে সাম্যবাদী ধারার রাজনৈতিক আদর্শ, দলিতের মুক্তির ঘোষণা অথবা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে হাইদরী হাঁক ১৯৪২ সালে কবির অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মিইয়ে গেল। এর কারণ যে কি, তার বহুরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে পারে। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভীতি-অনিশ্চয়তা এবং যুদ্ধোত্তর দেশভাগের নানা সংকট, মধ্যবিত্ত বাঙালি, বৈশিষ্ট্যে যে আত্মকেন্দ্রিকতার সমাজে কবিকে নিয়ে ভাবার সময় সুযোগ খুব একটা হয়নি। কিন্তু দেশ ভাগের ২/৩ বছরের মধ্যে এইসব ঝক্কি-ঝামেলা কেটে যাবার পর বাঙালি সত্যি আর ত্রিশের দশকের মতো কবিকে নিয়ে মেতে উঠলো না। সমকালের বাঙালি নেতৃত্ব বা নজরুলপ্রেমীরা কোন অবস্থাতেই এই ভূমিকার জন্য ধন্যবাদর্হ নন।
চুরুলিয়ার দুখু মিঞা বালক বয়সে যে একদিন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অজয় নদীর প্রবাহের মতো জীবনকে জয় করতে বেরিয়ে ছিলো, সে আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বাঙালি জাতিসত্তার এক মহিমান্বিত মহানায়ক। জাতিসত্তার প্রভাবকে যে সীমান্ত কখনো বিপন্ন করতে পারে না তারও প্রমাণ নজরুল ইসলাম। এই নজরুল আজ তাই বাংলাদেশ ও ভারতের-পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও বিশ্বের সব প্রবাসী বাঙালির জাতীয় কবি।
এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরাসহ বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি বাঙালির অধিকাংশেরই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে, সাহিত্যিকের কর্তব্যবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণা নেই। কারণ, ভূমিহীন নিরন্নের ক্ষেত্রে অশিক্ষা এবং উচ্চবিত্ত সমাজে সাহিত্য মার খায় বিত্তের জৌলুসের কাছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজেই মূলত সাহিত্য রচয়িতা ও ভোক্তার উপস্থিতি। কিন্তু সংখ্যায় এই শ্রেণীটি নগণ্য, ত্রিশ কোটির এক-তৃতীয়াংশেরও কম। নিম্নবিত্ত-অশিক্ষিত, জীবিকাই যার জীবন সংগ্রামের প্রধান ধর্ম, তার কাছে সাহিত্য তেমন কোন অপরিহার্য বিষয়ই নয়। সেই বাঙালি সমাজে আপামর হয়ে এই যে উঠে এলেন নজরুল ইসলাম। তার মূলে যতটা না ক্রিয়াশীল তাঁর সাহিত্য, তার চেয়ে বেশি তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক ভূমিকা ও সঙ্গীতের যুগান্তকারী আবেদন। নজরুল নিজেই বলেন, ‘অশিক্ষিত বাঙালি যে লিখতে পড়তে জানে না, সে গান বোঝে।’ সঙ্গীতের মাধ্যমেই তিনি তাদের জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। সাহিত্যকে এই যে গণমুখী করে তোলা, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া- বাংলায় আর কোনো লেখকের কলমের এমন ধার সেদিন পরিলক্ষিত হয় না।
রবীন্দ্র যুগে, বাঙালি যখন তাঁর কলমের ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত। তখন নজরুলের উত্থানপর্বটি অনায়াস সাধ্য ছিলো না। কিন্তু প্রবল বিক্রমে নজরুল উঠে এলেন, রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে সাহিত্য-সাংবাদিকতায় বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ চেতনার নতুন ধারা সৃজন, যুগ মনষ্কতার বিচারে যা রেঁনেসাসরূপী, নজরুলের এই স্বাতন্ত্র্য ও যুগ¯্রষ্টার গৌরবকে কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথও করেননি। বরং অসীম মমতায় অদ্যোপান্ত অনুপ্রাণিত করেছেন নজরুলকে।
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নজরুলকে বা নজরুল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে টেনে আনা দূরভিসন্ধিমূলক। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে গেছেন। ‘ধূমকেতু’ মামলায় কারারুদ্ধ তরুণ নজরুলকে ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যটি উৎসর্গ করে তার একটি কপি কারাগারে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘নজরুলকে আমি ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাঁকে ‘কবি’ বলে সম্বোধন করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র। … কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝঙ্কার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও এই সুর বাজত। …. আমি তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠে আর্শীবাদ জানাচ্ছি। আরো বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।’
রবীন্দ্র-নজরুলকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের মতো আরেকটি মহল নিজের মাথায় পাথর ভাঙ্গার মতো রবীন্দ্র ছায়ায় অবস্থান করেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও বিতর্কে লিপ্ত হয়। বাঙালি সমাজের এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলের উদ্ধত অনাচার অতীতের সকল মাত্রাকে অতিক্রম করে। বিশ্বচেতনায় ধার বা আত্মসাতের কোন প্রশ্নই আসে না। চেতনাগত সাদৃশ্য থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ বা ‘ঘরে-বাইরে’র মধ্যে এই সাদৃশ্য যদি পরিলক্ষিত হয়ই, তাতে দোষটা কি তা কেউ স্পষ্ট করে বলছেন না। আবার একথাও বলছেন না যে, রবীন্দ্রনাথ এগুলো অনুবাদ করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।
একইভাবে ‘বিদ্রোহী’ রচনার পর নজরুলকে নিয়েও টানা-হেঁচড়া কম হয়নি। কবি মোহিতলাল ছিলেন এই অনাসৃষ্টির হোতা। অথচ ‘মোসলেম ভারতে’ এই নজরুলের কবিতা পড়েই মোহিতলাল প্রথম বাংলা সাহিত্যের স্বারশ্বত ম-পে নজরুলকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। একইভাবে ‘সবুজপত্রে’র প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক নজরুলের অমনোনীত লেখাটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পেয়ে এবং ছেপে যে ‘প্রবাসী’ আরো চাই বলে মন্তব্য করেছিলো, হিন্দু রমণী প্রমীলাকে বিয়ে করায় সেই ‘প্রবাসী’সহ আরো কয়েকটি পত্রিকা চিরতরে নজরুলকে অপাঙক্তেয় ঘোষণা করে। আর কোনদিনই এরা নজরুলের লেখা ছাপেনি।
মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করায় শুরু থেকেই ‘মোহাম্মদী’ নজরুল ইসলাম ও ‘সওগাতে’র অব্যাহত নিন্দাবাদ করেছে। ‘সওগাত’ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর ‘সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন, পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণার লালন ও প্রগতিবাদের বিরোধিতার কারণে বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে থাকায়- এক পর্যায়ে মোহাম্মদী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয় এবং নজরুল ইসলামের লেখা ছেপেই সেদিন পত্রিকাটি তাঁর পড়ন্ত বাণিজ্যিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলে। এ প্রসঙ্গে ‘নজরুল এছলাম’ শীর্ষক মাসিক ‘মোহাম্মদী’র পঞ্চম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা ১৯৩২-এর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি প্রাণিধানযোগ্য। দীর্ঘ প্রায় এক দশক অব্যাহতভাবে নজরুল ইসলামের বিরোধিতা ও নিন্দাবাদের পর দীর্ঘদিনের অনাচারকে ‘মোহাম্মদী’ তীব্র অভিমান হিসাবে উল্লেখ করে বলছে, ‘কবি ও সাহ্যিতিক হিসাবে নজরুল এছলাম বিপুল খোদাদাদ শক্তির অধিকারী, একথা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাঁহার প্রতিভা ও শক্তিমত্ততার প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ ও গৌরব, তাহা উপভোগ করার জন্য আমাদের প্রাণও দীর্ঘকাল হইতে ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে তাহা ভোগ করিবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়ে উঠে নাই, তাহা নজরুলের প্রতি আমাদের এবং আমাদের ন্যায় অধিকাংশ সমাজ সেবকের একটা তীব্র অভিমান ছিল। …. এছলামের আদর্শ এবং মুছলমানের দরদ ও অনুভূতি আজ তাঁহার কণ্ঠকে যে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাকে অন্তরের অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য নজরুলের এই শ্রেণীর গজল, সঙ্গীত ও কবিতাগুলি আমরা মোহাম্মদীতে ছাপিবার ব্যবস্থা করিতেছি। এই সংখ্যা হইতে তাহার সূত্রপাত করা হইল।’১
প্রবাসী গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি’র প্রধান কাজই ছিলো নজরুলের বিরুদ্ধাচরণ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। এই সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেই নজরুল উঠে এলেন বাঙালি জাতিসত্তার ডাক দিয়ে মহানায়কের দৃপ্ত পদচারণায়।
এই প্রতিক্রিয়াশীল বিরুদ্ধবাদীরা সব জায়গাতেই তৎপর। এদেরই বশংবদরা রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বর্জন করে। অথচ ধর্মের সবচেয়ে বড় শিক্ষাই হচ্ছে নিরপেক্ষতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান। যারা এসব উদ্যোগ নিচ্ছে, তাদের মধ্যে হিন্দু বা মুসলমান কোন বৈশিষ্ট্যেরই অস্তিত্ব নেই। কারণ এরা ছাত্রজনতার মিছিলের উপর ট্রাক তুলে দেয়, গুপ্তহত্যার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ খুন করে। কোন ধর্মেই এই শিক্ষা নেই। এগুলো এরা করেছে রাজনৈতিক স্বার্থে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে।
পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেও হিন্দির অব্যাহত আগ্রাসন মোকাবিলায় ক্লান্ত এই কবিপ্রেমিরা কিছু গান শোনা ছাড়া নজরুল চর্চার ধারে কাছেও যাননি। গোড়ায় গলদ থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে সেহেতু অনাসৃষ্টির অভিযোগ আসছে না। ফলে কবি অসুস্থ হওয়ার পরপর নজরুল চর্চা ও অসুস্থ নির্বাক কবির জীবনে ১৯৪২ সাল থেকেই নেমে আসে অন্ধকার যুগ। মহাযুদ্ধ সংকটকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও কিছুতেই দায় এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ নজরুল চর্চা ব্যতীত আর সব কাজই কম বেশি চলেছে। একমাত্র নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি কবির জন্মজয়ন্তী উদযাপন ছাড়া এসময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কাজই করতে পারেনি।
আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, নজরুল চর্চা মানে কেবল জন্মজয়ন্তী পালনকে বোঝায় না। অথবা নজরুলের গানের প্রসার দ্বারাও নজরুল চর্চার ব্যাপকার্থের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা চলে না। যদি সে গান হয় বাণী ও সুরের বিকৃতিতে পূর্ণ। এখানে যারা নজরুলের গানের চর্চা নিয়ে গর্ববোধ করেন, তাদের জন্য কবি স্বয়ং একটি দুঃসংবাদ রেখে গেছেন। মঞ্চ বা সভা-সমাবেশের কথা ছেড়েই দেয়া যাক। প্রতিদিন রেডিওতে নিজের গানের বাণী ও সুরের বিকৃতিতে ক্ষুব্ধ কবি সাপ্তাহিক ‘নবশক্তি’ পত্রিকার ২৩ আগস্ট ১৯২৯ সংখ্যায় লিখেছিলেন,‘ … আমার নিজের দিক থেকে কিন্ত স্পষ্ট গোটা কতক কথা বলবার আছে এ নিয়ে। তার কারণ আমার গান প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন আর্টিস্ট রেডিওতে গেয়ে থাকেন এবং আমার সৌভাগ্যবশত তা শুনেও ফেলি। এক উমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং কদাচিৎ দু-একজন গাইয়ে ছাড়া অধিকাংশ ভদ্রলোক বা মহিলা আমার গান ও সুরকে অসহায় ভেবে (বা একা পেয়ে) তার পি-ি এমন করেই চটকান যে মনে হয় ওর গয়ালাভ এখানেই হয়ে গেল। সে একটা রীতিমতো সুরাসুরের যুদ্ধ।’২
কবির এই খেদোক্তিতে তাঁর গানের করুণাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আরো যে একটি নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাহলো নজরুল সঙ্গীতের প্রায় অধিকাংশ গবেষকেরই অভিমত যে, তাঁর গানের বাণী ও সুরের বিকৃতি শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পর। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। কবির জীবদ্দশাতেই বেসরকারিভাবে জাতীয় সংবর্ধনা পাবার আগেই নিয়মিত রেডিওতে তাঁর গান প্রচারিত হচ্ছে এবং সমতালে তার বাণী ও সুরের বিকৃতিও ঘটছে।
মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরকারি আনুকূল্য অর্জনের অভিযোগে প্রতিক্রিয়াশীলরা যতটা তৎপর ছিলো, নজরুলের ক্ষেত্রে তাদের ততটা তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। তাদের দুর্ভাগ্য যে, নজরুল ইসলামের প্রায় সব বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় বইগুলোই শাসক ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করে। বইগুলো হচ্ছে, ‘যুগবাণী’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘দুর্দিনের যাত্রী’, ‘প্রলয়শিখা’ এবং ‘চন্দ্রবিন্দু’। শেষপর্যন্ত বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ হয়নি কিন্তু এ উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার চিহ্নিত করেছিলো এ ধরনের গ্রন্থগুলো হচ্ছে ‘অগ্নিবীণা’, ‘সর্বহারা’, ‘ফণি-মনসা’, ‘রুদ্রমঙ্গল’, ‘সঞ্চিতা’ ও ‘কুহেলিকা’।
সুত্র: এখন সময়







