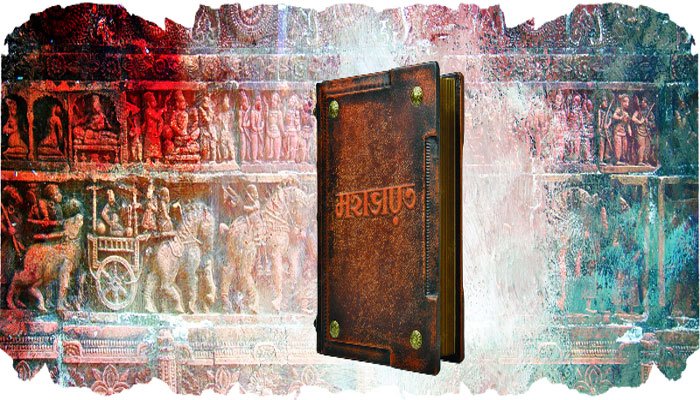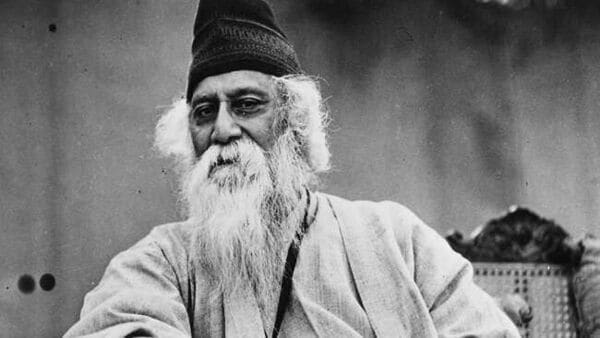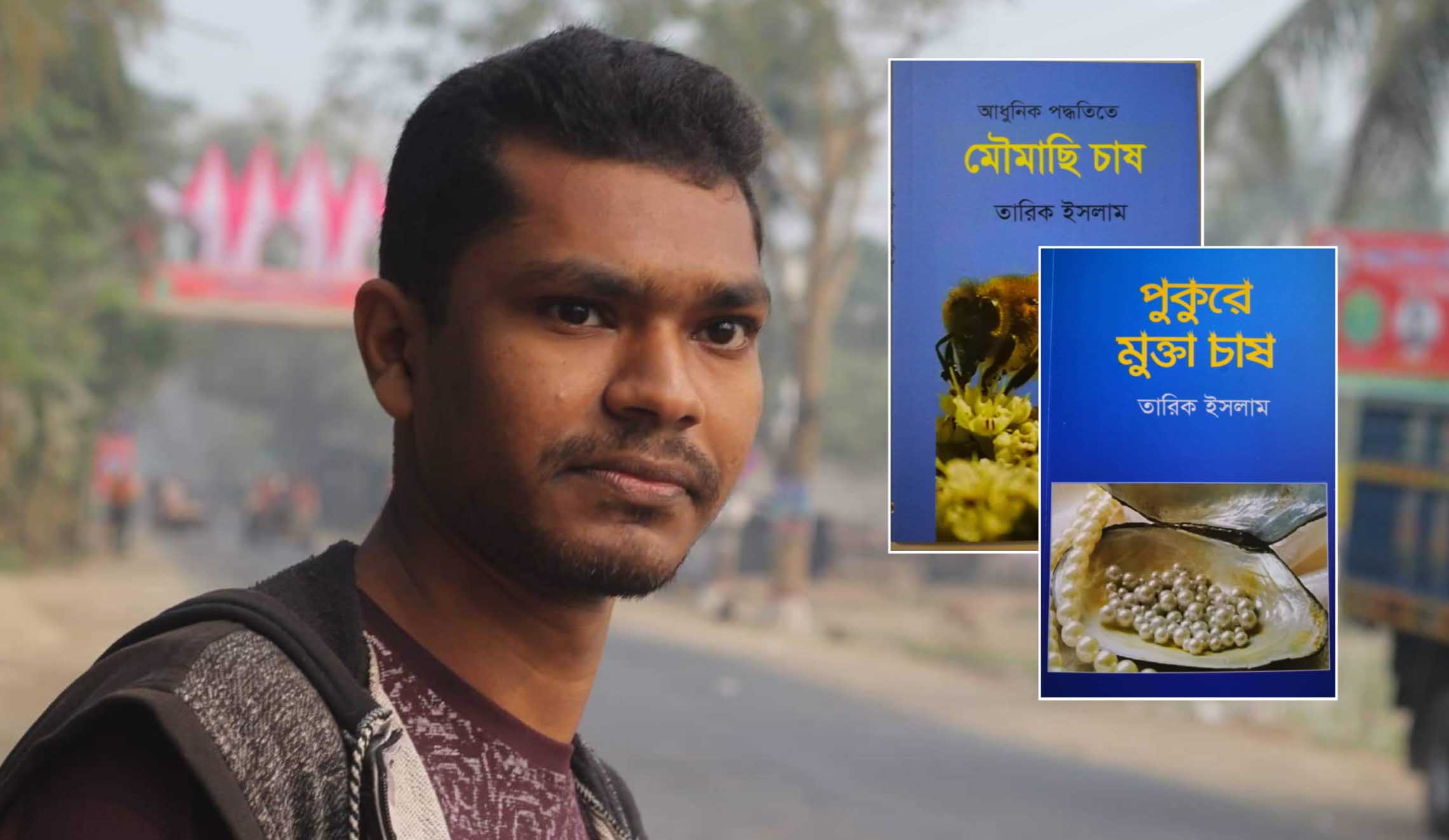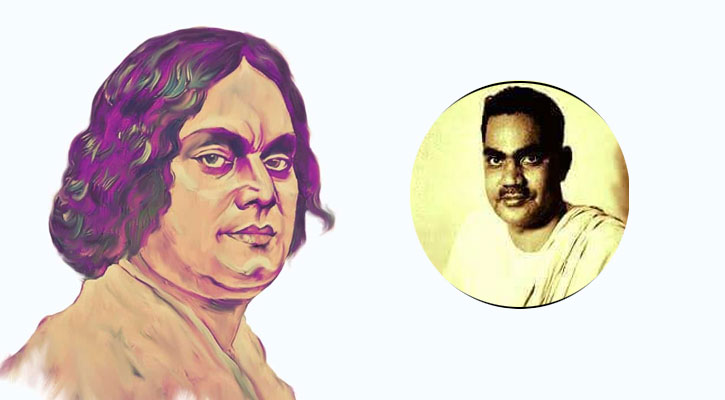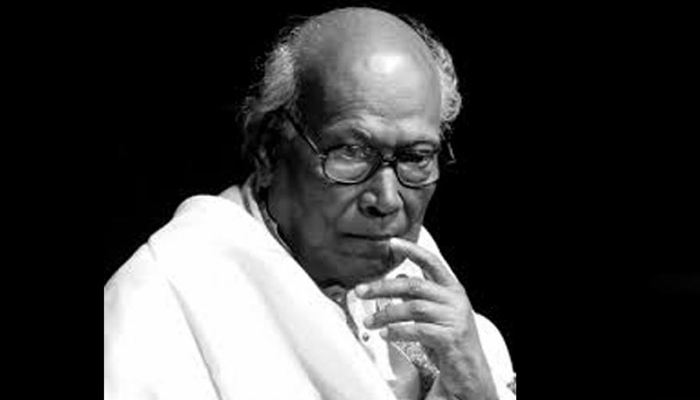সম্প্রতি তিব্বতের জনগণের ধর্ম পালন ও নিজেদের নিয়মিত স্বাধীন জীবনযাপনের বিষয়ে মার্কিন হাউসে ‘তিব্বত’ রেজল্যুশন পাস করা হয়। এ বিষয়ে শুরু থেকেই হুমকি দিয়ে আসছিল চীন। কিন্তু দেশটির সেই রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চস্তরের কংগ্রেশনাল প্রতিনিধিদল ভারতে তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামার সঙ্গে দেখা করেন জুন মাসের ১৯ তারিখে। বিষয়টি তিব্বতের মানবাধিকার ইস্যুর জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। এই প্রতিনিধিদল তিব্বতের জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানায়।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, তিব্বত ইস্যুতে চীনের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ফেরত দেওয়ার আলোচনা শুরু করতেই যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপ। যেখানে মার্কিন প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন মার্কিন হাউসের প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। চীনের হুমকি উপেক্ষা করেই ভারতে দালাই লামার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ২০২২ সালেও চীনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাইওয়ান সফর করেছিলেন তিনি। ন্যান্সি দালাই লামার শিষ্য হিসেবে সুপরিচিত। সুতরাং এটি বেশ স্পষ্ট যে, চীনের শত বিরোধিতার পরও ন্যান্সি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে দালাই লামার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং হয়তো ভবিষ্যতেও করবেন।
বিগত কয়েক বছর করোনা মহামারি ও বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিব্বতের নিজেদের আগ্রাসন আরও বাড়িয়েছে চীন। ২০২১ সালে তিব্বতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে চীন। এ সময় তিব্বতের অধিবাসী ও প্রবাসে থাকা তিব্বতিয়ানরা জানান, স্থানীয়দের নিজেদের সংস্কৃতি অনুসারে চলতে বাধা দিচ্ছে চীন সরকার। সেইসঙ্গে তিব্বতের অধিবাসীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমেও বাধা প্রদান করে চীন। ২০২২ সালে তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের মুখপাত্র তেনজিন লক্ষ্মী জানান, বেশ কিছু তিব্বতিয়ান লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীদের বন্দি ও আটক করেছে চীন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তিব্বত এখনো চীনের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি। আর তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণে চীন আরও যুদ্ধংদেহী অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা তিব্বতের সব ঐতিহ্যের নিন্দা করার পাশাপাশি সেখানকার সব ঐতিহ্য মুছে ফেলছে ধীরে ধীরে।
তিব্বতের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম এবং ইতিহাস ছিল। বেশ শক্তিশালী নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা বোধ ছিল এ অঞ্চলের মানুষের। কিন্তু চীনা কমিউনিস্টরা সর্বদা এ অঞ্চলকে যুক্ত করতে চেয়েছিল। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর চীনের সেনা তিব্বতে প্রবেশ করে। সেই সময় বেশিরভাগ তিব্বতি এ আক্রমণের কথা ভাবতেই পারেননি। দাওয়া নরবু, সেই সময়ে শিশু। ১৯৭৮ সালে ওয়ার্ল্ড ভিউ ম্যাগাজিনে তিনি লেখেন, ‘১৯৫০ সালের চীনা আগ্রাসনের খবর আমাদের কাছে ১৯৫২ সালের কোনো একসময়ে এসে পৌঁছেছিল।’ ১৯৫০ সালে তিব্বত এমনই ছিল। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে নরবু লিখেছেন, ‘পৃথিবীর ছাদে আধুনিকতার আশীর্বাদ এবং বাধা উভয় থেকেই দূরে (তিব্বত) ছিল একটি প্রত্যন্ত ভূমি। ধীরে ধীরে চীনা আগ্রাসনের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বেগ ছড়ায় আরও ধীরে। আতঙ্কজনক খবর সত্ত্বেও শাক্যতে কেউ তার তরবারি ধারালো করেননি। তার ধনুক এবং তীর ব্যবহারও করেননি।’ শাক্যের বাসিন্দারা কল্পনাও করেননি যে, চীনের আক্রমণ একটি স্থায়ী দখলদারি হয়ে উঠবে, যা তিব্বতকে চিরতরে বদলে দেবে। চীনের সেই আক্রমণের ৭৪তম বছর চলছে এখন। কিন্তু চীনের অস্ত্রের বিরুদ্ধে কখনোই তিব্বতের মানুষ সহিংস অবস্থান গ্রহণ করেননি। কেননা সহিংসতা তিব্বতের অধিবাসীদের শিক্ষা নয়। কিন্তু এমন অহিংস একটি জাতির ওপর চীনের অত্যাচার নিপীড়ন নিয়ে বিশ্বের নিশ্চুপ অবস্থান এ অঞ্চলের মানুষের সেই অহিংস আচরণ বজায় রাখার পথে ভবিষ্যতে বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে। এটি শুধু চীনের জন্য নয়, বরং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান এমনকি বাংলাদেশের জন্যও হুমকির কারণ হতে পারে। আর এ কারণেই চীনের ক্ষোভ উপেক্ষা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দালাই লামার সঙ্গে বৈঠকের পর আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের দ্বিদলীয় সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রায় একই সময়ে, কানাডিয়ান হাউস অব কমন্স সর্বসম্মতিক্রমে তিব্বতের স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব পাস করে। তিব্বতিরা একটি জাতি হিসেবে এ মৌলিক অধিকারের দাবিদার।
মার্কিন প্রতিনিধিদলের এ সফর শেষে বেইজিং বেশ হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করেছে যে, বিশ্ব তার চাপ এবং গুণ্ডামি কৌশলের কাছে নতিস্বীকার করবে না। বিশ্ব তিব্বতের ওপর চীনা দখলের বৈধতা সম্পর্কে দেশটির প্রোপাগান্ডাকে গ্রহণ করবে না। বেইজিং এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে তিব্বত সমর্থনে উত্থাপিত বিলে স্বাক্ষর না করার জন্য আবেদন করছে, যা শুধু স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে। এতদিন চীন হুমকি দিয়ে এসেছে, দালাই লামার সঙ্গে দেখা করলে তার ফল যুক্তরাষ্ট্রকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু এখন দালাই লামার সঙ্গে বৈঠক শেষে চীন তার আগের একগুঁয়ে অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। বরং এখন চীন ‘তার রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলোর সম্পূর্ণ প্রতিফলন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশোধন করার’ কথা জানিয়েছে, যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেনি চীন। চীনের হঠকারিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তারা মার্কিন আইনপ্রণেতাদের দালাই লামার সঙ্গে দেখা না করার জন্য হুমকি দেওয়ার সাহস দেখিয়েছে। শুধু গণমাধ্যমে নয়, হুমকি প্রদান করে চীন প্রতিনিধিদলটিকেও চিঠি প্রদান করেছে। প্রতিনিধিদলের নেতা ইউএস হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান মাইকেল ম্যাককাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বলেন, ‘আমাদের প্রতিনিধিদল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছে, যেখানে আমাদের এখানে না আসার জন্য সতর্ক করেছে। তারা তাদের মিথ্যা দাবির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, ১৩ শতক থেকে তিব্বত চীনের অংশ। কিন্তু আমরা সিসিপির সেই ভয় দেখানোতে মনোযোগ দিইনি এবং আমরা আজ এখানে এসেছি।’ ভারতের ধর্মশালায় নির্বাসিত তিব্বত সরকারের তত্ত্বাবধানে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যাকে চীন ‘নিছক রাজনৈতিক চক্র’ বলে উড়িয়ে দেয়। মার্কিন প্রতিনিধিদলের এই নেতা বলেন, ‘তিব্বতের জনগণ একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের অধিকারী এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা বলা উচিত। তাদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করার অধিকার লাভ করার কথা। সে কারণেই আমরা এখানে সিসিপির সতর্কতা অমান্য করেছি।’
মার্কিন আইনপ্রণেতারা যারা আমেরিকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সমর্থন করেছেন। তারা মনে করেন, তিব্বতে কখনোই চীনের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ নিয়ন্ত্রণের মাত্রাটি ছিল একটি শিথিল আধিপত্য, যা এ অঞ্চলের ওপর সার্বভৌম অধিকার থেকে অনেক দূরের বিষয়। অতীতেও বেশ কয়েকবার এ বিষয়ক আলোচনায় জানানো হয়, তিব্বত কীভাবে চীনা নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ছিল এবং ১৯১২ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তিব্বত একটি স্বাধীন দেশ ছিল। আর এ কারণেই ১৯৫০ সালে তিব্বতে চীনের অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ।
তিব্বত সমস্যার সমাধান বিষয়ক বিলটি মার্কিন হাউসে ৩৯১ বনাম ২৬ ভোট ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়। তিব্বতের পক্ষে সব ডেমোক্র্যাটের পাশাপাশি অধিকাংশ রিপাবলিকান ভোট দেন। মাত্র ২৬ জন রিপাবলিকান এর বিপক্ষে ভোট দেন। এ বিলটির অন্যতম প্রবর্তক ও মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতা ম্যাককল বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র কখনোই স্বীকার করেনি যে, তিব্বত প্রাচীনকাল থেকে চীনের অংশ ছিল। কারণ সিসিপি মিথ্যা দাবি করেছে। এ আইনটি মার্কিন নীতিকে স্পষ্ট করেছে এবং তিব্বতি জনগণের অনন্য ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। এটি মার্কিন কূটনীতিকে চীনা প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশনা দেয়, তিব্বতিদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত করে এবং সিসিপি ও তিব্বতের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অন্য নেতাদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। যে কোনো রেজল্যুশন বা আলোচনায় তিব্বতি জনগণের ইচ্ছা ও কণ্ঠকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।’
এর আগে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২০ সালে তিব্বতের জনগণের পরবর্তী দালাই লামার পছন্দে চীনের হস্তক্ষেপ রোধ করতে ২০২০ সালে তিব্বত নীতি ও সমর্থন আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন। কানাডিয়ান হাউস অব কমন্সে গৃহীত প্রস্তাবটি তিব্বতিদের চীনের পদ্ধতিগত সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের বিরোধিতা করেছে এবং বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় নীতিগুলো বেছে নেওয়ার অধিকারকে তিব্বতি জনগণের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে। সেইসঙ্গে ১৪তম দালাই লামার পুনর্জন্ম নির্বাচনের বিষয়টিও তিব্বতের জনগণের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
কানাডিয়ান হাউসের প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয় যে, ‘চীন তিব্বতিদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। তিব্বতিরা, একটি জাতি হিসেবে তাদের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে পারে। কোনো বাহ্যিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় নীতি নির্বাচন করতে পারে এবং এ ক্ষমতায়ন চীনকে ১৪তম দালাই লামার পরবর্তী তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেয়।’
কানাডিয়ান হাউসের রেজল্যুশন বেশ স্পষ্টভাবে তিব্বতের জনগণের জন্য প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে। সেইসঙ্গে বর্তমান দালাই লামার অবস্থানের সঙ্গেও বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও বোঝায়।
এটি বেশ স্পষ্ট করেই বলা যায়, এ প্রেক্ষাপটে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন আইনপ্রণেতাদের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠক তিব্বতের জনগণের জন্য ভারতীয় সমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তিব্বতের জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে বিশ্বের জন্য ভারতীয় সমর্থন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত তিব্বতের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক তিব্বতি উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিচ্ছে। প্রায় এক লাখের বেশি তিব্বতিয়ান ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছে। সেইসঙ্গে দালাই লামা ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ মর্যাদাসহ ১৯৫৯ সাল থেকে ভারতের সম্মানিত অতিথি হিসেবে রয়েছেন। তিব্বত মালভূমিতে চীনের এ নীল-নকশাকে পরাস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে মার্কিন প্রতিনিধিদল। তারা বলেছিল, একসঙ্গে আমরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিরোধের একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠাতে পারি। কারণ যখন বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতন্ত্র একসঙ্গে দাঁড়ায়, তখন স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা জয়লাভ করে।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট